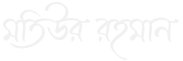আনিস স্যার: সাধারণ, তবু অসাধারণ
অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে অনেকেই অনেক পরিচয়ে সম্বোধন করেন, ব্যাখ্যা করেন, আলোচনা করেন; কিন্তু আমার কাছে তিনি আনিস স্যার। যদিও সরাসরি তাঁর ছাত্র ছিলাম না, আমার বিষয় সংখ্যাতত্ত্ব আর তিনি শিক্ষক ছিলেন বাংলার। আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, স্যার তখন সেখানে শিক্ষক। আমরা জানি, তিনি শিক্ষক হতে চেয়েছিলেন, আমৃত্যু শিক্ষকই ছিলেন। কিন্তু সেই কখন, কোন সময়, কীভাবে যোগাযোগ, কোন পরিচয়ের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে আমাদের আনিস স্যার হয়ে উঠলেন, সেটা এখন খুঁজে বের করা কঠিন।
তবে এটা খুব পরিষ্কার, আনিস স্যার সত্যিকার অর্থে আমাদের জীবনে একজন শিক্ষকই হয়ে উঠেছিলেন। একবার দুষ্টুমি করে বলেছিলাম, স্যার, আমরা তো প্রায় সমবয়সী। আমাদের বয়সের পার্থক্য আর কত? সাত-আট বছর! তিনি শুধু হেসেছিলেন। তাঁর ব্যবহার-আচরণে নম্রতা ও সৌজন্য, আনন্দ ও কৌতুক এবং সবসময় সহযোগিতার মনোভাবের মধ্য দিয়েও তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জেনেছি, বুঝেছি ও শিখেছি। তিনি কখনোই এটা করা উচিত বা উচিত নয়, এটা ঠিক হয়নি বা ভালো করোনি্—ধরনের কোনো কথা বলেছেন বলে মনে পড়ে না। কোনোদিন কারো সম্পর্কে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি।
আনিস স্যার যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করতেন, তাঁরা বয়সে ছোট হলেও একপর্যায়ে তাঁদের মধ্যে সেই বয়সের পার্থক্যটা কমে যেত। আমরা নির্দ্বিধায় সাতপাঁচ না ভেবেই যে-কোনো বিষয়ে তাঁর শরণাপন্ন হতাম। অথবা, নেহাতই একান্ত একটা ভালো ও সুন্দর কিছু সময় কাটানোর একটা বড় আশ্রয় হয়ে উঠেছিলেন তিনি। আরেকটি বিষয়, কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার শুরু থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত স্যারের আচরণ, ব্যবহার ও বিদায় নেওয়া—এসবের মধ্যেও একটা ভীষণ রকমের সহজ সৌজন্যের প্রকাশ ছিল।
আনিস স্যার কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে—সেটা ব্যক্তিক, পারিবারিক বা সামাজিক হোক না কেন—কোনোদিন দেরিতে গেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। একান্তই আড্ডা দেওয়ার জন্য বা কিছুটা আনন্দময় সময় কাটানো—এ রকম অনুষ্ঠানে অনেক সময় বিলম্ব হতো আমার। চার-পাঁচ বছর আগে ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে আমাদের একটা ভালো আড্ডার জায়গা তৈরি হয়েছিল—লেখক-শিল্পীদের উপস্থিতি ছিল প্রধান। তো সেখানে যেতে আমার বিলম্বের মধ্যে স্যার ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন, কোথায়? কখন আসছ? কখনো কখনো সেটা নিয়ে কুণ্ঠিত হয়েছি, বিব্রত হয়েছি; কিন্তু সেই একই কাজ আবারো করেছি।
কোনো ধরনের পরামর্শ, সহায়তা বা সাহায্য-সহযোগিতা চেয়ে পাইনি, এমন কোনো কথা মনে করতে পারব না। তবে এটাও ঠিক, বেশ কয়েক বছর ধরে প্রথম আলোর কোনো অনুষ্ঠানে স্যারকে আসতে বলা, কোনো লেখা বা অন্য কিছু করার জন্য স্যারকে আমি অনুরোধ করতে চাইনি। আমাদের অফিসের কেউ বলতে চাইলেও আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত থাকতাম। বলতাম, দেখো, স্যারকে আর কষ্ট দিয়ো না। তাই বিগত তিন-চার বছরে আমাদের যেসব অনুষ্ঠানে তিনি নিয়মিত আসতেন, সেগুলোতেও কোনোভাবে তাঁকে যুক্ত করা থেকে আমি বিরত থাকতে চেষ্টা করতাম। তারপরও হয়তো বাধ্য হয়ে কখনো-সখনো সেটা করেছেন সাজ্জাদ শরিফ বা জাফর আহমদ।
আমাদের দেখা জীবনে আনিস স্যার কোনোদিনই কাউকে ‘না’ বলেননি। আমরা, আমাদের অনেক বন্ধু, অনেক সংগঠন, অথবা তার বাইরেও অনেকেই—স্বল্পপরিচিত হলেও, তাঁরা নানা সময়ে নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকতেন। প্রতিদিন এক বা একাধিক সভা-সমিতি, ছোট-বড়-মাঝারি যেকোনো অনুষ্ঠানে যাওয়া তাঁর জন্য ছিল একটি দায়িত্ব বা কর্তব্যের ব্যাপার। কোনো কোনো সময় অসুবিধা বা বিরক্ত বোধ করলেও না বলতে পারতেন না। বেশ কয়েক বছর আগে এ-বিষয়ে আমি দুয়েকবার বললেও পরে আর বলিনি। স্যারের অনেক সুহৃদ তাঁকে এসব বলার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরাও বলেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর মতো করেই চলেছেন। তিনি মানুষ পছন্দ করতেন, মানুষকে ভালোবাসতেন, যে-কোনো মানুষের ছোট-বড় যে-কোনো অনুরোধ রক্ষা করাকে তিনি দায়িত্ব মনে করতেন। এসব তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ হয়ে গিয়েছিল।
দুই
১৪ মে বিকেলে আনিস স্যারের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরপরই বন্ধু আসাদুজ্জামান নূর আমাকে ফোনে অনেক কথা বললেন। অনেক কষ্ট নিয়ে বললেন, ‘গেল ফেব্রুয়ারি মাসের বইমেলাতেও প্রায় প্রতিদিন স্যার তিনটা-চারটার সময়ে নানা বইয়ের প্রকাশনার অনুষ্ঠানে হাজির হতেন। বলতাম, স্যার, কেন, কী দরকার এসবের? সেই একই জবাব, আমি তো না করতে পারি না।’ অসুবিধা হলেও এটা যেন ছিল তাঁর কর্তব্য। আমরা কত ছোট ছোট কাজ বা লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে স্যারের কাছে গেছি, কোনোদিন না করেননি। আমাদের মতো আরো বহু বন্ধু-সহযোগী বা গুরুজনের কথা তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শুনেছেন, তাঁদের অনুরোধ-উপরোধ মেনেছেন। আনিস স্যারের কাছে ছোট কাজ বা বড় কাজ বলে কিছু ছিল না। সারাজীবনের পুরোটা সময় তিনি ব্যস্ত থেকেছেন বহুমুখী কাজে—একটির পর আরেকটি, না হয় তো একসঙ্গে একাধিক—বলা যায় একটি-দুটি নয়, দশ রকম কাজ একসঙ্গে করেছেন।
দেশেই শুধু নয়, বিদেশে গেছেন পড়াশোনা, গবেষণা বা সেমিনারে অংশ নিতে। সেখানেও নানা কাজ তো ছিলই, ব্যক্তিগত অনুরোধেও কত কিছু করতে হয়েছে। এত কিছুর পরও আনিস স্যার ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে আশিতম জন্মবার্ষিকীর অভিভাষণ ‘জীবনে আমার কোনো খেদ নেই’-এ বলেছেন, ‘অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক আফসোস করতেন, “আপনি তো আর লেখাপড়া করলেন না!” তাঁর মতো মানুষের প্রত্যাশা যে আমি পূরণ করতে পারিনি, তা আমার জন্য দুঃখের বিষয়। ভেবে দেখেছি, আশানুরূপ কিছু করতে না পারার তিনটে কারণ আছে আমার—সামাজিক অঙ্গীকার পূরণের চেষ্টা, আমার স্বাভাবিক আলস্য এবং অস্বাভাবিক আড্ডাপ্রিয়তা। সামাজিক কর্তব্যবোধ আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেজন্য সময় দেওয়াটা আমি কখনোই সময়ের অপচয় মনে করতে পারিনি। নিজের আলস্য অবশ্য ক্ষমার অযোগ্য। আমার বন্ধুচক্র বিশাল। তাদের সঙ্গে সময় কাটানো আমার জীবনের প্রশান্তির একটা বড় উৎস।’
ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসে শিক্ষকতা ও ক্লাসের বাইরে অসংখ্য কাজ এবং ছোট-বড় অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ততা, দেশে-বিদেশে বহু আলোচনা ও বক্তৃতা, লেখালেখি, গবেষণা, সম্পাদিত বই ও নিজের বই প্রকাশ, বড় কোনো সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া—স্যারের প্রায় বিরাশি বছরের এতসব কাজ যদি ‘স্বাভাবিক আলস্য’ হয়, তা হলে আমরা সক্রিয়তা কাকে বলব?
প্রসঙ্গত বলি, মাত্র ২৫ বছর বয়সে আনিস স্যার পিএইচ.ডি করেছেন। সেই তরুণ বয়সে শুরু, এরপর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস নিয়ে গবেষণায় তিনি এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। প্রবন্ধ, গবেষণা, স্মৃতিকথা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিচারণ, শিশুসাহিত্য, নাটকের অনুবাদ, বক্তৃতা সংকলন ইত্যাদি মিলিয়ে আনিস স্যারের মৌলিক বইয়ের সংখ্যা ৪০টি। এগুলো প্রকাশিত হয় ঢাকা, কলকাতা, টোকিও ও লন্ডন থেকে। স্যারের সম্পাদিত (একক, যুগ্ম ও যৌথভাবে) বই ষাটটি—বাংলা ও ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে।
তিন
১৯৬৩ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করি, তার আগে থেকেই আমরা আনিস স্যার সম্বন্ধে জানি যে, বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনের সময় থেকেই গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর যুক্ততা ছিল। পঞ্চাশের দশকেই সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক নানা রকম কর্মকাণ্ডে তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত তা বজায় ছিল।
১৯৬২ সালের দিকে আমাদের এক কাকার লালবাগের বাসায় আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতা জ্ঞান চক্রবর্তী থাকতেন। সে-সময় তাঁর লালবাগের ছোট্ট বাসায় গিয়ে দেখি কমরেড জ্ঞান চক্রবর্তী আনিসুজ্জামানের পিএইচ.ডির সেই থিসিসের (পরে যা ঈষৎ পরিমার্জিত হয়ে মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য নামে বই হিসেবে প্রকাশিত হয়) টাইপ করা কপি পড়ছেন। এটা আমাকে খুব বিস্মিত করেছিল। ওই যে প্রথম জীবনে বামপন্থার প্রতি তাঁর সমর্থন এবং পঞ্চাশ-ষাটের দশকের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এদেশের সামগ্রিক গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক, এমনকি বড় রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর একটা যুক্ততা, জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্তই এটা ছিল। আশিতম জন্মবার্ষিকীর অভিভাষণে স্যার বলেছেন, ‘ভাষা আন্দোলনের অল্পকাল পর আমি গোপন কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসি। সে সংযোগ বছর পাঁচেকের বেশি স্থায়ী হয়নি। তবে ওই সময়ে বামপন্থার যে শিক্ষা লাভ করেছিলাম, তা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি চিরকালের জন্য গঠন করে দিয়েছিল। ওই শিক্ষা না পেলে আমি “আমি” হতে পারতাম না।’
সেই ভাষা-আন্দোলনের সময় থেকে আমরা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে একজন সক্রিয় কর্মী ও সংগঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখি। গণতান্ত্রিক যুবলীগের দফতর সম্পাদক থাকাকালেই সংগঠনের পক্ষে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কী ও কেন পুস্তিকা তাঁর লেখা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরপর এপ্রিলে গঠিত প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের খসড়া রচনা আনিস স্যারের। তারপরই আমরা তাঁকে শান্তি পরিষদের কাজে সক্রিয় দেখি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এটা ভাবতে আমাদের ভালো লাগে যে, এসব সংগঠনের সঙ্গে আমরাও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম।
কর্মী ও সংগঠক হিসেবে আনিস স্যারের দুটি উদ্যোগ দেশের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকবে—১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্রবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে ১৯ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির যে-খসড়া করেছিলেন মুনীর চৌধুরী, তা চূড়ান্ত করতে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও আনিসুজ্জামান যুক্ত ছিলেন। আনিস স্যার বিবৃতি কপি করে ঢাকায় পত্রিকা অফিসগুলোতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।
১৯৮৭ সালে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিষয়ে ৩১ নাগরিকের আরেকটি ঐতিহাসিক বিবৃতির উদ্যোগ শুরু হয়েছিল দুই আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের সঙ্গে ড. মোজাফফর আহমদ ও আনিস স্যারের আলোচনার মধ্য দিয়ে। বিবৃতির খসড়াও তৈরি করেছিলেন এই দুজন মিলে। পরে অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন ও আনিস স্যারের বাসাই হয়ে উঠেছিল বিবৃতিদানকারীদের বৈঠকের স্থান। এরশাদের পতন পর্যন্ত এই নাগরিকেরা সক্রিয় ছিলেন। তবে কয়েকজন এই উদ্যোগ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।
সেই ভাষা-আন্দোলনের শুরু থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ পুরো শিক্ষা ও শিক্ষকতা জীবনে আনিস স্যার বহুমুখী কাজে যুক্ত হয়েছেন কর্মী হিসেবে, আবার সংগঠক হিসেবেও। সাহিত্য ও সংস্কৃতি শুধু নয়, দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে স্যার দূরে সরে থাকেননি কখনো। সর্বশেষ ২০১২ সালের ডিসেম্বরে সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদবিরোধী সংগঠন ‘রুখে দাঁড়াও বাংলাদেশে’র আহ্বায়ক ছিলেন আনিস স্যার।
সাম্যবাদী রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে থেকে আমি যে-দায়িত্বগুলো পালন করতাম, তার মধ্যে পত্রিকা ও প্রকাশনা ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিভাগ এবং শান্তি-মৈত্রী-সংহতি আন্দোলনের জাতীয় কমিটিগুলো দেখভালের দায়িত্বে ছিলাম আশির দশকের বেশ কয়েক বছর। সে-সময়ে আমাদের উদ্যোগে এই তিনটি কমিটির মধ্যে বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির সভাপতি হলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এবং বাংলাদেশ শান্তি পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন লেখক ও সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীন। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের সভাপতি হয়েছিলেন আনিসুজ্জামান। ডা. সাইদুর রহমান ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক। আবুল হাসনাতও অনেক সহযোগিতা করেছেন। আনিস স্যার ওই আন্তর্জাতিক সংগঠনের সহসভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কমিটির হয়ে তিনি নয়াদিল্লি, কলম্বো, এডেন (ইয়েমেন), কায়রো (মিশর) ও মস্কো গেছেন সম্মেলন বা আলোচনায় যোগ দিতে। এসব সফর করেছেন আনন্দের সঙ্গে। কায়রোতে দেখা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা ও বুত্রোস বুত্রোস-গালি (পরে জাতিসংঘের মহাসচিব), মস্কোতে ভিয়েতনামের নেত্রী নগুয়েন থি বিন প্রমুখের সঙ্গে। দেশে এই সংগঠনের অনেক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন স্বাভাবিকভাবেই।
চার
১৯৬২ সাল। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। কিন্তু সেই ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ সালের আন্দোলন শুরুর আগে থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলা ও মধুর ক্যান্টিনে আমার নিয়মিত উপস্থিতি শুরু, তখন স্যারকে দেখেছি। ১৯৬৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ও সংস্কৃতি সংসদের সংকলন প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হই, তারপর কয়েকবার স্যারের কাছে লেখা চাইতে গেছি। আরেকটা ঘটনা মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে চারদিকে তুমুল আন্দোলন চলছে, চরম উত্তেজনাও। প্রায়ই রাতে সূর্য সেন হলে রাত কাটাই। সেই ঊনসত্তরের ফেব্রুয়ারির কোনো এক রাতে হলে থাকা যাবে কি না, রাতে পুলিশ বা সামরিক বাহিনী ঢুকে যেতে পারে—এই ভাবনা থেকে মানিক ভাই (সে-সময়ে ছাত্র ইউনিয়নের নেতা সাইফউদ্দিন আহমেদ) আর আমি দুজনই রাত দশটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীলক্ষেত পাড়ার কোয়ার্টারে স্যারের বাসায় গিয়ে রাতে থাকার কথা বলতেই তিনি কোনো প্রশ্ন না করে নির্দ্বিধায় তোশক, চাদর আর বালিশ নিয়ে এলেন। রাতে বৈঠকখানায় ঘুমিয়ে স্যার জেগে ওঠার আগেই আমরা বেরিয়ে আসি বাসা থেকে।
’৬৮ সালে একদিন বিকেলে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানে আনিস স্যারের সঙ্গে মালেকা ছিল। তো আনিস স্যার গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন, গেটের কাছে মালেকাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাবে? সেখানে আমিও ছিলাম, একসঙ্গে কোথাও যাব—আমাদের দুজনকে আমাদের গন্তব্যস্থলে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। খুব ছোট্ট একটা ঘটনা, কিন্তু এটা করা আর না-করার মধ্যে যে কত পার্থক্য! একইভাবে ’৭৭ সালে বেইলি রোডের মহিলা সমিতি মিলনায়তনে আমি আর মালেকা নাগরিকের বের্টোল্ট ব্রেখ্টের নাটক, আসাদুজ্জামান নূর-অনূদিত দেওয়ান গাজীর কিস্সা দেখে বেরোচ্ছি, তিনিও। বললেন, তোমরা কোথায় যাবে? বললাম, লারমিনি স্ট্রিটের বাসায়। বললেন, গাড়িতে ওঠো। তিনি আমাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন শ্বশুরবাড়িতে স্বামীবাগের বাসায়। তাঁর এ-ধরনের সৌজন্যের ছোট ছোট কত ঘটনার কথা মনে পড়ে! নিশ্চয়ই এরকম অভিজ্ঞতা বহুজনের রয়েছে।
মনে পড়ে যে, আনিস স্যার মুনীর চৌধুরীর ওপর একটা বই লিখবেন, তাঁর জন্য কিছু তথ্য জানার আগ্রহ ছিল। মালেকার বড় ভাই সাবেক অর্থসচিব গোলাম কিবরিয়া ও তাঁর স্ত্রী মুনীর চৌধুরীর ছোট বোন নাদেরা চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলবেন। আমাদের লারমিনি স্ট্রিটের বাসায় ব্যবস্থা হলো। স্যার সন্ধ্যাবেলা এলেন, কথা বললেন। খাবারদাবারের ব্যবস্থা ছিল, সেটা শেষ করে রাতের ট্রেনে তিনি চট্টগ্রাম চলে যাবেন। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা আনিস স্যার মফিদুল হকের মোটরসাইকেলের পেছনে বসে কমলাপুর রেলস্টেশনে রওনা হলেন। তাঁর মতো একজন অধ্যাপক নির্দ্বিধায় মোটরসাইকেলের পেছনে বসে চলে গেলেন। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম।
মুনীর চৌধুরী বইটা বের হয়েছিল ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে, থিয়েটার থেকে। পরে ২০১৪ সালে বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মুনীর চৌধুরীর বোন নাদেরা চৌধুরী ও ভাই শামসের চৌধুরী। বইটি বের হয়েছিল বাংলা একাডেমি থেকে। তাতে স্যার খুব খুশি হয়েছিলেন। তবে দুই অনুবাদক তখন আর বেঁচে নেই।
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী থেকে স্যারের স্বরূপের সন্ধানে বইটি প্রকাশের অনুমতির জন্য মফিদুল হক ও আমি গিয়েছিলাম স্বামীবাগের বাসায়। স্যার সানন্দেই অনুমতি দিয়েছিলেন। মফিদুল হক সেদিনও বললেন, স্যার স্বরূপের সন্ধানে বইয়ের প্রুফ দেখতে তাঁর মোটরসাইকেলের পেছনে বসে পুরান ঢাকার অ্যাবকো প্রেসে গেছেন। বইটি বেরিয়েছিল ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে।
১৯৭৫ সালের ২৭ অক্টোবর ঢাকার কাপ্তানবাজারের পাশে ঠাটারীবাজারের (বামাচরণ স্ট্রিট) বাসায় আনিস স্যারের বাবা খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ এ.টি.এম মোয়াজ্জম মৃত্যুবরণ করেন। পুরো নাম আবু তাহের মোহাম্মদ মোয়াজ্জম। স্যারের পুরো নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান। মনে পড়ে, বন্ধু আবুল হাসনাত ও আমি স্যারের বাবার কুলখানিতে গিয়েছিলাম। আমরা দুজনই সে-সময় ওই বাসার কাছাকাছি থাকতাম। সেখানে পরিচিতদের মধ্যে ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দেখেছিলাম। ডা. নুরুল ইসলাম ও ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী স্যারের বাবার চিকিৎসক ছিলেন। সে-বছর এপ্রিল মাসে ডাক্তার নুরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কিংস্টন যাওয়ার পথে আনিস স্যারকে লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে বলে গিয়েছিলেন যে, বাবাকে দেখতে হলে অক্টোবরের মধ্যে দেশে ফিরতে হবে। গবেষণার কাজ শেষ করে স্যার দেশে ফিরেছিলেন ১২ আগস্ট।
কয়েক বছর আগে একবার হঠাৎ আনিস স্যারের কাছ থেকে পোস্টে একটা খাম এলো। খুলে আমি অবাক বিস্ময়ে দেখি, ১৯৭০ সালের আমাদের বিয়ের বউভাতের অনুষ্ঠানের কার্ডটি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন। হতে পারে কিছু একটা খুঁজতে বা গোছাতে গিয়ে কোনো বইয়ের মধ্যে এটা পেয়েছেন। তিনি মনে করে আমাকে সেটা পাঠিয়েছিলেন ডাকে। আসলে বিয়ের কার্ডের এই স্মৃতি রাখার বিষয়টি যে তিনি মনে করে পাঠালেন, কত ছোট্ট একটা বিষয়, অথচ কতই না দরদে ভরা! সেটাও আমি যত্ন করে রাখতে পারিনি। এমন কত কিছুই তো আমরা হঠাৎ পেয়ে যাই। কাউকে তো এভাবে দিই না।
২০১৫ সালের জানুয়ারির একটি ছোট ঘটনা বলি। আনিস স্যার মালেকাকে এক সন্ধ্যায় ফোন করলেন, তুমি বাসায় আছ? মালেকা বলল, আমি আছি, মতি বাসায় নেই। আনিস স্যার বললেন, তা হলে আমরা আসছি। ভাবিকে নিয়ে তিনি এলেন। তাঁর সদ্য প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বইটা মালেকার হাতে দিয়ে বললেন, দেখো মালেকা। বইটার উৎসর্গপত্রে লেখা, ‘মতিউর রহমান/মালেকা বেগম’। নিচে সই, আনিসুজ্জামান, তারিখ ১০.০১.১৫। আবার দুজনের জন্য দুটি বই। মালেকা অভিভূত। আমি পরে এসে জানলাম। এই যে তিনি বাসায় এসে বইটা আমাদের দিয়ে গেলেন—এই হলেন আনিসুজ্জামান। আরো কেউ কেউ বই উৎসর্গ করেছেন, তবে এভাবে বেবী ভাবিসহ বাড়িতে এসে বই দিয়ে যাওয়া … ছোট্ট একটি ঘটনা, কিন্তু ব্যস্ততা, শত কাজের মধ্যে এটি একজন মানুষের ভালোবাসার এক পরিচয়! সব সময় এমনই ছিলেন তিনি।
আনিস স্যার কখনো-সখনো এটা-সেটা নিয়ে জানতে চাইতেন ফোনে। সবার কুশল সংবাদ নিতেন। কখনো কখনো আমার কোনো লেখা পড়ে ফোন করতেন। মনে পড়ে, কবি অরুণ মিত্র মারা গেলে ১ সেপ্টেম্বর ২০০০ সালে প্রথম আলোতে লিখেছিলাম ‘অরুণ মিত্র : মিছিলের কবি, মিছিলের যাত্রী নন’। লেখাটি পড়ে সেদিনই বিকেলে ফোনে প্রশংসা করেছিলেন। খুব ভালো লেগেছিল। আমাদের কাগজের সাহিত্য সাময়িকীতে চে গুয়েভারাকে নিয়ে বড় একটি লেখা ‘বন্দুকের পাশে কবিতা’ ছাপা হয়েছিল ২০০৮ সালের ১০ অক্টোবর। আবার স্যারের ফোন, ‘মতি, খেটেখুঁটে লিখেছ। ভালো হয়েছে।’ আরো কয়েকবার হয়েছে এরকম। আসলে লেখালেখি তো করিনি তেমন। দিন-রাত দৈনিক পত্রিকার কাজ করতে করতেই জীবনের ভালোবাসাগুলো দূরে সরে গেল।
পাঁচ
আমাদের বাসায় অনেক সান্ধ্য-অনুষ্ঠান বা কোনো বিশেষ অতিথির উপস্থিতির কারণে দেশ-বিদেশের বন্ধুদের জন্য বিশেষ আয়োজন—যে-কোনো কিছুই হোক না কেন, আনিস স্যারকে ছাড়া আমরা তেমন কোনো কিছু করতাম না। আর এমন কখনোই হয়নি যে তিনি আসেননি। এবং সেটা সময়মতো। কখনো কখনো সবার আগে। আর প্রতিবারই আমাদের জন্য বা নাতি-নাতনির জন্য হাতে করে কিছু নিয়ে আসেননি—তেমনটা হয়নি। কখনো নিয়ে আসতেন ফুল, কখনো মিষ্টি বা অন্য কোনো খাবার।
আনিস স্যারের একজন প্রিয় মানুষ পররাষ্ট্রসচিব ফারুক আহমেদ চৌধুরীর মৃত্যুর আগের বেশ কয়েক বছর কখনো পারিবারিকভাবে আমাদের বাসায় ফারুক ভাইসহ অনেককে আমন্ত্রণ জানিয়েছি অথবা কোনো জন্মদিন বা কোনো একটা উপলক্ষে হয়তো ফারুক ভাইয়ের বাসায় আনিস স্যার, ভাবি ও আমরা গিয়েছি। এরকম নানাভাবে আমাদের মধ্যে একটা নির্মল আনন্দময় সময় কাটানোর পরিবেশ তৈরি ছিল—নানা মজার স্মৃতি, কত গল্প, কখনো দুপুর বা রাতে খাওয়াদাওয়া, সঙ্গে পানীয়। ফারুক ভাই নেই, আনিস স্যার চলে গেলেন। এরকম বৈঠকি, মনোগ্রাহী, উজ্জ্বল গল্পসল্প আর কোনোদিন হবে না। এ-ধরনের নানা অনুষ্ঠানে সবার সঙ্গে অল্পস্বল্প কথায় একটা সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা আনিস স্যারের মধ্যে একদম সহজাত ছিল। একবার ফারুক চৌধুরীর জন্মদিনে আমার বাসায় দাওয়াত করেছিলাম। ফারুক ভাই ও জিনাত ভাবি, ছেলে আর দুই নাতি—সবাই এলেন। আনিস স্যার আর ভাবিও এসেছিলেন। সেই সন্ধ্যাটার কথা খুব মনে পড়ে। সেবার ফারুক ভাইকে আমি আর. শিবকুমার-সম্পাদিত ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রক, বিশ্বভারতী ও প্রতিক্ষণ-প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের আঁকা ১৭০০ শিল্পকর্মের সংকলন রবীন্দ্র চিত্রাবলির বড় চার খণ্ডের একটা সেট উপহার দিয়েছিলাম। একই বইয়ের একটা সেট আগেই আমাদের বাসায় এক অনুষ্ঠানে আনিস স্যারকে দিয়েছিলাম। তিনি বেশ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।
আনিস স্যার ও ভাবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সূত্রে তাঁদের ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি, স্যারের তিন শ্যালিকা, ভগ্নিপতি ও শ্যালকদের সঙ্গেও আমাদের একটা পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। তাঁরা সবাই এক রাতে আমাদের বাসায় এসেছিলেন। দিনটি ২ ডিসেম্বর ২০১৬। সেদিন দেখেছি স্যারের শ্যালিকা ও ভগ্নিপতিদের সঙ্গে খুনসুটি। আর একই সঙ্গে সবার মধ্যে বেবী ভাবির আনন্দময় উপস্থিতি। তাঁদের মধ্যে একজন ইয়াসমিন মিস, স্যারের শ্যালিকা, আমার দুই নাতি-নাতনির প্রিয় শিক্ষক। সব মিলিয়ে আনিস স্যার, বেবী ভাবি, তাঁর পুত্র-কন্যা, পুত্রবধূ ও জামাতা—এই সমগ্র পরিবার মিলে আনন্দঘন সময় কাটানোর একটা বড় সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম সে রাতে। কয়েক বছর ধরেই আমের মৌসুমে ভাবির কাছে আমের ঝুড়ি পাঠাই। বলতাম, সবার জন্য। পরদিন সকালে স্যার কৌতুক করে ফোনে বলতেন, মতি, তুমি আমের বাগান কবে কিনলে?
আমার ছোট ভাই ডা. জাকিউর রহমান স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। আনিস স্যার পুত্রবধূর জন্য আমার ভাইয়ের শরণাপন্ন হলেন। তিনি নিজে স্কয়ার হাসপাতালে এসে বললেন, তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। স্যার তাঁর দুই নাতি-নাতনির সময়েই আমার ভাইয়ের সাহায্য নিয়েছেন। তারপর মনে করে আমার ভাই ও ছেলের পরিবার এবং আমাদের পরিবারের সবাইকে স্যার বাসায় ডাকলেন। অনেক গল্প হলো, খাওয়া হলো। অনেক সুন্দর একটি সন্ধ্যা কাটল আমাদের। এরকম তো ডাক্তারকে অনেক পরিবারকেই সাহায্য করতে হয়, কতজন মনে রাখে! আমাদের বাসায় আসা-যাওয়ার সুবাদে আমার ডাক্তার ভাইয়ের সঙ্গেও স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল স্যারের। বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকা ক্লাবে স্যারের সঙ্গে দেখা আমার ভাইয়ের। হাতে অরেঞ্জ জুসের গ্লাস। স্যার বললেন, একি, বাঘ ঘাস খাচ্ছে! আমার ভাই তখন জন্ডিস থেকে সেরে উঠেছে।
এসব ব্যক্তি বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের বাইরেও প্রথম আলোর লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্গে বছরে অন্তত একবার এক আনন্দসন্ধ্যা কাটাতাম রেস্তোরাঁ লে সিয়েল, ঢাকা ক্লাব বা সোনারগাঁও হোটেলে। নানাজন যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও ড. রওনক জাহান, সস্ত্রীক স্যার ফজলে হাসান আবেদ, সস্ত্রীক এসেছেন সাইদুজ্জামান ও জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, জিনাত ভাবিসহ ফারুক চৌধুরী, ড. কামাল হোসেন ও হামিদা হোসেন; আরো এসেছেন ড. মোজাফফর আহমদ, মুর্তজা বশীর, কাইয়ুম চৌধুরী, মঈদুল হাসান প্রমুখ। আর অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন এরকম প্রতিটি আসরের মধ্যমণি।
ছয়
অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের জীবনকে যাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে কিংবদন্তিতুল্য অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের নাম আসে সবার আগে। আনিস স্যারের মধ্যে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা কাজ করেছে। ১৯৫৬ সালে বাংলায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার পর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সূত্রে অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে আনিস স্যারের সেই যে পরিচয় হলো, সেটা আমৃত্যু ছিল। ১৯৫৬ সালে তাঁর সঙ্গে সচিবালয় অফিসের প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রশ্নের পর প্রশ্নে জর্জরিত হওয়ার প্রসঙ্গটি একাধিক লেখায় আনিস স্যার লিখেছেন, ‘শেষ পর্যন্ত মনে হলো পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।’ তারপর নানা প্রশ্নের উত্তর পেতে স্যার আবার গেছেন, তা নিয়ে লিখেছেন, ‘সেই যে গেছি, সে যাওয়া তাঁর জীবদ্দশায় শেষ হয়নি।’অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক লেখাপড়া আর গবেষণার বাইরে আনিস স্যারকে বাজার করতে শেখানোর পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে বেবী ভাবিকে রান্না শিখিয়েছিলেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার বাইরে ছোট-বড় কত বিষয়ে অধ্যাপক রাজ্জাকের সঙ্গে আনিস স্যার জড়িয়েছেন, ভাবলে অবাক লাগে। একবার ভারত সরকার আমন্ত্রণ করেছে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাককে। তিনি আনিস স্যার ছাড়া যাবেন না। পরে আনিস স্যারও আমন্ত্রিত হলেন। অধ্যাপক রাজ্জাক সিঙ্গাপুরে যাবেন চিকিৎসার জন্য, সেখানেও স্যারকে যেতে হবে। হাসপাতালেও ভর্তি হতে হলো আনিস স্যারকে। এই দুই সফর নিয়ে আনিস স্যারের ‘আব্দুর রাজ্জাক’ (চেনা মানুষের মুখ) শিরোনামের লেখাটিতে দুজনের গভীর অন্তরঙ্গতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।
অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে আনিস স্যারের ঘনিষ্ঠতা সরাসরি বেশি না দেখলেও বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সঙ্গে পারস্পরিক আন্তরিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে আমাদের। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জেল খেটে বের হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আনিস স্যারের পরিচয়। তিনি বহু বিষয়ে আনিস স্যারের মতামতের ওপর নির্ভর করতেন ভীষণভাবে। বয়সে ছোট হলেও আনিস স্যারকে বলতেন ‘আমার অভিভাবক’। অর্থাৎ বিচারপতি হাবিবুর রহমান আনিস স্যারের পরামর্শ শুনতেন, মানতেন। অনেক সময় এমন হয়েছে যে, বিচারপতি স্যারকে নিয়ে আমরা বিশেষ কিছু করতে চাই বা কোথাও বক্তৃতা দিতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলব, আমরা ভয় পেতাম, তিনি রাজি হবেন কি হবেন না। তখন আমরা আনিস স্যারকে বলতাম, ‘স্যার, আপনি একটু বলে দেন।’ আনিস স্যার বললে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সাহেব সেই কথাটা রাখতেন। আবার কোনো সময়ে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে গেলে বলতেন, আমার কাছে আসেন কেন? আমার অভিভাবককে জিজ্ঞেস করেন। আমরা বলতাম, ঠিক আছে, আমরা আনিস স্যারকে বলব। আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।
মনে আছে, ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হলে শুরুর সময়ে তখনকার কিছু জটিল রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে আনিস স্যার ও আমি গিয়েছিলাম বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেবের বাসায় কথা বলতে, তাঁকে সতর্ক করতে। তিনি শুনলেন, তবে সেসব নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাইলেন না। নানা বিষয়ে কথার পর প্রধান উপদেষ্টা আনিস স্যারের কাছে জানতে চাইলেন, কাকে প্রেস সচিব করা যায়? আনিস স্যার চটজলদি বললেন, মতিকে করেন। বিচারপতি স্যার কী বলেছিলেন, মনে নেই। তবে পরে জেনেছি, তিনি আমার নাম প্রস্তাব করেছিলেন সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে। কিন্তু একটি গোয়েন্দা সংস্থা এ-প্রস্তাবে সম্মতি দেয়নি। আমিও বড় বিপদ থেকে বেঁচে যাই।
বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়েছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এবং বিখ্যাত কলাম লেখক সৈয়দ আলী কবির। তখন আমরা ভোরের কাগজে। পরে প্রথম আলো অফিস বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের একটা বড় জায়গা হয়ে উঠেছিল। সুন্দর হাসিমুখে অফিসে এসে হাজির হলে পুরো পরিবেশই অন্যরকম হয়ে যেত। একই উষ্ণতা আর আন্তরিকতা নিয়ে নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সবার খোঁজ নিতেন। আমাদের সঙ্গে কফি খেতেন। কিছু খেতে জোরাজুরি করলে বলতেন, স্যান্ডউইচ খেতে পারি। তাঁর বাসায় যেতে বলতেন ভালো কফি খেতে। নিজ হাতে বানিয়ে নিজেই নিয়ে আসতেন। আপাদমস্তক একজন বাঙালি, কিন্তু একরকম সাহেবি আভিজাত্য ছিল।
আমাদের একজন কর্মী নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছিল, বিচারপতি স্যার এলে সবরকম সাহায্য যেন পান। প্রথমার জাফর আহমদের ওপর তাঁর বড় নির্ভরশীলতা ছিল। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান যে শনিবার রাতে মারা যান, তার দুদিন আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি নিজে এসে নাগরিকদের জানা ভালো বইয়ের ভূমিকা দিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর বেশ পরে ভাবি ইসলামা রহমান ও মেয়ে রুবাবা রহমান আনিস স্যার ও বেবী ভাবি, সাজ্জাদ শরিফ ও আসফিয়া আজিম, মালেকা ও আমাকে গুলশানে এক রেস্টুরেন্টে আপ্যায়ন করেছিলেন। এখনো তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আন্তরিক। বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও আনিস স্যার মিলে আইন-শব্দকোষ (২০০৬) নামে বাংলায় একটি আইন অভিধান সংকলন করেছিলেন। প্রথমা প্রকাশন থেকে তাঁর দশটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।
বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান প্রসঙ্গে আনিস স্যার লিখেছেন, শুধু ভাষা নয়, জীবনের নানা দিকেই তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। তিনি প্রকৃতই জীবনরসিক ছিলেন, আর ছিলেন উদার। মাতৃভাষাকে ভালোবেসে অন্য ভাষার মর্যাদা দিতে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগী হয়েও অন্য ধর্মের বিষয়ে ছিলেন বদান্য। বাংলাদেশকে স্বদেশ মেনে তিনি ছিলেন বিশ্বনাগরিক।
তবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের জীবনে সবচেয়ে বেশি কার প্রভাব ছিল, এ প্রশ্নের জবাবে আনিস স্যার একদিন আমাকে মুনীর চৌধুরীর নাম বলেছিলেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি। আনিস স্যার লিখেছেন, ছাত্র হিসেবেই তাঁর হৃদয়ের খুব কাছাকাছি আসার সৌভাগ্য হয়েছিল। আরো লিখেছেন, একমাত্র শিক্ষক, ক্লাসের বাইরে যাঁকে স্যার না বলে মুনীর ভাই বলে ডাকতাম। মুনীর চৌধুরীর ক্লাসে পড়ানো নিয়ে আনিস স্যার লিখেছেন, প্রমথ চৌধুরীর নীললোহিতের মতো তিনিও শুধু মুখে কথা বলতেন না, ‘তাঁর হাত, পা, বুক, গলা সব একত্র হয়ে একসঙ্গে বলত।’
মুনীর চৌধুরী মালেকার খালাতো ভাই। আমাদের বিয়ের পর ১৯৭০ সালের জুলাই বা আগস্টের কোনো এক সন্ধ্যায় মুনীর ভাইয়ের বাসায় গিয়েছিলাম। নানান গল্প করে চা-নাশতা খেয়ে ফিরে এসেছিলাম। তাঁর কাছ থেকে ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার একটি নাটকের বই পড়তে এনেছিলাম। তারপর আর দেখা হয়নি। তবে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগের মাসগুলোতে মুনীর ভাই বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণাধীনের স্বপক্ষে ছিলেন। ওই আন্দোলনের দিনগুলোতে মালেকা তাঁর কাছ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির জন্য চাঁদা নিয়ে আসত। আনিস স্যার লিখেছেন, এই আন্দোলন সম্পর্কে মুনীর চৌধুরী যে কতটা উৎসাহী ছিলেন, তা আমরা যারা কাছাকাছি ছিলাম, তারাই জানি।
একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা যখন আগরতলায়, তখন একদিন মুনীর ভাইয়ের বড় ছেলে আহমদ মুনীর (ভাষণ) আমার কাছে এসে কীভাবে তাঁকে ঢাকা থেকে বের করে আনা যায়—সে-বিষয়ে কথা বলেছিল। এ নিয়ে আনিস স্যারের মুনীর চৌধুরী বইয়ে কিছু কথা আছে।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুনীর চৌধুরী ঢাকায় পিত্রালয়ে থেকে গেলেন। স্ত্রী লিলি চৌধুরী, সন্তান ও অনেক শুভানুধ্যায়ীর অনুরোধ সত্ত্বেও দেশ ত্যাগ করলেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন। এর মধ্যে একাত্তরের ১ সেপ্টেম্বরও তাঁর কাছে লে. জে. টিক্কা খানের চিঠি গেল, ভবিষ্যতে ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ কোনো কাজে অংশ নিতে সাবধান করে। শেষ পর্যন্ত ‘জীবনে নিরাপদ’থাকতে চেয়েও পারলেন না। পাকিস্তানিরা মুনীর চৌধুরীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। আর আনিস স্যার লিখলেন, ট্র্যাজেডি যাঁর স্বভাবের অনুকূল ছিল না, সেই মানুষটি শেষ পর্যন্ত হলেন ট্র্যাজেডির মহানায়ক।
সাত
আনিস স্যার ২০০৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বাভাবিক নিয়মে অবসর নিয়েছিলেন। এরপর সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক, এমেরিটাস অধ্যাপক ও জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন শেষ পর্যন্ত। অবসর গ্রহণের আগেই আমি খুব বেশি না ভেবে স্যারকে প্রস্তাব করলাম, আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে থাকবেন। একসঙ্গে কিছু করব। এই প্রস্তাবে স্যার একধরনের সম্মতি দিলেন। এর কিছুদিন পর ফোন করে সন্ধ্যার পর ঈশা খাঁ রোডের বাসায় যেতে বললেন। বাসায় একথা-সেকথা হওয়ার পর আমার প্রস্তাবের কথা স্মরণ করে বললেন, আবুল খায়ের (লিটু) তাঁকে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে যোগ দিতে বলেছেন। আমি তখনই স্যারকে লিটুর প্রস্তাবে আমার সম্মতির কথা বলি। স্যারের মতও সেদিকে ছিল। সবদিক থেকে তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল। এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সঙ্গে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাকের যুক্ততার বিষয়টিও কাজ করেছে।
আনিস স্যার ২০০৪ সালের এপ্রিলে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনে যোগ দিয়েছিলেন। বিগত দেড় দশকে স্যারের কাজ যে বিস্তৃতি পেয়েছিল, সেটি সেখানে থাকাতে সহজ হয়েছিল। স্যারও সাধ্যমতো ‘কালি ও কলম’ এবং অন্যান্য প্রকাশনায় অনেক সাহায্য করেছিলেন। সপ্তাহে দুদিন তিনি নিয়মিত অফিসে যেতেন। বেঙ্গল ফাউন্ডেশন যেভাবে স্যারকে কাজ ও কাজের বাইরে সহায়তা করেছে, সেটা অনেক বড় ব্যাপার ছিল।
আট
প্রথমে আমাদের ভোরের কাগজ ও পরে প্রথম আলোর সঙ্গে আনিস স্যারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তা অব্যাহত ছিল শেষ সময় পর্যন্ত। তাঁর জীবনের শেষ লেখাটি লিখেছেন প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় এ-বছরের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ‘মুজিববর্ষে স্বাধীনতা দিবস’ শিরোনামে। লেখালেখির ব্যাপার তো ছিলই, এর বাইরেও ছোট-বড় অনুষ্ঠান বা নানা কাজে তিনি চলে আসতেন আমাদের অফিসে। আমরাও যেতাম তাঁর কাছে। তাঁর সব লেখার প্রুফ দেখার জন্য সময় জানিয়ে ঠিক চলে আসতেন অফিসে। এক কাপ কফি খেয়ে প্রুফ দেখে গল্প করে ফিরে যেতেন।
বেশ কয়েকবার এমন হয়েছিল যে দেশে বা বিদেশে কোনো লেখা প্রকাশের জন্য পাঠাবেন কিংবা বড় লিখিত বক্তৃতা করবেন; তিনি বইপত্র ও নিজের লেখালেখি নিয়ে প্রথম আলো অফিসে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লিখতেন, কম্পোজ হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রুফ দেখতেন। শেষ পর্যন্ত থেকে পুরো বক্তৃতার প্রিন্ট কপি নিয়ে বাসায় যেতেন। এটা হয়েছে বেশ কয়েকবার। রাত গভীর হয়ে যেত। ফিরে যেতেন কখনো কখনো রাত ১২টা বা তারও পরে। আমার কাজ শেষ হয়ে গেলেও স্যারের জন্য থেকে যেতাম। চা-কফি বা অন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতাম। খুব একটা খেতে চাইতেন না। স্যারের জন্য এটুকু যত্ন করতে পেরেছি বলে এখন ভাবতে ভালো লাগে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে এখন চোখ ভিজে যায়।
নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকেই আনিস স্যার অতীতের নানা কর্মকাণ্ড, বিচিত্র অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিমানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব অথবা মেলামেশার স্মৃতি যখন বলতেন বা লিখতেন, তখন অবাক হতাম। কোনো ডায়েরি নেই, কীভাবে তিনি এত কিছু মনে রাখেন! নানা সময়ে আমরা তাঁকে বলতাম স্মৃতিকথা লিখতে। তো শত ব্যস্ততার মধ্যে আসলে স্যারের সময় ছিল না। এরকম কথাবার্তা হতে হতে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের রজতজয়ন্তী সামনে রেখে ১২ এপ্রিল থেকে ২৭ নভেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত ভোরের কাগজের সাহিত্য সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে লেখা শুরু করলেন আমার একাত্তর। বহু রকম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি লিখেছেন। আর সবকিছু ঠিকঠাকমতো দেখে ছেপেছেন ভোরের কাগজের সাহিত্য সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ। আমার একাত্তর ছাপার শুরু থেকেই আনিস স্যার পাঠকের কাছ থেকে বেশ সাড়াও পেয়েছিলেন। পরে দ্রুতই ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে মফিদুল হকের সাহিত্য প্রকাশ থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। পাঁচটি মুদ্রণ হয়েছে বইটির।
এভাবে আমার একাত্তর বের হওয়ায় আনিস স্যার বেশ উৎসাহিত বোধ করলেন। তারপর দ্রুত তিনি ভোরের কাগজেই শুরু করলেন কাল নিরবধি—স্মৃতিকথার প্রথম খণ্ড। লিখেছিলেন আমার একাত্তর বইটির পরে, কিন্তু এর বিষয় তাঁর আগের জীবনপর্ব, একাত্তরের ২৫ মার্চ পর্যন্ত। প্রথম আলোর শুক্রবারের সাময়িকীতে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৯৮ থেকে ৮ মার্চ ২০০২ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি পক্ষে কাল নিরবধি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। সে-সময় পাঠকের মনে অনেক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল এই ধারাবাহিক নিয়ে। স্যারকে অনেকে ফোন করতেন, চিঠি লিখতেন, আবার কেউ কেউ কোনো বিষয়ে বিতর্ক তুলতেন—এমনও হয়েছে। এভাবেই এই ধারাবাহিকও শেষ হলো। পরে কাল নিরবধি বইও প্রকাশিত হলো সাহিত্য প্রকাশ থেকে। এটিও প্রকাশিত হয়েছিল সেই ফেব্রুয়ারি মাসে, ২০০৩ সালে।
আনিস স্যার তাঁর স্মৃতিকথা কাল নিরবধির ভূমিকায় লিখেছেন, ‘আমার একটা পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিকথার প্রথম প্রস্তাব আসে ডা. সারোয়ার আলীর কাছ থেকে। যে বীজ সে রোপণ করে, তাতে পানি ঢালে মতিউর রহমান, সাজ্জাদ শরিফ ও মফিদুল হক।’
এই দুটি ধারাবাহিক স্মৃতিকথা লেখার আগে ভোরের কাগজের সাহিত্য সাময়িকীতে ‘আমার চোখে’ শিরোনামে বেশ কিছু লেখা ছাপা হয়েছিল। পরে সেগুলো এবং আর কিছু লেখা যোগ করে বই প্রকাশিত হয়েছিল আমার চোখে।
আনিস স্যার আবার নতুন করে তাঁর স্মৃতিকথার দ্বিতীয় খণ্ড বিপুলা পৃথিবী লিখতে শুরু করলেন প্রথম আলোতে। সেটি প্রকাশ হলো ২৩ এপ্রিল ২০০৪ থেকে ৭ নভেম্বর ২০০৮ সাল পর্যন্ত। তাঁর স্মৃতিকথার দ্বিতীয় অংশ শেষ হলো ২০০০ সালে এসে। ইচ্ছে ছিল ২০০৭ পর্যন্ত লিখবেন। সেটা আর হয়ে ওঠেনি। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, ‘বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেও যখন দেখা গেল পরিত্যক্ত সূত্র আর কুড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে না, তখন ঘটনাকালের সমাপ্তি ২০০০ সালেই টানলাম।’ কথা ছিল বইটা প্রথমা বের করবে। আনিস স্যার সময় পান না। আবার পুরোটা গুছিয়ে দিলেন। পুরো বইয়ের প্রুফ দেখলেন। শেষ পর্যন্ত বিপুলা পৃথিবী বই আকারে বের হলো ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলায়। এই বই প্রকাশে জাফর আহমদের এক বড় ভূমিকা ছিল। বইটি কলকাতার ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’র বছরের সেরা বই হিসেবে পেল আনন্দ পুরস্কার। আমরা ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। বিপুলা পৃথিবী চার বছরের মধ্যে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সপ্তম মুদ্রণ হলো।
আমাদের প্রথমা থেকে স্যারের প্রথম বই বেরিয়েছিল চেনা মানুষের মুখ। এই বইয়ের নিবেদনের শুরুতেই তিনি লিখেছিলেন, ‘এই বইয়ে যে আটাশজন নর-নারীর আলেখ্য নির্মাণের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সবাইকে আমি চিনতাম। তবু এ বই তাঁদের সান্নিধ্যের বিবরণী নয়, আবার নিরবচ্ছিন্নভাবে সকলের কৃতির বিবরণও এতে নেই।’ এই আটাশজনের মধ্যে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আব্দুর রাজ্জাক থেকে আখতার ইমাম, মধুসূদন দে (মধুদা), গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও সেলিনা বাহার জামান পর্যন্ত আছেন। বড় লেখাগুলোর আট-নয় পৃষ্ঠা, ছোটগুলো তিন পৃষ্ঠা পর্যন্ত। কিন্তু প্রতিটি লেখাতেই প্রত্যেকের জীবন ও কাজের মর্মকথা অতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নিয়ে উপস্থাপন করেছেন। চেনা মানুষের মুখ বইটি বের হয়েছিল ২০১৩ সালের বইমেলায়। দুটি মুদ্রণ হয়েছে বইটির।
আনিস স্যারের শেষ বইটি সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি : দশটি বক্তৃতা আমরা প্রথমা থেকে বের করেছিলাম ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে। বেরোনোর আগে ১০-১২ বছরে যেসব লিখিত বিশেষ বক্তৃতা করেছেন, সেগুলোর একটি সংকলনগ্রন্থ এটি। বইয়ের প্রথম ও শেষের দুটি বক্তৃতা ছাড়া বাকিগুলো অধ্যাপক ইবরাহীম খাঁ, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দীন আহমদ, মিসেস নূরজাহান মুরশিদ ও প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ প্রমুখকে নিয়ে। প্রথম বক্তৃতাটি ‘বাংলার মুসলমানের পরিচয় বৈচিত্র্য’; অপর দুটির একটি হলো ‘বাংলাদেশের সংবিধান’ ও অন্যটি ‘আমরা কি এক সংকটের মুখোমুখি?’ আসলেই সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি : দশটি বক্তৃতা থেকে এসব বিষয়ে স্যারের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গির অনেকটাই আমরা দেখতে পাই। এভাবে চেনা মানুষের মুখ ও সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি : দশটি বক্তৃতা (প্রথমা) বইদুটির মতো বেঙ্গল পাবলিকেশন্সের সংস্কৃতি ও সংস্কৃতি-সাধক গ্রন্থটি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে ছয়টি এবং ১৪ জন কবি, লেখক, শিল্পী—জসীমউদ্দীন, সুফিয়া কামাল, আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর প্রমুখকে নিয়ে লেখা। আমার চোখে (অন্যপ্রকাশ) বইয়ে ২০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিমানুষ—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন থেকে শুরু করে সিরাজুদ্দীন হোসেন এবং আট-দশটি নানা বিষয়ে নাতিদীর্ঘ লেখা রয়েছে। এর বাইরে সমাজের নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট চৌত্রিশজনকে নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলো একত্র করে চন্দ্রাবতী একাডেমি থেকে বের হয়েছে স্মরণ ও বরণ। ইতিহাসের নানা সময়ের ঘনিষ্ঠ জড়িতদের নিয়ে খণ্ড খণ্ড বিশেষ ব্যক্তির ভূমিকা নিয়ে লেখাগুলো। সব মিলিয়ে এই বইগুলোর লেখাগুলো পড়লেই দেশের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নয়, ভবিষ্যতে আমাদের করণীয় নিয়ে অনেক কাজ সামনে চলে আসে। এসবের সঙ্গে স্যারের আমার একাত্তর এবং দুই খণ্ডের স্মৃতিকথা পড়লে একজন অত্যন্ত সক্রিয় গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও মানবিক মানুষের প্রতিকৃতিই ভেসে ওঠে।
তবে প্রথমা থেকে ওপরে উল্লিখিত আনিস স্যারের লেখা তিনটি বই প্রকাশ পেলেও প্রথম বই বের হয়েছিল তাঁর সম্পাদনায় রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে। প্রথম আলোর উদ্যোগে ২০১১ সালের ১৮ ও ১৯ জুন দুদিন ধরে আটটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বড় আয়োজন করে আলোচনা হয়েছিল। সহযোগিতা করেছিল ব্র্যাক ব্যাংক। দেশের বিশিষ্ট প্রায় ৪০ জন কবি, লেখক, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞ আলোচনা করেছিলেন। আনিস স্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন, একটি অধিবেশনে সভাপতি হিসেবেও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। তাঁর আলোচনা শুরু হয়েছিল এভাবে, ‘এই সেমিনার সম্পর্কে প্রথম আলো থেকে আমার কাছে একটি কাগজ এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে—পত্রপ্রেরক আনিসুজ্জামান, পত্রপ্রাপক অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।’
অর্থাৎ, এই পুরো আয়োজনের আহ্বায়ক ছিলেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, যিনি সবসময় নিজেকে আনিসুজ্জামান হিসেবে পরিচয় দিতেই খুশি হতেন। দুদিন ধরে যত আলোচনা হয়েছে, তা সব দেখে আনিস স্যারের নাতিদীর্ঘ ভূমিকাসহ রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে বইটি বের হয়েছিল ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, বইমেলায়। স্যার এই বই প্রকাশ ও পুরো ব্যবস্থাপনায় সাজ্জাদ শরিফের কথা বিশেষভাবে বলেছেন। আমার কথাও বলেছেন। সেটা ছিল স্নেহের প্রকাশ।
২৩ মার্চ ২০১৮ থেকে ১৯ জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত আনিস স্যার প্রথম আলোর শুক্রবারের সাময়িকীতে ‘আমার অভিধান’ বলে ধারাবাহিক শুরু করেছিলেন। প্রতি শুক্রবার একটি প্রচলিত (প্রায়শ ভুল অর্থে ব্যবহৃত) শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ নিয়ে সামান্য কয়েকটি বাক্যে লিখতেন। স্যারের ইচ্ছা ছিল, এরকম ১০০ শব্দ লিখবেন। পরে বললেন, ৮০টি করবেন। ৬২টি শব্দ নিয়ে লেখার পর আর পারলেন না। শেষ পর্যন্ত ৬২টি শব্দ নিয়ে ছোট একটি বই করার জন্য পুরোটাই স্যারকে পাঠিয়েছিলাম। সেটাও দেখে দিতে পারলেন না।
মনে পড়ে, ২০০৯ সালে বেশ কিছুদিন ভেবেচিন্তে আমরা ঠিক করলাম একটি প্রকাশনা সংস্থা করব। অরুণ বসুকে নিয়ে কিছু কাজ শুরু করে দিলাম। কথা এলো, এর নাম কী হবে? আবার সেই আনিস স্যার। তিনি আমাদের প্রকাশনার নাম দিলেন প্রথমা। প্রথম আলো থেকে প্রথমা। সেই থেকে আমাদের প্রথমা প্রকাশনার কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথম বই বের হলো একাত্তরের চিঠি। বইটির ৩৮ মুদ্রণ হয়েছে।
নয়
আসলে নানাভাবেই আনিস স্যার প্রথম আলোর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলেন অথবা আমরা তাঁকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। আমাদের যেকোনো ভালো কাজ বা উদ্যোগের সঙ্গে তিনি সহজেই যুক্ত হতেন। সময়ও দিতেন তিনি। প্রথম আলো বর্ষসেরা বই পুরস্কার শুরু করলাম এপ্রিল, ২০০৩ সাল থেকে। তো স্বাভাবিকভাবে তিনিই হলেন পরামর্শক। সেরা বই কীভাবে নির্বাচিত হবে বা পুরস্কার কমিটির জন্য নির্দেশনার বিষয়গুলো তাঁর সাহায্য নিয়েই চূড়ান্ত হয়েছিল। ২০০৬ ও ২০০৭ এবং ২০১১ ও ২০১২ সালে—দুবার দুই বছর করে মোট চারবার বিচারকমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন। স্যার খুবই গোছানোভাবে বই নিয়ে আলোচনা করে পরিষ্কার মতামত দিতেন। সবটাতেই তাঁর অবস্থান ছিল বিশেষ করে যা বলার, তা সীমিত, মার্জিত সীমার মধ্যে বলা।
আনিস স্যার দেশব্যাপী কিশোর-তরুণ ছাত্রদের জন্য আমাদের ‘ভাষা প্রতিযোগ’-এর আহ্বায়ক ছিলেন, যার শুরু এপ্রিল, ২০০৫ সাল থেকে। শেষ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্বে ছিলেন। আর, কমিটির বৈঠকে নানা পরামর্শ দিতেন আন্তরিকভাবে। ‘ভাষা প্রতিযোগ’ নামটাও তাঁর দেওয়া। স্যারের ভাবনা ছিল, যারা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে, একই অর্থের সহজ আরেকটি শব্দ ‘প্রতিযোগ’ তারা শিখে ফেলবে। ভাষা প্রতিযোগের স্লোগানটিও তাঁর দেওয়া—‘বাংলা ভাষায় কাঁদি-হাসি/ সকল ভাষা ভালোবাসি।’
২০১১ সালে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজবিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘প্রতিচিন্তা’ বের করলে অন্যদের সঙ্গে উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য থাকতে সম্মত হয়েছিলেন আনিস স্যার। একাধিক বৈঠকেও এসেছিলেন।
মনে পড়ে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় ভূমিকা রাখতে আমরা একটি সাহিত্যপত্রিকা করেছিলাম—‘গণসাহিত্য’—বর্তমানে ‘কালি ও কলম’–এর সম্পাদক এবং আমার বাষট্টি বছরের বন্ধু আবুল হাসনাত সম্পাদক। মফিদুল হক ও আমিও ছিলাম এর সঙ্গে। এখানে উপদেষ্টা হিসেবে অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সঙ্গে ছিলেন কবি শামসুর রাহমানও। এভাবে কত কিছুতে আনিস স্যার আমাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন! ‘গণসাহিত্য’ পত্রিকার পেছনে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি।
এখানে ছোট্ট একটি তথ্য যোগ করতে আমার ভালো লাগছে যে, একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি আনিস স্যার তাঁর হালকা নীল রঙের ভক্সওয়াগন গাড়িটি কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে শফিউলের (পরে ডাক্তার, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী) হাতে দিয়ে গেলেন। মুক্তিযুদ্ধের কাজে গাড়িটি ব্যবহৃত হয়েছে পুরো সময়জুড়ে।
শিক্ষকতা ও লেখালেখির বাইরেও স্যার আমাদের সঙ্গে নানা উদ্যোগে যুক্ত থাকতেন। সেসব ভাবতে গিয়ে আজ অবাক হই। আসলে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো উদ্যোগের কথা মনে হলে স্যারের কথাই সবার আগে মনে হতো। এভাবেই তিনি সবার কাছে অত্যন্ত যোগ্য এক আসনের জন্য সবচাইতে গ্রহণীয় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। এজন্য সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু আবুল মোমেন সব সময় বলেন, ‘একজনের ভূমিকা ছাপিয়ে দশজনের ভূমিকায়।’
দশ
আনিস স্যার আমাদের সঙ্গে আরেকটি কাজ করেছেন; সেটিও করেছেন সতেরো বছর ধরে। সেটি ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় জমকালো তারকাখচিত ‘মেরিল-প্রথম আলো তারকা জরিপ’ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান ভোরের কাগজের সময় থেকেই শুরু হয়েছিল, তবে ১৯৯৮ সালে প্রথম আলো শুরু হলে তার পরের বছর থেকে আবার নতুন করে শুরু করি। এই অনুষ্ঠান তিন বছর চলার পর ২০০২ সাল থেকে নতুন একটি পুরস্কারের সিদ্ধান্ত নিই আমরা, সেটা হলো আজীবন সম্মাননা পুরস্কার। সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা সারাজীবন চর্চা করেছেন, বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন, সে-সম্মাননা ছিল তাঁদের জন্য। এই পুরস্কার নির্বাচনের জন্য যাঁরা সক্রিয়ভাবে কাজ করতেন, তাঁদের মধ্যে আনিস স্যার ছিলেন প্রধান। এই সতেরো বছর ধরে স্যার আমাদের সঙ্গে বসে ও আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দিতেন। তাঁর সঙ্গে আরো যাঁরা বিভিন্ন সময়ে যুক্ত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী, নীলুফার ইয়াসমিন, রামেন্দু মজুমদার, সেলিনা হোসেন, আসাদুজ্জামান নূর, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা প্রমুখ।
আমাদের মধ্য থেকে সাজ্জাদ শরিফ, আনিসুল হক আর আমি থাকতাম। এই আলোচনাটি আমরা সবসময়ই করতাম হোটেল সোনারগাঁওয়ের ঝরনা রেস্তোরাঁয়। স্যার তো ঠিক সময়ে আসতেন, অন্যদের কেউ কেউ দেরি করতেন। আমাদের আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খেতে খেতে অনেক মজার গল্প হতো। সেসবই ছিল শুধু আনন্দের।
আমরা জানি, স্যার খেতে ভালোবাসতেন। কোনো সালাদ নয়, স্যুপ খেতেন, তারপর হয়তো বিফ স্টেক না-হয় বড় গলদা চিংড়ি গ্রিল। আবার ফল নয়, পছন্দ করতেন মিষ্টি। বিশেষ পছন্দ ছিল ক্রিম ক্যারামাল। শেষে এক কাপ কফি। প্রতিবার সবার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যেতেন গেট পর্যন্ত। আমরা তাঁর সঙ্গে। গাড়িতে উঠে হাত নেড়ে বিদায়হ নিতেন। সেসব দৃশ্য মনে করে এখনো বড় বেশি বেদনা হয়। আর কোনোদিন এমন হবে না। আমরা এখন কাকে নিয়ে এমন কিছু করব—খুঁজে তো পাই না।
এগারো
সেই ষাটের দশকের পর ধীরে ধীরে সত্তর পেরিয়ে আশি, তারপর নব্বইয়ে ভোরের কাগজ ও প্রথম আলোর শুরুর পর্যায়ের পর বিগত দুই দশকে আনিস স্যারের সঙ্গে যতটা আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, সেটাই আমার জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা হয়ে আছে এবং থাকবে। প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনে আনিস স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ যেমন প্রায় নিয়মিত ছিল, অন্যদিকে মুঠোফোনে মালেকার সঙ্গে বেবী ভাবির কথাবার্তা প্রায় প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে উঠেছিল, যা এখনো অব্যাহত।
এভাবেই জানতে পেরেছিলাম যে এই দশকের মাঝামাঝি থেকে স্যার বেশ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সে-সময় থেকেই স্যারের চিকিৎসাব্যবস্থাদির সঙ্গে কিছুটা জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। তখন হৃদ্রোগের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। ভুল না হলে ২০১৪ সালে এজন্য ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি হলেন। সেবারই চিকিৎসাব্যবস্থার মধ্যে ছিল হৃৎপিণ্ডে স্টেন্ট লাগানো। সেটা সফলভাবে হয়েছিল। ওই হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার শামীম আহমেদ; আমাদের সঙ্গে বেশ জানাশোনা। আনিস স্যার তাঁর হাসপাতালে আছেন জানতেই সেবার চিকিৎসার পুরো দায়িত্ব তিনি নিয়েছিলেন। এরপরও তিনি বেশ কয়েকবার হাসপাতালে গেছেন। সে-সময় আনিস স্যারের খোঁজখবর নিতে গেছি। তবে ২০১৭ সালে যখন বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ল্যাবএইডের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে দীর্ঘ চিকিৎসা নিলেন। সেখানেই তাঁর মেরুদণ্ডের গুরুতর সমস্যা ধরা পড়ল।
আবুল খায়ের সেবার আনিস স্যার ও তাঁর পরিবারের সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নিলেন। আমরা দুজন মিলে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে স্যারের চিকিৎসার ব্যবস্থাপনার কাজটি করেছিলাম। বেশ দীর্ঘ সময় চিকিৎসা হলো; মেরুদণ্ডের অপারেশন হলো। সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন ঢাকায়। তিনি সামান্য ঝুঁকে গিয়েছিলেন বলে মনে হলো। তারপর থেকে স্যারকে দেখলেই মনটা খারাপ হয়ে যেত। মনে আছে, সুস্থ হয়ে ফিরে আসার পর তিনি আমাদের খাইয়েছিলেন এক রেস্তোরাঁয়। স্যারের পরিবার, আবুল খায়েরের পরিবারের প্রায় সব সদস্য ও আমরা। তাঁর সঙ্গ তো যে-কোনো জায়গা বা অবস্থায় আনন্দের ছিল। এরপর স্যার বেশ দ্রুত আরো সুস্থ হয়ে গেলেন। আবার ফিরে গেলেন দৈনন্দিন রুটিনে। ২০১৮ সালের পুরোটাই বেশ ভালো ছিলেন। তারপর ২০১৯ সালের মধ্যভাগ থেকে আবার অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলেন।
২০১৮ সালের শেষে বা ২০১৯ সালের শুরুতে আনিস স্যারকে নিয়ে আমরা একটা বক্তৃতা অনুষ্ঠানের কথা ভেবেছিলাম—তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা আর বাংলাদেশ নিয়ে। সে-অনুষ্ঠানে দেশের সেরা মানুষের একটা জমায়েত করে স্যারকে আমরা শুভেচ্ছা জানাব। স্যার এ-প্রস্তাবে একরকম সম্মতিও দিলেন। বারকয়েক কথা হলো। তো এভাবে সময় চলে গেল। শেষ পর্যন্ত বিগত সেপ্টেম্বরে একদিন দুপুরে দুজন কথা বলব বা গল্পসল্প করব, সেভাবে হোটেল সোনারগাঁওয়ে সময় ঠিক হলো। স্যারের সঙ্গে দেখা হলো, কথাও হলো অনেক। একসময় সেই বক্তৃতা অনুষ্ঠানের কথা বললাম। স্যার বললেন, মতি, আমি আর পারব না। বুঝতে পারলাম, স্যার আর পেরে উঠবেন না। সময়ের নানা বিষয় নিয়ে কথা বললাম। খাওয়া হলো, কফিও খেলেন। অন্য সময়ের মতো প্রাণবন্ত গল্প হলো না। স্পষ্ট বোঝা গেল, বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছেন। স্যারকে বিদায় দিতে হেঁটে হেঁটে গাড়িবারান্দায় গেলাম। গাড়িতে উঠে হাত নেড়ে চলে গেলেন। মনে পড়ে, বেশ বিষাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম সেই অপরাহ্ণে।
তারপর গত বছরের ২৬ নভেম্বর প্রথমার নতুন বই সন্জীদা খাতুনের শান্তিনিকেতনের দিনগুলির প্রকাশনা উৎসব করলাম বেঙ্গল শিল্পালয়ে। সন্জীদা খাতুনের সঙ্গে আনিস স্যারও মঞ্চে বসলেন। কথা বললেন, পরে গান শুনলেন। সেদিনের জমায়েতটা খুব ভালো ছিল। অনেক বিশিষ্টজন এসেছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলেও অনেকক্ষণ থাকলেন স্যার। পুরো সময়টা তিনিও উপভোগ করলেন। তারপর যেমন করেন, একে একে সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সেটাই আমাদের সঙ্গে স্যারের শেষ অনুষ্ঠান।
এখন এটা ভাবতে ভালো লাগে যে, গত বছরের জুলাইয়ের শুরুতে বেবী ভাবিকে গান শুনতে কলকাতার সারেগামার ক্যারাভান (পাঁচ হাজার গানসহ রেডিওর মতো একটি বিশেষ যন্ত্র) পাঠিয়েছিলাম। তার মধ্যে ভারতের সেরা গায়ক-গায়িকাদের দুই হাজার রবীন্দ্রসংগীত রয়েছে। আরো অনেক গান ছিল। বেবী ভাবি আর স্যার সকাল বা রাতে খাবারের আগে-পরে রবীন্দ্রসংগীত শুনেছেন। এটা জেনে আমাদের খুব ভালো লেগেছিল।
বারো
প্রথম আলোর সম্পাদকীয় নীতির জন্য সরকারের সঙ্গে দূরত্ব হয়েছে। সেজন্য প্রথম আলোকে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পথ চলতে হচ্ছে। কখনো আমরা হয়রানিরও শিকার হয়েছি। এমনকি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশিত সংবাদকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের মামলা হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। এ নিয়ে আনিস স্যার খুব উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেগে থাকতেন।
এসবের মধ্যে আমি স্যারের বাসায় গেলাম। তখন তিনি কিছুটা অসুস্থ। পুরো ঘটনা তাঁকে বললাম। তিনি সব শুনলেন, দুঃখ পেলেন। আরো কিছু কথা হয়েছিল। এখন সেসব আর মনে নেই। বিদায় দিতে তিনি লিফট পর্যন্ত এলেন। কাঁধে হাত রেখে বললেন, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। স্যারের সঙ্গে বাসায় এই আমার শেষ কথা।
তারপর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে স্যার বেশ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুবার ল্যাবএইড হাসপাতালে গেলেন। এর মধ্যে করোনা ও নানা ঝামেলায় স্যারের কাছে যেতে পারলাম না। তারপর তো ২৭ এপ্রিল ইউনিভার্সেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হলেন।
শুনছিলাম শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়ছে। ৩০ এপ্রিল সচিবালয়ে এক বৈঠকের পর সরাসরি হাসপাতালে চলে গেলাম। বন্ধু ডাক্তার আশিস চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে গেলেন স্যারের কেবিনে। বেবী ভাবি ছিলেন সেখানে। স্যার শুয়ে আছেন, শরীরের নানা জায়গায় ইসিজি মনিটরের লিড, পালস অক্সিমেট্রি, অক্সিজেন ও ক্যাথেটার ইত্যাদি শরীরে লাগানো ছিল। ভাবি স্যারের বিছানার কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, ‘দেখো, মতি এসেছে।’ স্যার ডান হাতটা সামান্য তুললেন, মাথা নাড়লেন। বুঝতে পারলাম, চিনেছেন। কিছু হয়তো বলার চেষ্টা করলেন। খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। এর মধ্যে ভাবি আর ডাক্তারকে বারবার বলছিলেন, ‘বাসায় যাব।’ ভাবি ছাড়াও ডাক্তার আশিস বোঝালেন যে আরেকটু সুস্থ হলেই বাসায় যেতে পারবেন।
ভাবি আমাকে বলছিলেন, ডাক্তার বা হাসপাতালে যাওয়ার ব্যাপারে স্যারের খুবই আপত্তি ছিল সবসময়। তারপরও দেশ-বিদেশে কতবার যে স্যারকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে, অস্ত্রোপচারসহ কত রকম চিকিৎসা নিতে হয়েছে! প্রতিবারই হাসপাতাল থেকে ফিরে নতুন করে আবার বহুমুখী কাজে লেগে পড়েছেন।
ফেরার সময় স্যারের বেডের কাছে আবার গিয়ে দাঁড়াই। বেবী ভাবি বলেন, মতি যাচ্ছে। স্যার আবার হাত তুলে বিদায় জানালেন। সেই বিদায় শেষ বিদায় হয়ে থাকল।
ইউনিভার্সেল হাসপাতাল থেকে সিএমএইচে নেওয়া হলো। যাওয়ার সময় স্যার ডা. আশিসকে বললেন, তোমরা আমাকে অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছ। ডা. আশিস বলেছিলেন, আপনার চিকিৎসার জন্য সবার সিদ্ধান্ত এটা। স্যার আর কিছু বললেন না। ডা. আশিস বলেন, দোয়া করবেন।
সেদিন বিকেলে হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরতে ফিরতে গভীর বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। বারবার কান্না চলে আসছিল। কত কিছু যে ভেবেছিলাম! বারবার মনে পড়ছিল নানা কথা, কত না স্মৃতি! ভাবছিলাম, স্যার আবার কবে বাসায় ফিরতে পারবেন? সত্যি কি বাসায় ফিরে যেতে পারবেন? আমার মধ্যে গভীর এক আশঙ্কা তৈরি হলো। সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধু আবুল হাসনাত আর আবুল খায়েরকে বললাম আমার আশঙ্কার কথা। এরপর নিয়মিতভাবে স্যারের চিকিৎসার খবরাখবর পেতাম ভাবির কাছ থেকে, মালেকার মাধ্যমে। ১৪ মে বিকেলে সেই দুঃসংবাদটি পেলাম যে আনিস স্যার আর নেই। কী আশ্চর্য, অমোঘ এক নিয়মে এই খবরও মেনে নিতে হয় আমাদের!
এ-সংবাদের কিছু সময় পর আবুল খায়ের ফোন করে কাঁদতে শুরু করলেন। অনেক কথা বললেন। তাঁর সঙ্গে স্যারকে নিয়ে রাত প্রায় দুটা পর্যন্ত অনেক কথা হলো। আনিস স্যার নিয়ে আমাদের কথা এ-জীবনে শেষ হবে না!
পরদিন সকালে আজিমপুর কবরস্থানে বাবার কবরে স্যারকে সমাহিত করা হলো। সঙ্গী হতে পারলাম না শেষযাত্রায়। স্যারের ছেলে, জামাতা ও ভাইসহ আবুল খায়ের এবং হাবীবুল্লাহ সিরাজী ছিলেন। অথচ প্রতিবার যেখানে স্যারের সঙ্গে দেখা হতো, সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতেন গেট পর্যন্ত, আমরা তাঁর সঙ্গে। গাড়িতে উঠিয়ে বিদায় নিতাম। এবার আনিস স্যার একাই সবকিছু ফেলে সবাইকে বিদায় না বলেই চলে গেলেন। এখন কেন জানি মনে হয়, স্যার এমন বিদায়ই কি চেয়েছিলেন?
বিগত এক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই স্যারের এই লেখা, সেই লেখা, কত মানুষকে নিয়ে কত লেখা, কত বিষয়ে কত বই, কত কাজ—সেসব নিয়ে পড়তে পড়তে, ভাবতে ভাবতে অবাক বিস্ময় জাগে মনে। কত কথা, কত স্মৃতি ভিড় হয়ে জমা হয় মনের গভীরে। এখনো এ বিষয়-সে বিষয় মনে হলে হঠাৎ ভাবনা আসে, স্যারকে ফোন করি, বাসায় চলে যাই বা কোথাও ডেকে আনি, কথা বলি, কিছুটা সময় কাটাই। নতুন কিছু শিখি, নতুন কিছু জানি। সে তো আর হবার নয়।
এতসব কিছুর পরও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন সাধারণ, একই সঙ্গে অসাধারণ। কবি শামসুর রাহমান এভাবেই কবিতায় লিখেছেন, ‘যখন পাঞ্জাবি আর পাজামা চাপিয়ে/ শরীরে সকালে কিংবা বিকেলে একলা হেঁটে যান/ প্রায় প্রতিদিন দীর্ঘকায় সবুজ গাছের/ তলা দিয়ে তাকে বাস্তবিক সাধারণ মনে হয়।’