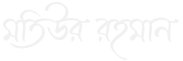বাংলাদেশে সত্যিকারের রেনেসাঁর সময় হলো ষাটের দশক
সাখাওয়াত টিপু: আপনার বাল্যকাল দিয়েই সাক্ষাত্কার শুরু করা যাক। ছেলেবেলা কেমন ছিল?
মতিউর রহমান: আমার পুরো জীবনটাই কেটেছে বলা যায় ঢাকা শহরের মধ্যভাগে—মানে পুরান ঢাকা আর নতুন ঢাকা। পুরান ঢাকা, একসময় নতুন ঢাকা—এরই মধ্যে আমার এই পঁচাত্তর বছরের জীবনটা কেটে গেল। সেই ছোটবেলা থেকেই বলা যায়, এক অর্থে বংশাল রোডে ছিলাম, পুরান ঢাকায়।
স্কুলে পড়েছি নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে। স্কুল-কলেজের ছাত্রাবস্থায় একটা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি পল্টন ময়দান আর স্টেডিয়ামে ঘোরাঘুরি বা খেলাধুলা করে। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির অফিস ছিল পুরানা পল্টনে। আবার আশির দশকে এসে সাপ্তাহিক একতার অফিস হলো বংশালে। আমি পড়লাম ঢাকা কলেজে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষাটের দশকের একটা বড় সময় কাটল হল-হোস্টেলগুলোতে।
পরের জীবনে সত্তর দশকের মাঝামাঝি, বংশাল থেকে আমরা গিয়েছি ওয়ারীতে, ওয়ারী থেকে ইস্কাটনে, ইস্কাটন থেকে লালমাটিয়ায়। সামান্য সময়ের জন্য ধানমন্ডিতে থেকেছি, আবার লালমাটিয়ায়। এখানেই জীবন শেষ হবে। এভাবে বলা যায়, পুরান ঢাকা আর নতুন ঢাকার মধ্যখানে এই পঁচাত্তর বছরের জীবনটা কেটে গেল। এটার একটা সুবিধা ভোগ করলাম যে, আমার কর্মস্থল ও বাসস্থল কখনো খুব দূরে ছিল না। এটা আমাকে অনেক স্বস্তি দিয়েছে।
আমার সবচেয়ে ভয় লাগে এই ঢাকার যানবাহন, যাতায়াত, দূর থেকে আসা-যাওয়া, অফিস-কর্মস্থল বাসার দূরত্ব। এখনো দেখি—আমার যে বন্ধুরা অফিসে আমাদের সঙ্গে কাজ করেন, কেউ উত্তরা থেকে আসেন, অনেকে আরেকটু দূর থেকেও আসেন। খুব কষ্ট হয়, মায়া হয়, ঢাকা শহরের যানবাহন সমস্যার এই যুগে। এইটুকু সুবিধা হয়তো পারিবারিক কারণে, বাসস্থান ও কর্মস্থলের কারণে, সাংবাদিক হওয়ার কারণে পেয়েছি।
পুরান ঢাকায় থাকার কারণে, পুরান ঢাকার সঙ্গে মিশে থাকার কারণে এবং জীবনের প্রায় তিন দশকের বেশি সময় থাকার কারণে পুরান ঢাকার প্রতি সর্বদা একটা গভীর ভালোবাসা, মমতাবোধ অনুভব করি। সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি ও মানুষ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার ছোটবেলার বন্ধুবান্ধবের একটা বড় অংশই পুরান ঢাকার অধিবাসী ছিল। আমার স্কুলের বন্ধুদের অনেকেই ছিল পুরান ঢাকার অধিবাসী। সেদিক থেকে পুরান ঢাকা আমার একটা ভালোবাসার জায়গা।
একবার স্থপতিদের একটা সম্মেলনে—অনেক আগে—আমাকে নিবন্ধ পড়তে বলা হয়েছিল। আমার বক্তৃতার শিরোনাম ছিল ‘একজন ঢাকাইয়া বলছি’। নিবন্ধের ভেতরে উল্লেখ ছিল, আমার নিজেকে ‘কুট্টি’ বলতে দ্বিধা নেই, এ রকম একটা আবেগ কাজ করে। বংশালের যেখানে থাকতাম, আর দৈনিক সংবাদের অফিসের মধ্যে দূরত্ব খুব কম ছিল। ভুল না হলে, দৈনিক সংবাদের ঠিকানা ২৬৩ বংশাল রোড, আর আমাদের বাড়ি ছিল ২৪০ নম্বর বংশাল রোড। সেই শৈশবকালে ক্লাস থ্রি না হলেও, চতুর্থ শ্রেণি থেকে ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ ছিল—সংবাদ অফিসের দেয়ালে সাঁটানো সংবাদ পত্রিকাটা পড়া। মূলত পেছনের পৃষ্ঠায় সেখানে খেলার সংবাদ থাকত, সেটাই পড়তাম। এভাবেই আমার দৈনিক সংবাদ পত্রিকার পাঠ শুরু।
বাসায় থাকত আজাদ পত্রিকা, বাবা রাখতেন। তাও দীর্ঘ সময় খেলার পাতাতেই আমার মনোযোগ ছিল। খেলার পাতা, খেলার খবর, সেটা ফুটবল, সেটা ক্রিকেট—যেকোনো খেলাই হোক। ক্রিকেট অত জনপ্রিয় ছিল না, ফুটবল অনেক জনপ্রিয় ছিল তখন। আবার পাশাপাশি আমি নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে ভর্তি হই ক্লাস থ্রিতে। এর আগে পড়েছি নবাবপুর রোডের একটি স্কুলে, যেখানে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ত। আমার ছোট বোন নাজমাও সেখানে পড়ত। তো বংশালে নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাস করি ১৯৬১ সালে। আমাদের স্কুল থেকে দশ মিনিটের রাস্তা পুরানা পল্টন। পল্টন ময়দান আর স্টেডিয়াম ওই সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যেত। বলা যায়, স্কুলজীবন পর্যন্ত জীবন ছিল বংশাল থেকে পল্টন ময়দান আর স্টেডিয়াম।
টিপু: পল্টন ময়দান বা স্টেডিয়ামে কেন আসতেন?
মতিউর: আমার খেলার প্রতি ভীষণ আগ্রহ ছিল। আমি সব খেলা দেখতাম। মাঠে খেলা দেখতাম, তাদের প্র্যাকটিস দেখতাম, ক্লাবে ক্লাবে ঘুরতাম, খেলোয়াড়দের পেছনে পেছনে ঘুরতাম। ক্রিকেট নেট প্র্যাকটিসে দূরে দাঁড়িয়ে বল তুলে খেলোয়াড়দের হাতে দিতাম। সব খেলাধুলার প্রতি আমার ভালোবাসা তৈরি হয়। ফুটবল তো অবশ্যই দেখতাম, ক্রিকেট দেখতাম, এমনকি ভলিবল প্রতিযোগিতা, সাঁতার প্রতিযোগিতা, পরে বাস্কেটবল এবং অ্যাথলেটিকসের প্রতিও আগ্রহ ছিল। তখন ইন্টার স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতা, ইন্টার স্কুল স্পোর্টস হতো। আমি ইউনিভার্সিটি খেলার মাঠেও যেতাম। ফজলুল হক হলের সুইমিংপুলে সাঁতার প্রতিযোগিতা বা স্টেডিয়ামে জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতাও আমি দেখতে গেছি। এ রকম একটা খেলার জগতের মধ্যে খুব নিমজ্জিত ছিলাম। ক্লাসে হাজির থাকা ছিল নামমাত্র। ক্লাস শেষ হওয়ামাত্র বাসায় গিয়ে আবার খেলার মাঠে চলে আসা, বন্ধের দিনে খেলার মাঠে কাটানো, মাঝে মাঝে কোনো খেলা দেখার জন্য স্কুল ফাঁকি দেওয়া... এসবই চলত। স্কুলের চেয়ে বেশি আকর্ষণ ছিল খেলার মাঠ। সেদিক থেকে পল্টন ময়দান আর স্টেডিয়াম ছিল সবকিছুর কেন্দ্র।
টিপু: স্কুলে কি আপনার পড়ালেখার প্রতি খুব অনাগ্রহ ছিল?
মতিউর: তেমন কোনো আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা করলাম না। শুধু স্কুল নয়, সেটা ধরুন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়েও। ভালো পড়তে হবে, শিখতে হবে, এমন কোনো আগ্রহ ছিল না। আমার বড় দুই ভাই ভালো ছাত্র ছিল। বাড়ির সবার আশা ছিল, হয়তো আমিও ভালোই পড়াশোনা করব। আসলে আমি পড়াশোনা করিনি। এটা এখনো খুব আফসোস হয়, শিক্ষাজীবনে পড়াশোনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এবং সেটা না করার জন্য তার ফল এখন ভোগ করি। সব সময় অনুভব করি যে, অনেক কিছু পারি না, জানি না, শিখিনি, পড়িনি। নিজে নিজে খুব পীড়িত বোধ করি, কষ্ট পাই। কারণ, পরবর্তী সময়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে গিয়েও পড়িনি। ফাঁকি দিয়েছি।
টিপু: তাহলে আপনার তো খেলার মাঠের প্রতি আকর্ষণ...
মতিউর: হ্যাঁ। তো সেই খেলার জগতে... ক্লাস এইট-নাইনে গিয়ে আসেত্ম আসেত্ম আমি ক্রিকেটের প্রতি বেশি আকর্ষণ বোধ করি। প্রায় প্রতিদিন এই নেট প্র্যাকটিস দেখতে যাই। ভিক্টোরিয়া ক্লাবের তত্কালীন ক্যাপ্টেন, এখনো খুব মনে পড়ে আব্দুস সালাম, তাঁর অভয়ে আমি নেট প্র্যাকটিসে যোগ দিই। ক্লাস নাইন-টেন থেকে আমি ভিক্টোরিয়া ক্লাবের হয়ে খেলতে শুরু করি, স্কুল টিমে আর কলেজ টিমেও। ভিক্টোরিয়া ক্লাবে আমি একনাগাড়ে ছয়-সাত বছর খেলেছি। শেষ দুই বছর ভিক্টোরিয়া ক্লাবের ক্রিকেট টিমের অধিনায়কও ছিলাম।
নিজে খেলা, একই সঙ্গে খেলা দেখা। আমার মনে আছে, ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের খেলা, ১৯৫৫ সালের শেষ দিনের শেষবেলা, খেলা দেখতে ভিড় ঠেলে, টিকিট ছাড়া স্টেডিয়ামে ঢুকে যাই বড় ভাইয়ের সঙ্গে। পরের বছর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা, পরের বছর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা, তারপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা—এই টেস্টগুলো দেখেছি। তখন বাসায় একটা রেডিও ছিল মারফি, রেডিওতে বড় বড় ক্রিকেট খেলার ধারাভাষ্য শুনতাম। এই একটা ক্রিকেট জগৎ। আবার অন্য খেলাগুলোর জন্য মাঠে থাকা হতো প্রায় দিনই। আমাদের ভিক্টোরিয়া ক্লাবটা সুন্দর ছিল। কাঠের তৈরি পুরোনো ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। একটা ভালো টেবিল টেনিস বোর্ড ছিল, টেবিল টেনিসও খেলতাম।
টিপু: আপনাদের বাড়ির পরিবেশ কেমন ছিল?
মতিউর: আমাদের বাড়ির পরিবেশটা ছিল ভিন্ন... আমরা ছিলাম নয় ভাইবোন। বাবা বেশ ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আইনজীবী ছিলেন। আম্মা ছিলেন উদার, মুক্ত মনের মানুষ। তিনি পড়াশোনা করতে পারেননি, এটা খুব কষ্ট ছিল তাঁর। আমাদের নয় ভাইবোনের সফলতার সবকিছু তাঁকে কেন্দ্র করেই। যদিও অর্থের জোগান দিতেন বাবাই। আবার, বাবার কয়েকজন আত্মীয়-ভাই, যাঁরা মূলত প্রথমে গ্রামে থাকতেন, পরে কেউ কেউ ঢাকায় থাকতেন। তাঁরা বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা আমাদের বাসায় থাকতেন কেউ কেউ। পড়াতেন আমাদের। তো সেই একটা প্রভাবে আমাদের বাড়িতে বামপন্থী পত্রপত্রিকা, বইপত্র—এসব আসত।
টিপু: এটা কত সালের দিকে?
মতিউর: ১৯৫৪ থেকে ৫৯ সাল পর্যন্ত এ রকম চলেছে। আমি বংশালে থাকতাম, ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৫৩-৫৪ সালের মিছিলগুলো হতো বংশাল, নবাবপুর, ইসলামপুর থেকে জেলখানা পর্যন্ত এলাকাজুড়ে। জেলখানা ছিল বংশাল দিয়ে পশ্চিমের শেষ মাথায়। যত মিছিল—সব পল্টন-বংশাল-নবাবপুর দিয়ে যেতো। মনে পড়ে, ’৫৬ কি ৫৭ সালে আরমানিটোলা মাঠে একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানে আমি কাকাদের সঙ্গে গেছি। তাদের সাথে আমার নানা রকম অনুষ্ঠানে যাওয়ার-আসার সুযোগ হতো।
টিপু: নাম কী আপনার কাকাদের?
মতিউর: একজন কাজী জহুরুল হক, পরে আইনজীবী হয়েছিলেন; আরেকজন কাজী আজিজুল হক, মত্স্য বিভাগে বড় কর্মকর্তা ছিলেন। আমার বড় ভাইয়ের নামে আমাদের বাসায় ইন্টারন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ-এর মাসিক ম্যাগাজিন আসত বুদাপেস্ট থেকে। আইইউএস ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন স্টুডেন্ট’স-এরও ম্যাগাজিন বাসায় আসত প্রাগ থেকে। এসব দেখতাম। আমার বড় ভাই কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এইভাবে আমাদের বাড়িতে পড়াশোনা, সাহিত্য ও বামপন্থী রাজনীতির একটা পরিবেশ ছিল। আমার কাকাদের একজন গান করতেন, তাঁর গলায় আমার গণসংগীত শোনার সুযোগ হয়েছে। তাঁর নাম আখতারুজ্জামান। স্কুলশিক্ষক ছিলেন। নরসিংদীর চালাকচরে থাকতেন। সরদার ফজলুল করিম ভাইয়ের বইয়ে ওনার কথা উল্লেখ আছে। সরদার ভাই ১৯৫০ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ওই গ্রামে আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন। স্কুল, খেলা, আবার বাড়িতে বামপন্থার প্রভাব—এ রকম একটা পরিবেশের মধ্যে ছিলাম আমরা।
আমার বাবার এক ফুফাতো ভাই কাজী জহীরুল হক, ষাটের দশকের শুরুতে তিনি থাকতেন মালিবাগের ভেতরে নিরিবিলি একটা বাসায়। আমি ওই বাসায় যাওয়া-আসা করতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় গেলাম। গিয়ে ওখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্ঞান চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হলো। পরে ওই কাকা তাঁর বাড়ি নিয়ে আসেন লালবাগে। লালবাগে বাড়ি করলেন, বিয়ে করলেন। আমি তাঁর বাসায় গিয়েছিলাম ’৬১ সালের ডিসেম্বরের এক দুপুরে। ওই বাড়িতে গিয়ে বুঝলাম যে ওটা কমিউনিস্ট পার্টির একটা ডেন [আশ্রয়স্থল]। আমি যেদিন গেলাম, সেদিন জ্ঞান চক্রবর্তী ওই বাসায় ছিলেন। আমি দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করবে না? আমি বললাম, হ্যাঁ, করব। তিনি একটা চিঠি লিখে দিলেন আবদুল হালিমকে, মালেকার বড় ভাই। চিঠি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি থাকতেন লারমিনি স্ট্রিট, ওয়ারীতে। এইভাবে আমার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। এইভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে পড়লাম।
তিনি তখনো ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন। তখন ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্রীয় সেলের সদস্য ছিলেন। ওনার মাধ্যমে ’৬২ ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলনের প্রস্তুতির খবর আমরা জানতাম। তিনি আমাকে নানা কাজে পাঠাতেন। এইভাবে ’৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের প্রথম দিন, ধর্মঘট হলো ১ ফেব্রুয়ারি। সোহরাওয়ার্দীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে। তার কয়েক দিন আগে থেকেই আমি মধুর ক্যানটিনে যাওয়া-আসা করি। তখন আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র। প্রথম বর্ষে পড়ি।
টিপু: এইভাবে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হলেন?
মতিউর: আসলে ছাত্র ইউনিয়নে যুক্ত হওয়ার আগে আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হয়ে গেলাম। সে সময় সেই অর্থে ঢাকা কলেজে ছাত্র ইউনিয়নের সংগঠন ছিল না। আমি ছাত্র আন্দোলনের নানা কর্মসূচিতে উপস্থিত হতে থাকলাম। কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হতে শুরু করল। এর চিঠি নেওয়া-দেওয়া, যোগাযোগ করা—এই সব। আন্দোলনের দিনগুলোতে আমি যুক্ত থাকতাম। প্রথমে যুক্ত থাকা, খোঁজখবর দেওয়া-নেওয়া। আন্দোলনের সকল কর্মসূচিতে অংশ নিতাম।
শুধু ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে না, শুরুতে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কর্মী হিসেবে ’৬২ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে ’৬৯ পর্যন্ত যত আন্দোলন হয়েছে, তাতে আমি যুক্ত ছিলাম। মনে পড়ে, বাষট্টির ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটা উত্তাল তরঙ্গমালা তৈরি হলো—অত্যন্ত সাহসী একটা আন্দোলন। তখন এত ছোটখাটো মিছিল হতো না। ফেব্রুয়ারির প্রথম দিনের মিছিল, দ্বিতীয় দিনের মিছিল, তৃতীয় দিনের মিছিল... ক্রমাগত এটা বড় হয়েছে। মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে, গুলিস্তান হয়ে পুরান ঢাকার নবাবপুর, ইসলামপুর হয়ে পুরোটা ঘুরে জেলখানায় দিয়ে শহীদ মিনারে এসে শেষ হতো। একটা মিছিল হলো—৫ বা ৬ তারিখে—বিশ্ববিদ্যালয় মাঠ হয়ে মেডিক্যাল কলেজের ভেতর দিয়ে বের হয়ে জেলখানার সামনে দিয়ে ইসলামপুর আর নবাবপুর হয়ে শহীদ মিনারে শেষ হলো।
সেই মিছিলগুলোতে বিপুল ছাত্র জমায়েত হতো, আর পথে পথে এটার শক্তি বৃদ্ধি হতো, সাধারণ মানুষ যোগ দিত। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করত, ছবি ভেঙে, ছবি মাড়িয়ে।
’৬২ সালের এই আন্দোলনটা পরবর্তী বাংলাদেশের বহু আন্দোলনের সূত্র ও শুরু এবং অত্যন্ত সফলভাবে হয়েছিল সেটা। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আইয়ুব খানের শক্তি, ক্ষমতা ও দম্ভ অনেকটাই চূর্ণ হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। ছাত্রদের আন্দোলন একটা নতুন ব্যাপ্তি ও ব্যাপকতা পায়। সারা দেশে এটার একটা প্রভাব তৈরি হয়। এর ফলে রাজনৈতিক দলগুলো নড়াচড়া শুরু করে, তারা উদ্যোগী হয়। তারপর ৯ নেতার বিবৃতিসহ অনেক ঘটনা ঘটতে থাকে। এটা বলা যায়, বায়ান্নর ছাত্র আন্দোলনের পর বাষট্টির আন্দোলন আরেকটি একটা নতুন ধাপ তৈরি করল, যেটা ঊনসত্তরের পরে ’৭০, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে অগ্রসর করে নিয়ে গেল।
টিপু: আচ্ছা, মধুর ক্যানটিনের ঘটনা বলছিলেন...
মতিউর: হ্যাঁ, মধুর ক্যানটিনে তো আমি যেতাম সেই শুরু থেকেই, তবে আমার পরিচিতি কম, তাই কম থাকতাম। সেই স্মৃতি তো মনে আছেই—পয়লা ফেব্রুয়ারির আগেই একটা উত্তেজনার পরিবেশ ছিল। প্রস্তুতির ব্যাপার ছিল। একটা ঘটনা মনে আছে, সেখানে গোয়েন্দা সংস্থার লোক ছিল, তাকে ধরে মারা হলো। ঠিক মধুর ক্যানটিনের উল্টো দিকে সিঁড়ি ছিল—সেখানে দাঁড়িয়ে বদরুল হক বক্তৃতা দিলেন। ভালো বক্তৃতা করতেন। তেষট্টি সালে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছিলেন, পরে বিচারপতিও হয়েছিলেন।
এ রকম সব ঘটনা—লিফলেট তৈরি, সেটা বিলি করা, পোস্টার তৈরি, আবার সেটা লাগানো—এই সমস্ত কাজে যুক্ত ছিলাম। সেই কারণে শুরু থেকে কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় নেতাদের আমি দেখি, চিনি। বিশেষ করে রাশেদ খান মেনন, রেজা আলী, হায়দার আকবর খান রনো, পংকজ ভট্টাচার্য, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকসহ নেতাদের দেখতাম। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হলো। তাঁদের কথা শুনতাম। বক্তৃতা শুনতাম। তখন আমি ঢাকা কলেজে পড়ি। এই ছাত্র আন্দোলনের কাজ করতে সুবিধা হবে বলে বাসা ছেড়ে আমি ঢাকা কলেজের হোস্টেলে উঠলাম। লেখাপড়া একদমই করতাম না। ক্লাস করতাম না। পুরো সময়ে একদিকে ছাত্র আন্দোলন, আরেক দিকে তখনো আমি খেলি। খেলাটা আমার চলেছে ’৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত।
’৬৩ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে ভর্তি হই। আমার সাবসিডিয়ারি বিষয় ছিল গণিত ও অর্থনীতি। আমি আসলে কোনোটার ক্লাস করতাম না। একপর্যায়ে গিয়ে দেখা গেল, রাজনীতিটাই আমার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল। খেলাটা আমার পক্ষে চালানো আর সম্ভব নয় এবং আমি খেলার মাঠ ছেড়ে দিলাম। তবে খেলার প্রতি আমার কখনো আগ্রহ কমেনি। সারা জীবন কিছুটা ক্রিকেট, কিছুটা ফুটবল, কিছুটা অ্যাথলেটিকস—সবকিছুর খোঁজখবর রেখেছি। আর সংবাদপত্রের একটা বড় উপাদান তো খেলা। সেটা জানতে হয়, বুঝতে হয়, সেদিক থেকে অভ্যাসটা এখনো রয়ে গেছে। মনের ভেতর খেলার প্রতি একটা আবেগ কাজ করে।
টিপু: তাহলে এভাবেই রাজনীতি প্রধান হয়ে উঠেছিল?
মতিউর: গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি আর প্রকাশ্যে ছাত্র ইউনিয়ন—এই হয়ে গেলো আমার জীবন। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন আর পার্টির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুটো সেল গঠন করা হলো। একটা সেল ছাত্র ইউনিয়নের প্রকাশ্যে রাজনীতির কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে—তার মধ্যে পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, সারওয়ার আলী প্রমুখ ছিলেন। আরেকটা সেল ছিল সাংগঠনিক যাঁরা পার্টির ভেতরের কাজটা গোছাবেন—সেখানে আমি ছিলাম, সঙ্গে ছিলেন সিলেটের ইকবাল হোসেন চৌধুরী [কিছুদিন আগে মারা গেলেন], রায়পুরার ফজলুল হক খন্দকার [পরে কৃষকনেতা], নোয়াখালীর আবদুল হাই [পরে আইনজীবী হয়েছেন], কিছু পরে ঢাকা হলের আবু তাহের—আরও দু-একজন থাকতে পারেন। তখন তো ছাত্ররাজনীতির বাইরে কমিউনিস্ট পার্টির পরামর্শে কোনো শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, সভা-সমিতি থাকলে সেখানে থাকতাম। আমার মনে আছে, ’৬৪ সালে ঢাকা জেলা কৃষক সম্মেলনের জন্য রায়পুরায় গেলাম তখনকার ছাত্রনেতা, পরে কৃষকনেতা ন–রুর রহমানের সঙ্গে [আমাদের বন্ধু ছিলেন, মারা গেছেন]।
টিপু: বাষট্টির কয়েক বছর পর ৬ দফা থেকে ১১ দফায় কীভাবে এলেন আপনারা?
মতিউর: বাংলাদেশে, তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তানে, পাকিস্তান হওয়ার পর—বিশেষ করে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকে কিন্তু ধীরে ধীরে তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তান কিংবা পূর্ব বাংলা, আমাদের এই দেশের মানুষ, প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, লেখক-শিল্পী এবং রাজনীতিবিদ, তাঁদের মধ্যে এই অঞ্চলের শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য নিয়ে কথা বলা বা আলোচনা বড় করে শুরু হয়ে যায়। আমরা যদি ১৯৫৪ সালের নির্বাচন দেখি, তাহলে ফলাফলে পরিষ্কার দেখব, এই অঞ্চলের মানুষ সরাসরি মুসলিম লীগকে প্রত্যাখ্যান করেছে। বিশেষ করে—যাঁরা এক পাকিস্তানের অখণ্ডতার চিন্তা করেছেন, তাঁদের সমূলে উত্পাটিত করেছে। তারপরও যদি আমরা পাকিস্তান সংসদের আলোচনা দেখি, তখনো আমাদের তত্কালীন জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদেরা, তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানও আছেন, বিশেষ করে ওই আলোচনাগুলোতে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার প্রতি শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্যের কথা বলতেন। স্বায়ত্তশাসন, সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গও তাঁরা তুলেছেন। এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই অঞ্চলের, আমাদের অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় নেবে না।
বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন শুরু হলো। তখনই কিন্তু আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে আলোচনা হয়, সে আলোচনায় শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। বলেছিলেন, স্বাধীনতা না হলে কিছু হবে না। সে বৈঠকে কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিং ও খোকা রায় ছিলেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও ইত্তেফাকের সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। সিপিবির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, আমরা এই চিন্তার যৌক্তিকতা মানি, বুঝি। তবে এখনই এই বিষয়, এই স্লোগান নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে না, সময় লাগবে। আমাদের সে জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান বিষয়টা মেনে নিলেন, তবে বলেছিলেন, আমার কথাটা থাকল। তারপরের কয়েক বছরে সামরিক শাসনের অত্যাচার, নির্যাতন, গ্রেপ্তারের ভেতর দিয়ে আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের দাবিদাওয়া উপেক্ষা করা হয়। বিশেষ করে—তখনকার শিক্ষানীতি বা অর্থনীতির নীতিমালার মধ্য দিয়ে এটা আরও পরিষ্কার হয়—যদি এই অঞ্চলের মানুষ নিজেদের অধিকার ফিরে না পায়, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ নেই। ৬ দফার দাবির ভিত্তিটা সেখান থেকে আসে। ৬ দফা নিয়ে কিন্তু তখন বামপন্থীদের মধ্যে, আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। তত দিনে কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে গেছে। সিপিবি আনুষ্ঠানিক বিভক্ত না হলেও কার্যত বিভক্ত হয়ে গেছে। সিপিবি বিভক্ত, অপরদিকে ন্যাপ বিভক্ত, ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত। এই হলো অবস্থা।
আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভেদের বিষয়গুলো বাদ দিলে আমরা যদি জাতীয় রাজনীতির বিষয়টা দেখি, দেখব, সে সময় আওয়ামী লীগের ৬ দফা, জাতীয়তাবাদ—এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের পার্টির সিপিবির অবস্থানটা ছিল, আমরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিরোধী নই এবং এটা অগ্রসর করার পক্ষে। তবে ৬ দফা নিয়েও আমাদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, তখনো কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়নি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, আমরা মস্কোপন্থীরা শেষ সময়ে এসে ৭ জুনের হরতালের আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, এই আন্দোলনে আমাদের থাকতে হবে। ৭ জুনের হরতালের পক্ষে অবস্থান নিয়ে আমরা অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের তরুণ ছাত্রনেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, আজকের সিপিবির নেতা, তিনি ৭ জুন হরতাল পালন করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরও কয়েকজন। তবে আমাদের বিষয়টা ছিল, আমরা ৬ দফা আন্দোলনের বিষয়টা বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করিনি। আমরা মনে করেছিলাম, এটার মধ্যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। এটাকে যদি সত্যিকার অর্থে মানুষের কল্যাণের-মুক্তির লড়্গ্যে নিতে হয়, আরও কিছু দফা বা দাবি যুক্ত করতে হবে। এটা আমাদের সিপিবির অবস্থান, এটা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির [মুজাফ্ফর] অবস্থান, এটা ছাত্র ইউনিয়নের অবস্থান। কিন্তু পিকিংপন্থী বন্ধুরা বা পিকিংপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি বা ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ, তাঁরা ৬ দফার সরাসরি বিরোধিতা করেছেন। এমনকি তাঁরা বলেছেন, এটা একটা সিআইএর চক্রান্ত। এটা ষড়যন্ত্র। আমাদের পক্ষে সিপিবি, ন্যাপ বা ছাত্র ইউনিয়নের চেষ্টাটা ছিল—৬ দফাটার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েও যেটা অসম্পূর্ণ সেখানে শ্রমিক-কৃষক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর দাবিদাওয়া, পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষানীতি এবং অন্য বিষয়গুলো যুক্ত না করলে পূর্ণাঙ্গ হয় না।
টিপু: তারপর কি সমাঝোতা হলো?
মতিউর: এসব নিয়ে আলোচনা আগে থেকে শুরু হলেও ৬৯-এ এসে চূড়ান্ত হয় জানুয়ারি মাসে। কারণ, তখন ওই অবস্থায় সত্যিকার অর্থে আইয়ুব খান বা ইয়াহিয়া খানের পতনের জন্য বা পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলনটাকে অগ্রসর করে নেওয়ার জন্য সর্বদলীয় ঐক্যের একটা প্রয়োজনীয়তা ছিল। সে সময় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগও এটা বুঝতে পেরেছিল শেষ পর্যন্ত। সে জন্য বলব—সিপিবি, অর্থাৎ গোপন কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বা ছাত্র ইউনিয়নের একটা চেষ্টা ছিল। এই চেষ্টাটা—এই যে নানা তর্ক-বিতর্ক-আলোচনা-চাপ, আবার ছাত্র ইউনিয়নকে বাদ দিয়ে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা সারা দেশে ছাত্রলীগের একক অবস্থানটা ছিল না। শেষ পর্যন্ত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে একমত হয়। চূড়ান্ত আলোচনার পেছনে ফরহাদ ভাইয়ের একটা বড় ভূমিকা ছিল। সে সময় ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গেও তিনি বৈঠক করেছেন। আমরা এ ধরনের নানা বৈঠকে থাকতাম। তবে ফরহাদ ভাইয়ের সঙ্গে মিলে একটা বৈঠক হয়েছিল বুয়েটের আহসানউল্লাহ হলের একটা রুমে। সেদিন বৈঠকে ঢাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ ছিলেন। সিরাজুল আলম খান ছিলেন—এ বিষয়গুলো আলোচনা করার জন্য। পরবর্তীকালে ইকবাল হলে এটা চূড়ান্ত হয়। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক আত্মগোপনে। আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ে, সে সভাগুলোতে আমার যোগদানের সুযোগ হয়েছিল। সামসুদ্দোহাসহ আমরা যাই। সেখানে ছাত্রলীগ নেতা আব্দুর রউফ, খালেদ মো. আলীরা থাকতেন। ওই যে কয়েকটা বিষয়ে আপত্তি ছিল, সেটার বিকল্প খুঁজে বের করা। মুদ্রা ব্যবস্থাটার একটা বিকল্প ছিল। অর্থাৎ এক মুদ্রা, দুই মুদ্রা—এই জায়গাতে দ্বিতীয় বিকল্পটাকে গ্রহণ করা হয়। আর ছাত্রলীগ-ছাত্র ইউনিয়ন একমত হয়, ৬ দফা থেকে ১১ দফাতে পূর্ণাঙ্গ করা হবে। সেখানে শ্রমিক-কৃষকের দাবি-দাওয়া, অর্থনীতি ও পররাষ্ট্র বিষয়গুলো যুক্ত করা হয়। পরে এটা ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপও মেনে নেয়। পরে মুসলিম লীগ সরকারের সমর্থক এনএসএফের একটি অংশ এই আন্দোলনের চাপে [মাহবুবুল হক দোলন ও নাজিম কামরান চৌধুরীরা] ১১ দফা মেনে নিল। সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ হলো, এই ১১ দফার প্রতি আওয়ামী লীগ সমর্থন জানাল। ন্যাপ [মোজাফ্ফর]সহ সব রাজনৈতিক দল, সংগঠনগুলো যুক্ত হয়ে ‘ডাক’ গঠন করলো। অর্থাৎ প্রশ্নটা ছিল, ৬ দফা মুক্তির সনদ নয়। এটা দিয়ে পূর্ব বাংলার মানুষের সব সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। এখানে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষ এবং অর্থনীতি, পররাষ্ট্রনীতিসহ অন্যান্য বিষয়কে যুক্ত করতে হবে। এ-ই ছিল প্রধান বিষয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও জেল থেকে বের হয়ে ৬ দফার সঙ্গে ১১ দফার প্রতি সমর্থন জানালেন।
টিপু: এটা তো বামপন্থীদের রাজনৈতিক বিজয় ছিল?
মতিউর: হ্যাঁ, এটা আমি বলব যে বামপন্থীদের একটা জয় ছিল। কর্মসূচিটাকে বৃহত্তর একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। আর একই সঙ্গে বলব, তখনকার ছাত্র আন্দোলন দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, নাট্য আন্দোলন, বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিকদের আন্দোলনগুলো ক্রমাগত বামপন্থীদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল। এটাও কিন্তু একটা বড় শক্তি হিসেবে ছিল। এই সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি, শিল্পীদের ভূমিকা কিন্তু ওই আন্দোলনটাকে বেগবান করেছে, প্রভাবিত করেছে। এটার মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি প্রভাব তৈরি করতে পেরেছে। ফলে ১১ দফা ওই সময়ের বিবেচনায় প্রগতিশীল অগ্রসরমাণ একটা ভবিষ্যত্মুখী কর্মসূচি ছিল। ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সফলতা, আইযুব খানের পতন, বঙ্গবন্ধু ও অন্যান্য নেতাদের মুক্তির নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। যদিও এটা খুব দুঃখজনক, পরে এই ঐক্যটা আর থাকেনি।
টিপু: তখন তো আন্দোলনের একটা সময় ছিল...
মতিউর: হ্যাঁ, একদিকে ছাত্র আন্দোলন, সামরিক শাসনবিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন, প্রকাশ্য আন্দোলন-অপ্রকাশ্য আন্দোলন, আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির কাজ—সব মিলিয়েই আমাদের জন্য একটা আন্দোলনের সময়। আবার খুব বেশি ভুল না হলে—’৬৫ সালে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক হই। সংস্কৃতি সংসদের কাজ করতে গিয়ে কবি, লেখক, শিল্পীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ি। কারণ, অনুষ্ঠান করতে গেলে তাঁদের ছাড়া সম্ভব নয়। সেটা করতে গিয়ে ছায়ানটের সঙ্গে যোগাযোগ হয়—সেখানে ওয়াহিদুল হক, সন্জীদা খাতুন, জাহিদুর রহিমসহ অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক হয়। আমরা যে ছাত্র ইউনিয়ন করতাম, সেখানে সংস্কৃতির জায়গাটার একটা বড় ভূমিকা ছিল—এই যে একুশের সংকলন, বিভিন্ন দিবসের সংকলন, নানা প্রকাশনা, অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশেষ করে একুশের সংকলন প্রকাশনার ১৯৬৪ থেকে ৭০ সাল পর্যন্ত আমি যুক্ত ছিলাম। সমপ্রতি আমি সব সংকলন মিলিয়ে বিদ্রোহী বর্ণমালা নামের একটা বই প্রকাশ করেছি—শুধু একটা ছাড়া—১৯৬৫ সালের একুশের সংকলন বিক্ষোভ খুঁজে পাইনি। তো সংকলন করতে গিয়ে লেখকদের কাছে যাওয়া, লেখা সংগ্রহ করা, প্রেসে যাওয়া, প্রেসের কাজ জানা—নানা কিছু করতে হয়েছে। সে সময় একদিকে ছাত্র আন্দোলন, অন্যদিকে গোপনে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ, মিছিল-মিটিং, ছাত্রসংগঠনের সম্মেলন ও পার্টির নানা অনুষ্ঠান মিলিয়ে সে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ ছিল আমাদের।
একটা বড় সময়ে ইকবাল হল, না হয় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আহসানউল্লাহ হল কিংবা কখনো কখনো মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে আমরা থাকতাম। তো সে সময় আমার চেয়ে যাঁরা বয়সে, লেখাপড়ায়, নেতৃত্বে সিনিয়র ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে একটা বন্ধুত্ব হয়। সেই যে ’৬২ বা ’৬৩ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময় থেকে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয়, সেটা এখনো অটুট আছে—পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সারওয়ার আলী বা রেজা আলীসহ অনেকের সঙ্গে। তখনকার ছাত্র আন্দোলনে তাঁরা অনেক বড় নেতা। রেজা ভাই দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। পঙ্কজদা বারবার জেলে গেছেন। আর সারওয়ার ভাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংসদের সাধারণ সম্পাদক, পরে বিএমএরও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ও অন্যান্য সংগঠনেও নেতৃস্থানীয় পদে আছের এখনো।
ছাত্র আন্দোলনের যা কিছু প্রাপ্তি, যা কিছু শেখা, যা কিছু জানাশোনা, যা কিছু অর্জন, সেটা ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরেই। ছাত্র রাজনীতি করতে গিয়ে নানা ধরনের বইপত্র পড়া, ম্যাগাজিন সাময়িকপত্র পড়া, সাহিত্য পত্রিকা ও বই পড়া, সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাবোঝা—এগুলো একসময় অভ্যাসে পরিণত হয়। পরবর্তী জীবনেও অব্যাহত থাকল! আমি বলব যে, ’৬২ থেকে ’৭০ সাল মানে প্রায় পুরো এক দশক বাংলাদেশের জন্য শ্রেষ্ঠ দশক। এই সময়েই কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের ভিত্তিভূমি তৈরি হয়ে যায়। আবার এই দশকের পেছনেও পঞ্চাশ দশকের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। কারণ, পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে—বিশেষ করে কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান, শিল্পকলা ও সংবাদপত্র জগতে নতুন উত্থান সূচিত হয়। যাঁরা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষা আন্দোলন শুরু করলেন, তাঁরাই কিন্তু বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিবর্তনের একটা ভিত্তি তৈরি করলেন পঞ্চাশ দশক জুড়ে।
টিপু: কী ধরনের ভিত্তি এটা?
মতিউর: এই যে, তাঁদের লেখার ভেতর, গানের ভেতর, চিত্রকলার ভেতর দিয়ে একটা প্রগতির চিন্তা-চেতনা, একটা সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা-চেতনা, একটা নতুন সমাজের চিন্তা-চেতনা, একটা নতুন রাষ্ট্রের চিন্তা-চেতনা—এঁরাই তো নিয়ে এসেছেন। আপনি যাঁর নামই বলেন না কেন, সেই ’৪৮ বা ’৫২ থেকে ৬২-তে তাঁদের কারও না কারও, প্রায় সবার উপস্থিতি আপনি দেখতে পাবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সবারই কিছু না কিছু অবদান দেখতে পাবেন। সেটা শিল্পকলায় কামরুল হাসান বা রশীদ চৌধুরী হোক, কবিতায় শামসুর রাহমান বা সৈয়দ শামসুল হক হোক, গানে আবদুল লতিফ বা আলতাফ মাহমুদ হোক, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান কিংবা আনিসুজ্জামানসহ আরও অনেক নাম বলা যাবে—প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রেখেছেন। আবদুল আহাদ বা খান আতাইর রহমানের নামও চলে আসে। এঁরা হয়তো শুধু রাজনীতিতে থাকেননি, সবাই শুধু অধ্যাপনায় থাকেননি, সবাই শুধু শিল্পকলায় থাকেননি, সবাই শুধু সাহিত্যে থাকেননি, কিন্তু প্রত্যেকেই নানা পেশায় যুক্ত হয়ে গেছেন। এটাই নতুন দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের যাত্রাপথের শুরু।
আমরা দেখি, দেশভাগের শুরু থেকেই নানা ক্ষেত্রে তাঁদের অনেকের কর্মকা– ও ভূমিকা অনেক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরের বিস্তৃতি ঘটান। এঁরাই ’৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের আগে ও পরে ছাত্র ইউনিয়নের গঠন, সংস্কৃতি সংসদের গঠন, এঁরাই পরে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠন করেন। সেই মোহাম্মদ সুলতান, সেই মোহাম্মদ তোয়াহা, সেই অলি আহাদ, সেই ইমাদউল্লাহ, সেই গাজীউল হক—এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু বামপন্থী। আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গাজীউল হক ও তাঁর ছোট ভাই নিজামুল হক, আলতাফ মাহমুদ—তাঁরা আরেকটা সংস্কৃতির জগৎ তৈরি করেছেন। শহীদুল্লা কায়সারের একটা বড় ভূমিকা, জহির রায়হানের সরব উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই। মুনীর চৌধুরী বা রণেশ দাশগুপ্তের বিশেষ উপস্থিতি দেখতে পাই। এই সময়ে চট্টগ্রামে কলিম শরাফী ও মাহবুবুল হক চৌধুরীরা অনেক কাজ করেছেন। সারা দেশ জুড়ে এমন অনেকেই ছিলেন আরও। তাঁরা প্রত্যেকেই সারা জীবন এই গণতন্ত্র, এই ভাষা আন্দোলন, এই প্রগতিমুখিনতা, এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত সৃষ্টি করেন। আর এই ভিত্তিটা ষাটের দশকে এসে একটা বড় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পরিণতির দিকে নিয়ে যায়—আমরা বলব, বাংলাদেশের সত্যিকারের রেনেসাঁর সময় হলো ষাটের দশক। সেখানে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতিতে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তা-ই সৃষ্টি হয়েছে এই সময়ে। সে সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে এভাবে নানা শক্তি কাজ করেছে। এভাবেই দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা গড়ে ওঠে। বহু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যার সামনে চলে আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ।
টিপু: আরেকটি সাংস্কৃতিক ধারা তো ছিল?
মতিউর: প্রগতিশীল রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শের ধারা। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে বামপন্থীদের প্রাধান্য ছিল, পঞ্চাশের দশক থেকে এর শুরু। ছাত্র আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলন আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর দিয়ে তারা আবার মূল আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করেছিল, শক্তি-সাহস জুগিয়েছিল। তারা একটা বড় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছিল। হ্যাঁ, আরেক দিকে অর্থনীতিবিদসহ অন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আমরা যাঁদের জানি—ন–রুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান, খান সারওয়ার মুরশিদ, মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, আনিসুজ্জামানসহ অনেকের নাম বলা যায়, যাঁরা লেখা দিয়ে, চিন্তা দিয়ে প্রগতিশীল ভাবনা-চিন্তাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের বিরাট অংশই দেশের পরিবর্তন চেয়েছেন। এটা কোনো একক রাজনৈতিক দলের ছিল না। এমন নয় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা আওয়ামী লীগই সবকিছু ভেবেছে, এক রাজনৈতিক দলের তাঁরাই সবকিছু এককভাবে করেছেন, বিষয়টা এমন নয়। সমাজে বহুমুখী চিন্তাশীল মানুষগুলোর উত্থান ঘটেছিল।
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান মানুষগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে যুক্ত হয়ে—জাতীয়তাবাদী বলি, গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলি, প্রগতিশীলতা বলি, যা-ই বলা হোক না কেন—সমাজে এই চিন্তাগুলো নিয়ে এসেছেন। যার মধ্য দিয়েই কিন্তু ষাটের দশকের রেনেসাঁ যুগের সৃষ্টি হয়েছে। আন্দোলন বেগবান হয়েছে যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে, উনসত্তরের আন্দোলনের ভেতর দিয়ে একটা গণবিপ্লব কিংবা একটা গণ-অভ্যুত্থান তৈরি করে। একটা পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার পরাস্ত হয়। ওরা আমাদের দাবি মানতে বাধ্য হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। সেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। এবং স্বাধিকার ও স্বাধীনতার প্রশ্নটা সামনে চলে আসে।
টিপু: আপনি কি সত্তরের নির্বাচনের কথা বলছেন?
মতিউর: হ্যাঁ, সত্তরের নির্বাচন... পরে স্বাধীনতার আন্দোলন সংগঠিত হয়। বলতে চাই, এখনো স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বাংলাদেশের ইতিহাস রচিত হয়নি। অনেক সময়েই ব্যক্তিচিন্তা, দলীয় চিন্তার প্রকাশ থাকে বেশি। তবে ইতিহাস নিয়ে এখনো অনেক কাজ হচ্ছে। আমি মনে করি, আমাদের গবেষকদের ইতিহাসের এই দিকগুলো নজর দেওয়া দরকার, সেই দিকগুলো তুলে আনা দরকার।
টিপু: ছাত্র রাজনীতি কখন শেষ করলেন? তখন কি সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছিলেন?
মতিউর: ১৯৬৯ সালে আমি ছাত্র ইউনিয়নের কার্যক্রম শেষ করি। যদিও আমার মাস্টার ডিগ্রির ফলাফল ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই আইন বিষয়ে, আরও দু-এক বছর ছাত্র হিসেবে থাকার জন্য।
’৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর ছাত্র ইউনিয়নের সম্মেলন শেষে আমরা অনেকেই ছাত্র সংগঠন থেকে সরে আসি। তারপরও ছাত্র ইউনিয়নের কিছু কাজ, গোপন কমিউনিস্ট পার্টির ‘শিখা’ পত্রিকা প্রকাশ করা—এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। পার্টির সাংগঠনিক কাজে নানা সহায়তা করা—এমন একটা সময় যাচ্ছিল আমার। কোনো সিদ্ধান্ত পাইনি কিংবা হয়নি, আমি আসলে কী কাজ করব! কোথায় যাব!
আমি পার্টির হোল টাইমার মানে সার্বক্ষণিক কর্মী হবো ঠিক হয়ে গেছে আগেই, পার্টির রাজনীতি করব ঠিক হয়ে গেল। আমি কিন্তু প্রকাশ্যে রাজনীতিতে বক্তৃতা বা মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া কর্মী বা নেতা ছিলাম না। তাহলে আমি কী করব, আমার কাজটা কী হবে? এর মধ্যে জানা গেল, কমিউনিস্ট পার্টি গোপনে একটা পত্রিকার ডিক্লারেশন পেয়ে গেল। আমাদের একজন বন্ধু ছিলেন পার্টির মেম্বার, নাম ওয়াহিদুল হায়দার চৌধুরী। খুব ভালো হাসিখুশির মানুষ। তিনি চামড়া ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর নামেই পত্রিকার ডিক্লারেশন হয়। কমিউনিস্ট পার্টি ওনাকে দিয়ে আবেদন করিয়ে সাপ্তাহিক একতার ডিক্লারেশন পায়। তো পার্টি থেকে এটা ঠিক হয়ে গেল, বজলুর রহমান সম্পাদক আর ওয়াহিদুল হায়দার চৌধুরী প্রকাশক হবেন। তখন আমার তো সরাসরি কোনো কাজ নেই। কিন্তু আমার প্রেসে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, লেখালেখির সঙ্গে যুক্ততা আছে, প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ততা আছে, সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে—সবকিছু মিলিয়েই আমাকে সাপ্তাহিক একতার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক করা হলো। এভাবেই সে সময়ে গোপন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র হলো সাপ্তাহিক একতা।
টিপু: এটা কি সত্তর সালের ঘটনা?
মতিউর: হ্যাঁ, সত্তর সালের ঘটনা। সত্তর সালের জুলাই মাসে সাপ্তাহিক একতা প্রকাশিত হলো। এই হলো আমার সাংবাদিকতার শুরু। আমি যে সাংবাদিকতা করব, সে জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি, তা নয়। তবে সে সময়ে বামপন্থী তরুণদের মধ্যে কবিতা-গল্প লেখা বা সাংবাদিকতার জগতে যাওয়ার কিছু আগ্রহ, ওই যে বলে না—কিছুটা পরিবেশ হয়তো তৈরি হয়েছিল। তবে সে সময় আমি কবিতা লিখতাম। বেশ কয়েক বছর কবিতা লেখালেখির পর বুঝলাম এটা আমাকে দিয়ে হবে না। কবিতা বিদায় হলো।
টিপু: কবিতা, কোন সালের কথা?
মতিউর: ষাটের দশকের শুরু থেকে বেশ কয়েক বছর আমি কবিতা লিখেছি। পরে দেখলাম যে এটা আমার একটা ব্যর্থ চেষ্টা ছিল। ক্রিকেট বাদ, কবিতা বিদায়! কিন্তু সাহিত্য পড়াশোনা অব্যাহত ছিল। সংবাদে যাওয়া-আসা করতে গিয়ে রণেশ দাশগুপ্ত, সন্তোষ গুপ্তের সঙ্গে সম্পর্ক, শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে পরিচয়—এসবই আমার জন্য অমূল্য ব্যাপার ছিল। রণেশদা, সন্তোষদা, শহীদুল্লা ভাইয়ের সঙ্গে সারা জীবনই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। এটা হয়তো কারণ, আমার ওই দিকে যাওয়া-আসা আছে, তো সাপ্তাহিক একতার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হয়ে গেলাম। ভুল না হলে ২৩ নম্বর শ্রীশ দাশ লেনে একতার অফিস ছিল। অনেকটা না জেনে, না বুঝে সাপ্তাহিক একতার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হলাম। তখন বজলু ভাই সংবাদের সহকারী সম্পাদক। তিনি একতার অফিসে আসেন। নানা কাজে সহযোগিতা করেন। আর আমরা অন্যান্য কাজ সম্পাদন করি। সংবাদ লিখি। প্রুফ দেখি। এবং সকালে যাই রাত পর্যন্ত থাকি। বৃহস্পতিবার সারা রাত থাকি। পত্রিকা ছাপা হতো বৃহস্পতিবার রাতে, শুক্রবার কাগজ বেরোয়। সারা রাত প্রেসে থাকতাম। মূলত ছিল কাজগুলো দেখা, শেখা, জানা, নানা প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকা। এইভাবে পত্রিকা জুলাই মাসে বের হলো, ’৭০ সাল গেল। একাত্তরের মার্চে তো মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো।
টিপু: মার্চেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল?
মতিউর: মার্চেও বের হয়েছিল। ২৫ মার্চের রাতেও পত্রিকা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু পত্রিকা আর বিলি হতে পারেনি। ২৫ মার্চের সকাল থেকে আমার শরীর খুব খারাপ ছিল। আমার মাইগ্রেনের সমস্যা ছিল। সারা দিন কাজের পর সেদিন রাতে হাঁটতে হাঁটতে বংশালের বাসায় ফিরলাম। সব রাস্তা কার্যত বন্ধ। পথে পথে মিছিল আর ব্যারিকেড। সারা দিন নানা রাজনৈতিক উত্তেজনা ছিল। আমরা কী হেডলাইন করেছিলাম মনে নেই এখন। সেদিন বজলু ভাই রাত ৮টার দিকে ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে ঘুরে এসে হেডিং বদলে দিলেন। সেদিনের হেডলাইন ছিল, ‘সর্বাত্মক লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হউন’।
টিপু: হেডলাইন কি ৮ কলাম ছিল?
মতিউর: হ্যাঁ, ট্যাবলয়েট সাইজের পত্রিকার পুরোটা জুড়ে হেডলাইন ছিল। সেদিন গভীর রাতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ করে বসল আমাদের বাড়ির পাশে বংশাল রোডের ফাঁড়িতে।
টিপু: ২৫ মার্চের দিনের পরিবেশের কথা মনে আছে?
মতিউর: আসলে দেখেন, অনেক বছর তো হয়ে গেছে। সত্যি বলতে, আসলে ২৫ মার্চের রাতের আক্রমণটা সকলের জন্যই আকস্মিক ছিল। আমরা তো জানতাম আলোচনা চলছে। সমঝোতা হতে যাচ্ছে; আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা দেশের নেতৃবৃন্দের কথায়, আচরণে বা প্রকাশ্য বক্তব্য প্রদানের মধ্যে দিয়ে একটা আশাবাদের জায়গা তৈরি হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে সবাই তো একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানই আশা করেছিল। শেষ আলোচনার পরেও, আমরা তো জানি, আমাদের নেতৃবৃন্দ ২৫ মার্চ সারা দিন, পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে তাঁরা উত্তরের অপেক্ষায় ছিলেন। ২৫ মার্চের দিন যত গড়াতে থাকে, আগের যত সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভয়ের যে ভাবনাগুলো ছিল, ২৫ মার্চ সারা দিন সেগুলোই ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে থাকে। যখন জানা গেল, সেদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান চলে গেছেন আকস্মিকভাবে—তার আগেই আরও অনেকেই চলে গেছেন। তখন কিন্তু কোনো কিছু বুঝতে বাকি থাকে না আর। সন্ধ্যার পর থেকে পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে গেল। সারা শহর জুড়ে থমথমে পরিবেশ।
২৫ মার্চের সন্ধ্যার পরেই এটা বোঝা গিয়েছিল যে, আলোচনা ব্যর্থ, পাকিস্তানিদের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অন্যভাবে ভাবতে হবে। প্রচ– অবিশ্বাস্য ঘটনা। পরে, ২৫ ও ২৬ মার্চ ২৭ মার্চের সারা শহর জুড়ে ভয়ঙ্কর সব ঘটনা, সর্বত্রই ধ্বংস, আগুনের শিখা, মানুষের চিত্কার আর মৃত্যু। সেদিন রাতে অফিস থেকে বাসায় ফেরার জন্য যখন আমরা বের হলাম, তখন দেখলাম, সারা ঢাকা শহর, সারা বাংলাদেশ জুড়ে—অবিশ্বাস্য সব ঘটনা, ভয়াবহ... শহরে সব ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অবিশ্বাস্য! এ সবের অনেক কিছু সেদিন রাতে আমাদের বাসা থেকে দেখতে পেয়েছিলাম সারা রাত, সারা দিন।
২৫ মার্চ তো সারা রাত ওই অবস্থা। ২৬ মার্চ সারা দিন গৃহবন্দী। চারদিকে মৃত্যু আর ধ্বংসের আওয়াজ। ২৭ মার্চ কারফিউ প্রত্যাহার করা হয়েছিল কয়েক ঘণ্টার জন্য। সকালবেলায় বের হই। আমাদের বাড়ির কাছে একটা পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। সামনের ঘরে দেখি, দুজন পুলিশ উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। ভেতরে একটা ঘরে চার-পাঁচজন পুলিশ মেঝেতে পড়ে ছিলেন। সকলের গায়েই পুলিশের পোশাক ছিল। সবকিছু তছনছ। এই প্রথম মৃত্যুর একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলাম।
আবার বাসায় আসি। সাড়ে দশটার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে বংশাল নাজিরাবাজার হয়ে পশু হাসপাতালের বাঁ দিকে জাদুঘরের রাস্তা পেরিয়ে মেডিকেল কলেজের সামনে দিয়ে শহীদ মিনারে গেলাম। কামান-ট্যাঙ্কের আক্রমণে ধ্বংস করা হয়েছে শহীদ মিনার। ওখানে আমাদের কয়েকজন বন্ধুর দেখা পেলাম। তাদের মধ্যে সেলিমও ছিলেন। ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে ইকবাল হলে গেলাম। ক্যানটিনের সামনে, ভুল না হলে ১০ বা ১২টা লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। তাঁদের মধ্যে একজন শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের লাশ। মৃত্তিকাবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন তিনি। আর কয়েকজনের লাশ... আর হলের ভেতরে ঢুকিনি। আমরা সবাই ভয়ার্ত। গভীর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। ওখান থেকে হেঁটে হেঁটে এস এম হলে গেলাম। এস এম হলের বারান্দায় হাঁটলাম। সেখানেও দেখলাম, একটা রুমে আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের এক ছেলের চশমা মেঝেতে পড়ে আছে। কিন্তু তার মৃতদেহ দেখিনি। এস এম হল থেকে বের হয়ে জগন্নাথ হলে গেলাম। তখন তো মৃতদেহ দেখিনি বা হলের ভেতরে ঢুকিনি। শুনলাম যে গোবিন্দ চন্দ্র দেবের কথা, তাঁর বাড়িতে গেলাম। ওখান থেকে মধুদার বাড়িতে গেলাম। শুনলাম, মধুদাকে হত্য করা হয়েছে। সর্বত্রই একটা ভয়ঙ্কর-ভীতির পরিবেশ। রাস্তায় রাস্তায় উদভ্রান্ত মানুষ চলছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এসব দেখে একটা ভয়ের পরিবেশের মধ্যে বাসায় ফিরলাম।
পরের দিন আবার বের হলাম। সেদিন আমাদের কিছু বন্ধুবান্ধবের খোঁজ করলাম। সেদিনই আবার আমি শিল্পী-শিক্ষক মোহাম্মদ কিবরিয়াকে খুঁজতে গেলাম। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীকে খুঁজতে গেলাম। তাঁকে পেলাম বাসায়। ভীত-সন্ত্রস্ত। নিতুনদাকে খুঁজলাম। তখন তিনি আজিমপুরে থাকতেন। বাসায় নেই। আবার ফিরে এলাম। এই কয়েক দিন—গোলাগুলি, অগ্নিসংযোগ—এগুলোর মধ্যে আছি। আমরা বাঁচব কি বাঁচব না—এ রকম ভয়ের মধ্যে থেকে তিন দিন পরে আমাদের বোনদের কেন যেন মনে হলো, বংশাল থেকে ওয়ারীর ওখানটা একটু নিরাপদ। ওয়ারীতে মালেকাদের বাড়িতে আমার বোনেরা গেল। পরে মালেকার সঙ্গে আম্মাও গেলেন। এপ্রিলের শুরুর দিকে ভাইবোনদের নিয়ে বাবা-মা, মালেকা, ভাইবোনেরা গাড়ি করে গিয়ে... নৌকায় নদী পার হয়ে বেরাইদ গেলাম। বেরাইদে মালেকার বড় ভাই রহিম ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি ছিল। ওখানে এক রাত থাকলাম। রাতে থেকে সকালবেলা নৌকা নিয়ে কাপাসিয়ার দিকে চললাম নদীপথে নানার বাড়ি। আমাদের সঙ্গে একটি ট্রানজিস্টার ছিল। নদীপথে যেতে যেতে হঠাৎ কলকাতা বেতারে শুনতে পেলাম দেবব্রত বিশ্বাসের সেই গান, ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা, আমার প্রতিরোধের...’। নানার বাড়ি একটা সুন্দর বাড়ি, স্বপ্নের গ্রাম, আমরা ছোটবেলা থেকে যাওয়া-আসা করতাম। ওখানে আমার মা-বাবা, ভাইবোন থাকল।
আমি আবার ফিরে এলাম। ফিরে এসে আমার দায়িত্ব পড়ল—ঢাকা থেকে বজলু ভাই, মতিয়া আপা এবং আমাদের ছাত্র নেত্রী আয়শা খানম, মনিরা খান ও তার বোন রোকেয়া খান [কবির]—তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। নানার বাড়িতে। নানার দুইটা বাড়ির ব্যবস্থা হলো—একটা পিরোজপুর, আরেকটা কাপাসিয়া। আমরা ঠিক করলাম, দুই গ্রুপ দুই বাড়িতে রাখব। নৌকাপথে আমার ছোট মামা মতিয়া আপা, বজলু ভাই, মনিরা আর রোকেয়াকে পিরোজপুরে নিয়ে গেলেন। আর আয়শা আমাদের সঙ্গে কাপাসিয়া গেলেন। দু-তিন দিনের মধ্যে শোনা গেল, মতিয়া আপাকে আশেপাশের মানুষ চিনে ফেলছে, কথাবার্তা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে মতিয়া আপাকে চিনবে না তখন! তো মতিয়া আপা আর বজলু ভাইকে কাপাসিয়ায় নানাবাড়িতে নিয়ে এলাম। ওখানে থাকলেন আমার ভাইবোন ও আম্মার সঙ্গে। আমি আবার ঢাকা এলাম। আমার ছাত্রবন্ধু, কর্মীবন্ধু—তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। তখন দায়িত্ব পড়ল রণেশ দাশগুপ্তকে [আমাদের রণেশদা] ঢাকা শহর থেকে রায়পুরা নিয়ে যাওয়ার।
টিপু: ওই সময়টায় কি নিজেদের স্বপ্নের দিকে...
মতিউর: ওই সময়টা ছিল একদম অন্য রকম। ষাটের দশকটা—সবকিছুর মধ্যে একটা স্বপ্ন ছিল আমাদের। স্বপ্নটা ছিল নিজেদের মধ্যে, দেশের মানুষের মধ্যে—বাংলাদেশের মানুষ জেগে উঠছে। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়তে চায়, তারা একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র চায়, তারা একটা প্রগতিশীল সমাজ চায়, তারা মানুষের জীবনের দুঃখ-কষ্টের অবসান চায়, তারা সমাজের সার্বিক পরিবর্তন চায়। তখন এই ধারণাগুলোর একটা ভিত্তি পায়।
আমরাও পাশাপাশি স্বপ্ন দেখি—এই সবকিছুর মধ্য দিয়ে একটা পরিবর্তন আসবে। সে সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে জমায়েত, ছাত্র আন্দোলনে জমায়েত, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে জমায়েত, যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে জমায়েত, যেকোনো অনুষ্ঠানে বিপুল-বিশাল জমায়েত এবং সর্বশ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল। তখন সত্যিকারার্থে—জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়েছিল। এটা কোনো রাজনৈতিক দলের ঐক্য নয়, এই ঐক্য ছিল আপামর মানুষের মধ্যে ঐক্য। সব শ্রেণির মানুষের মধ্যে সমঝোতা, একাত্মবোধ।
যদি এইভাবে মূল্যায়ন করি—এটা ঠিক যে এই আন্দোলনের গোড়াতে আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি একমত হয়েছিল, পাকিস্তানি সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করতে হবে। এবং ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এটা শুরু হবে। লক্ষ্য ছিল, ’৬২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে এটার সূত্রপাত হবে। কিন্তু করাচিতে সোহরাওয়ার্দী গ্রেপ্তারের ফলে আন্দোলন আগে শুরু হয়ে যায়। ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ যৌথভাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত করে। আন্দোলনের এটা একধরনের শুরু বটে। এই আন্দোলনে আমাদের জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির সাহসী ভূমিকা ছিল, সংগঠকের একটা ভূমিকা ছিল, নেতৃত্বের একটা ভূমিকা ছিল। পাশাপাশি বামধারার সংগঠনগুলো—কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, ছাত্র ইউনিয়ন ও সংস্কৃতি সংসদ, কৃষক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন—সবকিছু মিলিয়ে এই বৃহত্তর সমাবেশ তৈরির কাজটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একাত্তরে দেশের মুক্তিযুদ্ধ, সশস্ত্র সংগ্রামে সবারই এ ক্ষেত্রে ভূমিকা ছিল। একক ব্যক্তি বা দলের ভূমিকা যেমন ছিল, অন্য শক্তি বা দলের ভূমিকা খাটো করা সম্ভব নয়।
টিপু: ষাটের মাঝামাঝিতেই তো ছাত্র ইউনিয়ন তো দুভাগ হয়ে যায়...
মতিউর: প্রথমে তো তর্ক-বিতর্কটা পার্টির ভেতর শুরু হয়। পরে বিভেদটা ছাত্র ইউনিয়নের মধ্যে চলে আসে। অন্যান্য গণসংগঠনের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালে ছাত্র ইউনিয়ন বিভক্ত হয়ে যায়। কৃষক-শ্রমিক সংগঠন বিভক্ত হয়ে যায়। ন্যাপ বিভক্ত হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয়ে যায়।
ষাটের দশকে অনেক সফলতার পরও এই বিভক্তিটা খুবই ক্ষতি করে। কারণ, কমিউনিস্ট পার্টি ছোট হলেও সব সময়ে চিন্তাভাবনা ও কৌশল নির্ধারণে তাদের একটা উদ্যোগী ভূমিকা ছিল। রুশ-চীন দ্বন্দ্ব-বিভক্তিতে বাংলাদেশের বামপন্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো। না হলে আমরা বামপন্থীরা আরেকটু ভালো কিংবা আরও বড় ভূমিকা নিতে পারতাম। আমরা বলি না যে, আমরা নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে পারতাম, এটা সঠিক বলে মনে করি না। তবে এটা ঠিক, এই বিভেদ না হলে আমরা বামপন্থীরা আরেকটু শক্তিশালী অবস্থান নেওয়া, আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ ছিল। এটার একটা খুব দুঃখজনক পরিণতি হয়! আমরা জানি যে, রুশ-চীন দ্বন্দ্ব একই সময় সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিভেদ আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, সাম্যবাদী আন্দোলনে বিশ্বব্যাপী বড় ক্ষতি সাধন করেছে।
টিপু: ইউরোপ-লাতিন দেশগুলোতে তখন আন্দোলন হয়েছে...
মতিউর: আন্দোলন তো হয়েছেই। আমরা এটাও দেখেছি, ষাটের দশকে প্যারিস যুব বিদ্রোহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুবশক্তির যুদ্ধবিরোধী অবস্থান, লাতিন আমেরিকার সেই চে গেভারা ও অন্যদের সশস্ত্র অভিযান। যদিও বলিভিয়ায় চে গেভারার সেই সশস্ত্র অভিযান ব্যর্থ হয়। তাঁর সেই সশস্ত্র অভিযান ব্যর্থ হওয়ার কারণ ছিল। ফিদেল কাস্ত্রো সেই বলিভিয়া অভিযানের বিরোধী ছিলেন। অবশ্য সে সময়ে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশে আমরা এই ধরনের কিছু উত্থান দেখতে পাই। এসবের বড় প্রভাব ছিল। পাশাপাশি আফ্রিকার অনেক দেশে—এঙ্গোলা, মোজাম্বিক, গিনি বিসাউয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হয়েছে। এমপিএলএ এঙ্গোলায়, ফ্রেলিমো মোজাম্বিকে—এরা ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক শক্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এনসির নেতৃত্বেও মুক্তির সংগ্রাম চলছিল। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস [এএনসি] সম্পর্কে আমরা জানতাম। কমিউনিস্টদের একটা শক্তিশালী অবস্থান ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় তো এনসি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন [কোসাটো] ঐক্যবদ্ধভাবে ছিল। এখনো তাদের মধ্যে সেই ঐক্যটা আছে। যদিও এটা অনেক দুর্বল হয়ে গেছে।
টিপু: এশিয়ার নানা দেশেও তো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই হয়েছে?
মতিউর: সে সময় ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তির সংগ্রাম, লাওস, কম্পুচিয়া ও প্যালেস্টাইনে মুক্তির সংগ্রাম—তার সঙ্গে কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তির সংগ্রাম মিলেমিশে একটা আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও প্রগতিবাদী আন্দোলনের ধারাবাহিক পটভূমিতে বাংলাদেশের ষাটের দশকের আন্দোলনকে দেখতে পারি আমরা। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তির সংগ্রামেও আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির একটা প্রভাব সরাসরি ছিল।
টিপু: চে গেভারাকে নিয়ে লেখা আপনার বইয়ে লিখেছেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় চে’র সবুজ নোটবুক’ প্রেরণা জুগিয়েছিল, সেই প্রেরণাটা কী?
মতিউর: সবকিছুর পরও চে গেভারার আত্মাহুতি একটা বিরাট ঘটনা। চে তো বিশ্বের তরুণদের কাছে, মুক্তি-সংগ্রামীদের কাছে একটা সংগ্রামের প্রতীক হয়ে গেলেন। এখনো সেটা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একাত্তর সালে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামীরা, আমাদের ক্যাম্পে, আমাদের বন্ধু-সহকর্মীদের মধ্যে ভিয়েতনাম সংগ্রামের বই, চে’র গেরিলা যুদ্ধসংক্রান্ত বই অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।
টিপু: প্রভাবটা কি অন্যদের মধ্যে কাজ করেছিল?
মতিউর: না, এটা বলব না যে, সবার মধ্যে এই প্রভাব কাজ করেছে। তবে বামপন্থীদের মধ্যে একটা প্রভাব ভালোই কাজ করেছিল। আমরা যদি ওইভাবে দেখি—মুক্তির সংগ্রাম পরিচালনার একটা প্রধান জায়গা ছিল কলকাতা। সেখানে কিন্তু ভারতের শিল্পী, সংস্কৃতিসেবী, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদেরা আমাদের সংগ্রামে বিপুলভাবে সমর্থন দেয়। সেখানে আমরা দেখতে পাই, সিপিআই মানে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার উদ্যোগী ভূমিকা ছিল। তারা কিন্তু সর্বাত্মকভাবে পুরো ৯ মাস জুড়ে—সেটা মুম্বাই, দিল্লি বা কলকাতা সারা ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নানাভাবে আমাদের মুক্তিসংগ্রামকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।
আমরা বিশ্বব্যাপী প্রগতিশীলদের সমর্থন, মূলত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থন পেয়েছি। শুরুতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম নিয়ে পরিষ্কার ধারণা-চিন্তা হয়তো ছিল না। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোডগর্নি ৩০ মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যার নিন্দা করে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন শক্ত ভাষায়। তাতে আমরা খুব উত্সাহিত ছিলাম। তবে কমিউনিস্ট পার্টি বা সরকার কী নীতি নেবে, সেটা নিয়ে একটু দ্বিধা ছিল। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। তারা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন ও বিশ্ব শান্তি পরিষদকে বাংলাদেশের পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। তখন বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন ভারতের রমেশ চন্দ্র। কমিউনিস্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা ছিলেন। তিনি দারুণ সংগঠক ও সুবক্তা ছিলেন।
বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলনে আমাদের পক্ষে জড়ো করতে বিশ্ব শান্তি পরিষদে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন রমেশ চন্দ্র। সিপিআইয়ের একটা প্রতিনিধি দলের কথা আমার মনে আছে। সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন এন. কে. কৃষ্ণান, রমেশ চন্দ্র [আরেকজনের নামটা ভুলে গেলাম]। তাঁরা ইউরোপের দেশে দেশে যান। তাঁদের আমন্ত্রণে বিশ্ব শান্তি পরিষদে কনফারেন্সে যোগ দিতে বুদাপেস্টে যান আব্দুস সামাদ আজাদ, দেওয়ান মাহবুব ও ড. সারওয়ার আলী। তিনজনের একজন আওয়ামী লীগের, একজন ন্যাপের আর একজন সিপিবির। তাঁরা বুদাপেস্ট থেকে মস্কো যান, সোভিয়েত ইউনিয়নে যান। এভাবে কমিউনিস্ট-প্রগতিশীলদের বিশ্বজনমত তৈরির একটা বড় ভূমিকা পালন করেন।
টিপু: আরও জনপ্রিয় ব্যক্তিরা তো ভূমিকা পালন করেছে?
মতিউর: আমরা বলি যে শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতে নয়, আমরা জানি ১ আগস্ট রবিশঙ্কর, জর্জ হ্যারিসনের ‘কনসার্ট ফর বাংলাদেশ’ আমাদের পক্ষে বিরাট জাগরণ, সাংস্কৃতিক জাগরণ, জনমত তৈরি করতে ভূমিকা পালন করেছে। আমরা এত দিন এটাই জানতাম। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা অনেক গবেষণা করে আরও বেশ কিছু এ রকম অনুষ্ঠানের খোঁজ পেয়েছি। যেমন ধরেন, মুম্বাইতে একটি বড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছিল ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। মুম্বাইয়ের ওই অনুষ্ঠানে সেরা এমন কোনো শিল্পী, গায়ক, অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, পরিচালক বাদ ছিলেন না, যোগ দেননি। একইভাবে আমরা দেখতে পারি ওভাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী বেলা ১১ থেকে রাত ১১ পর্যন্ত রক কনসার্টে ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি। পরে আরও জানতে পারি, রবিশঙ্করের জ্ঞাতিভাই বীরেন্দ্র শঙ্কর একটা অনুষ্ঠান করেছিলেন লন্ডন ও অন্যান্য শহরে। সেখানে দেখা যায়, ভারতের বিশিষ্ট শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী, রুমা গুহঠাকুরতা, সবিতাব্রত দত্ত এবং বাংলাদেশের দুজন লোকসঙ্গীতশিল্পী মোশাদ আলী ও হাসান আলী সরকার উপস্থিত ছিলেন। লন্ডনের কয়েকজন যন্ত্রশিল্পী এবং অস্কার বিজয়ী অভিনেত্রী গ্লেন্ডা জ্যাকসন সেখানে কবিতা পাঠ করেছিলেন। পরে আরও দেখলাম, নিউইয়র্কে কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে অ্যালেন গিন্সবার্গের সঙ্গে রুশ কবি আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি কবিতা পাঠ করেন। তো বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারটা নানাভাবে সামনে এসেছে। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো মিছিল করেছেন আমাদের পক্ষে। বলেছেন, এটা আমার পক্ষে খুব স্বাভাবিক বাংলাদেশের পক্ষে থাকা; কারণ, রবীন্দ্রনাথের ভাষা যেহেতু বাংলা, বাংলাদেশে মানুষও ওই ভাষায় কথা বলে। এভাবে বিশ্বব্যাপী একটা আন্তর্জাতিক জনমত তৈরি হলো। এসব ক্ষেত্রে কিন্তু বামপন্থীদের একটা ভালো ভূমিকা, বড় অবদান আমরা দেখি।
টিপু: সেখানে ইন্দিরা গান্ধী বা ভারতের ভূমিকা...
মতিউর: পৃথিবীজুড়ে আমরা বিরাট একটা পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখলাম। সেটা নিয়েই কিন্তু মুক্তি সংগ্রাম এগিয়েছে। সেখানে ভারত সরকারের ভূমিকা, ইন্দিরা গান্ধীর বড় ভূমিকা এবং অবশ্যই বলতে হবে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা, প্রগতিশীল গোষ্ঠীর ভূমিকা, সারা দেশের মানুষের অবদান ছিল। তাদের আমরা যেভাবেই বলি না কেন, তাদের এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, বহুদিনের পরিকল্পনা ছিল, অন্য উদ্দেশ্য ছিল—সাধারণ মানুষের ভূমিকা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত ভূমিকা, তাঁর পরামর্শক, পি এন হাকসার, ডি পি ধর—আমাদের ভোলা উচিত না তাঁদের অবদানকে। বিশ্বযুদ্ধের একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।
সেখানে আমরা দেখি দারুণ কৌশল, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনায় বা এই বিশ্ব জনমত তৈরি, সব মিলিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর একটা সেরা নেতৃত্বের অবস্থান দেখি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আজকে অনেক টানাপোড়েন, অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক কিছু আছে, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে এই বন্ধনটা একাত্তরে শক্তিশালী ছিল। পরে কী হলো না হলো, সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক-বিতর্ক আমাদের মধ্যে হতে পারে। কিন্তু একাত্তর এবং আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে ভারতের সমর্থন ছাড়া এত দ্রুত বিজয় সম্ভব ছিল না।
টিপু: কোনো প্রশ্ন তুললে কি অন্যায় হবে?
মতিউর: প্রশ্ন তুললে অন্যায় হবে না। তবে আলোচনা হতে পারে, তাত্ত্বিক অলোচনা হতে পারে, ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ হতে পারে। যেমন আশির দশকের শেষ দিকে একটা সময় সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের বই—একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা পড়ে আমি অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে প্রতিটি দেশ তার তার নিজ স্বার্থে এখানে অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সমর্থন এটা একটা আদর্শের ব্যাপার—এইভাবে না ভেবে এটা ভারত তার জাতীয় স্বার্থে, চীন তার জাতীয় স্বার্থে, সোভিয়েত তার জাতীয় স্বার্থে, আমেরিকা তার জাতীয় স্বার্থে অবস্থান নিয়েছে। এটা কেমন ব্যাপার! এ কথাটা আমি অনেকটাই মানি এখন। তখন আমার মধ্যে খুব প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। এটা কেমন কথা হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন এটা সমর্থন করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, এটা তাদের প্রগতিশীল একটা ভূমিকা, একটা মানবিক ভূমিকা ইত্যাদি। এটা ঠিক, সবশেষে একটা রাজনীতি তো থাকেই! সেটা তার দেশীয় রাজনীতি, আঞ্চলিক রাজনীতি ও বিশ্বরাজনীতির মধ্যেও এটাই সত্য, বাংলাদেশের একটা অবস্থান তৈরি হয়ে গিয়েছিল তখন। ‘এই রাষ্ট্রগুলো তার তার মতো তখন’ ওই তর্ক-বিতর্কে না গিয়েই বলতে পারি, সোভিয়েতের ভূমিকা ছাড়া ভারতবর্ষের পক্ষে ওই অবস্থান নেওয়া সম্ভব ছিল না সেই একাত্তরে। তাদের এই জোরালো সমর্থন, এটার একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। চীন তখন জটিল রাজনৈতিক আবর্তে। ওই একাত্তরেই তো কিন্তু চীন-আমেরিকা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূত্রপাত! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ভূমিকা বা তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা কিসিঞ্জারের কথাও জানি।
টিপু: আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জনমত তৈরি করার অনেক কাজ বামপন্থীরা করেছে। এটা কি বলা যায়?
মতিউর: এটা অনেকটাই বলা যায়। মানে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন, দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি, ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর বাইরে ইতালি, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, গ্রেট ব্রিটেন—খুব বড় আকারে শক্তিশালী-প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেছিল। তারা কিন্তু খুব ভালো ভূমিকা রেখেছিল। সোভিয়েত সমর্থিত আন্তর্জাতিক ছাত্রসংগঠন, আন্তর্জাতিক যুব সংগঠন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন, আন্তর্জাতিক নারী সংগঠন—বিশ্বব্যাপী এ সংগঠনগুলো ছিল। এ ছাড়া সামনে ছিল ছিল বিশ্ব শান্তি আন্দোলন। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সমর্থনে আন্দোলনকে গড়ে তোলা এবং এটাকে লড়্গ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতে ও বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা ছিল। আমার ভালোবাসায় বাড়ানো হাত বইটিতে দেখবেন, কলকাতা বা ভারতব্যাপী যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সমর্থনের যে নাগরিক উদ্যোগ ছিল। তার পেছনে সিপিআই ও তাদের সমর্থক, লেখক, শিল্পী, বুদ্ধিজীবী—তাঁদের বিরাট অবদান ছিল।
টিপু: বামপন্থীদের ব্যাপারে ভারত সরকারের মনোভাব কেমন ছিল?
মতিউর: শুরুতেই, আমাদের বামপন্থী সংগঠনগুলোকে ভারত সরকার প্রথম দিকে সমর্থন, সহযোগিতা করেনি, করতে চায়নি। যদিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারত সরকারের মধ্যে সমর্থন, সহযোগিতার মনোভাব ছিল শুরু থেকে। কিন্তু তারাও পরিষ্কারভাবে স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি, দল বা সংগঠনগুলোর ভূমিকা কেমন, কী—বুঝতে বা জানতে কিছুটা সময় নিয়েছিল। তারপর তারা জেনে-বুঝে, তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে প্রবাসী সরকারের সব কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে। তবে আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা অংশ চায়নি যে, বামপন্থী বা সিপিবি বা অন্যদের সহায়তা করুক। ভারত সরকারের মধ্যেও সন্দেহ, অবিশ্বাস ছিল। কারণ, তখন পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন অঞ্চলে চারু মজুমদার, উগ্র বামপন্থী সশস্ত্র আন্দোলন চলছিল। তাদের মধ্যে ভয় ছিল, এই বামপন্থীদের যদি সশস্ত্র ট্রেনিংয়ের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তবে ভবিষ্যতে এটা ভারতের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হতে পারে। এমনকি, এটা বাংলাদেশের ভেতরে-বাইরেও হতে পারে। এটা নিয়ে ভারত সরকারের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল। আওয়ামী লীগ ও প্রবাসী সরকারের ভেতরেও এটা ছিল। এই চিন্তাভাবনাটা কাটতে সময় লাগে।
একপর্যায়ে সিপিবির নেতৃবৃন্দ ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। সিপিআইয়ের কেন্দ্রীয় নেতারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। এভাবে ইন্দিরা গান্ধী সম্মত হন—ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি-ছাত্র ইউনিয়ন গেরিলা বাহিনী গঠন, ট্রেনিং এবং আমাদেরকে নানাভাবে সহযোগিতা করতে। এটা করতে বেশ দেরি হয়ে যায়। সে জন্য যখন তারা ট্রেনিং শেষ করে বেশ কিছু দল দেশের ভেতরে সম্মুখ সমরে অংশ নিলেও আরও অনেকেই অংশ নিতে পারেনি। এটা অবশ্য সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ বা নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর অনেকেই শেষ পর্যন্ত এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পারেননি।
টিপু: একটা বিষয় বলতে চেয়েছিলেন—ঐক্য কীভাবে বিভেদে পরিণত হলো?
মতিউর: সত্তরের নির্বাচনে বিপুল বিজয় এবং একাত্তরে মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশ পেলাম আমরা। এর পেছনে ছিল একটা ধারাবাহিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। বাষট্টি থেকে উনসত্তর পর্যন্ত ধারাবাহিক এই আন্দোলনগুলো, বহুমুখী কর্মকা–গুলো বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছে এবং এগুলো বড় থেকে আরও বৃহত্তর হয়েছে। তার মধ্যে কিন্তু পাকিস্তান সামরিকগোষ্ঠীর ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্যে পরাজয় ঘটে। বাংলাদেশের জনগণের কাছ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়, বাংলাদেশের বিজয়। শুধু নির্বাচনে বিজয় নয়, স্বাধীন রাষ্ট্রের গঠনেরও দ্বারপ্রান্ত্মে আমরা পৌঁছে গেছি—এটা তখন পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন এত পরিষ্কার না হলেও এখন তো আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু একটা দুঃখজনক ঘটনা হলো, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পরপরই ছাত্র সমাজের সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বা রাজনৈতিক আন্দোলনে আর সেই ঐক্য থাকেনি। এটা বিভক্ত হয়ে যায়। রাজনৈতিক জোট ‘ডাক’ও আর থাকেনি। সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিভক্ত হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে এককভাবে অংশগ্রহণ করে। আবার স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সময়েও কিন্তু এই সমন্বয়-সমঝোতা হয়নি। ভারত সরকারের বহু চেষ্টা-উদ্যোগের ফলে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক দলগুলোর একটি সম্মিলিত উপদেষ্টা কমিটি হলেও এটা কার্যকর হয়নি। শুধু একটি বৈঠক হয়েছিল মাত্র।
টিপু: পরে এই ঐক্য নিয়ে কী হয়েছিল?
মতিউর: বাংলাদেশের রাজনীতির অতীত ইতিহাস বলে, আওয়ামী লীগ নিজেদের প্রয়োজন ছাড়া কিংবা নিজেরা বাধ্য না হলে কখনোই তারা ঐক্য বা সমঝোতায় যায় না। কোনো দল বা রাজনৈতিক সংগঠনকে তারা মেনে নিতে পারে না। ষাটের দশকে বলেন, সত্তরের দশকে স্বৈরাচার জিয়া সরকারবিরোধী আন্দোলন, এরশাদবিরোধী আন্দোলনে তারা নানা ধরনের ঐক্য ও অন্যান্য দলকে আওয়ামী লীগ সঙ্গে নিয়েছে, যখন তারা এককভাবে অগ্রসর হতে পারে না তখন। তারা অন্য দলগুলোকে নেয়, কিন্তু ওই সমঝোতা ঐক্যটাও তত দিনই থাকে, যত দিন তাদের প্রয়োজন পড়ে। এখন আপনি দেখবেন, চৌদ্দদলীয় একটা বৃহত্তর ঐক্য আছে। তবে তার কোনো কার্যকারিতা নেই, কোনো অবস্থান নেই, কোনো বৈঠক নেই, কোনো কাজ নেই। যেটা হয়েছে যে, এ ধরনের সমঝোতা দেখানো, যা তাদের জন্য প্রয়োজন। আর ছোট ছোট দল একটা-দুটো সিটের জন্য তাদের সঙ্গে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে তারা সরকারের আইন-নীতি পছন্দ করে না, মানে না। সেটা আবার বলতেও পারে না, সইতেও পারে না। কিছু করতেও পারে না, তাদের কোনো অবস্থান নেই।
টিপু: তাহলে কি একাত্তরে রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্য অগ্রসর হয়নি?
মতিউর: শেষ পর্যন্ত একটা উপদেষ্টা কমিটি হলো। একটা বৈঠকও হলো। এটা অনেকটা লোকদেখানো হলো। এটা ভারত সরকারের চাপে পড়ে কিছুটা সম্মত হয়ে করলেন। ওটার ব্যাপারে প্রবাসী সরকার ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের তেমন কোনো সমর্থন ছিল না। শুধু একটি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকের মধ্যেই ওটার শুরু এবং শেষ হয়ে যায়।
ভারতের জন্য এটা খুব জরুরি ছিল। কারণ, ভারতের জন্য প্রয়োজন ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সোভিয়েতের সমর্থন। সোভিয়েতের সমর্থনের জন্য প্রয়োজন ছিল, এখানে জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের একটা ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রূপ তৈরি করা, এটাকে টিকিয়ে রাখা। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা ভারতের সরকারের কাছে বা নীতিনির্ধারকের কাছে এটা ছিল—প্রধান শক্তি আওয়ামী লীগ এটা ঠিক আছে, কিন্তু অন্য রাজনৈতিক শক্তি প্রধানত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয়, সমঝোতা ও ঐক্য দরকার। তখন বিশ্বব্যাপী সোভিয়েতের সমর্থিত বা তাদের সঙ্গে যুক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের দেশে দেশে তাদের একটা মূল লক্ষ্যই ছিল এটার একটা ঐক্যফ্রন্টের মাধ্যমে মুক্তি আন্দোলনকে পরিচালনা করা, যেটা প্রয়োজন সফলতার জন্য। সেটা কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছেন এবং পি এন হাকসারের পাশাপাশি ওটা মূলত ডি পি ধরও চেষ্টা করেছেন।
সেই অর্থে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পরে নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা যে মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছালাম, বিজয়ী হলাম, কিন্তু আমাদের জাতীয় ঐক্যটা হলো না, থাকল না। রাজনৈতিক শক্তির ঐক্য হলো না। ছাত্র আন্দোলনের ঐক্য থাকল না এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য আমাদের থাকল না।
বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী হলেন। নতুন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করা হলো। দেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু করলেন। চারিদিকে নানা সমস্যা। ভেঙে যাওয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগসহ সকল কিছুর নতুন যাত্রা শুরু হলো। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ জরুরি বিষয়—বড় কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার। নতুন সরকার দ্রুত সংবিধান তৈরি করল, নির্বাচন করল, আবার বিপুলভাবে বিজয়ী হলো। সে নির্বাচনের কিছু কিছু আসন নিয়ে প্রশ্ন উঠল, তর্ক হলো এবং কিছু আসন জোর করে ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগও ছিল। অর্থাৎ যে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সমঝোতা এবং রাজনৈতিক ও ছাত্র আন্দোলনের ঐক্যর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে পরাভূত করা, তাতে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে বিজয়ী হলো আওয়ামী লীগ। জাতীয় ঐক্যের যে সমঝোতার ব্যাপার—যেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা রাষ্ট্রকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, সেটা পরে থাকল না।
স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নীতি ছিল—সরকারের ভালো কাজের সমর্থন করা, মন্দ কাজের সমালোচনা করা। এটা তারা করেছে। কিন্তু মানুষ এটা পারেনি। মানুষ দেখেছে, সমর্থনটাই প্রথম। একপর্যায়ে এসে, সিপিবি ‘ব্যর্থ সরকার বাতিল করো’ স্লোগানও তারা তুলেছিল। কিন্তু মানুষের কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমন কোনো সাড়া মেলেনি।
টিপু: সিপিবির এ দাবি কত সালে?
মতিউর: এটা ’৭৪ সালের দিকে। এই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ত্রিদলীয় জোট হলো—গণ ঐক্যজোট। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য জোট। অর্থাৎ ’৭২/৭৩ সালের পর—’৭৪ দুর্ভিক্ষ, মানুষের মৃত্যু, সরকারের ভেতরে-বাইরে দুর্নীতি, সরকারের অব্যবস্থাপনা এবং রক্ষীবাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বাড়াবাড়ি—এগুলো মানুষের মধ্যে নানা ধরনের প্রশ্ন, ক্ষোভ-বিক্ষোভ তৈরি করে। এটা ঠিক, সে সময়ে জাসদের আন্দোলনের কৌশল ও উগ্রপন্থা অবলম্বন—এগুলো গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এই অবস্থার মধ্যে সিপিবি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সমালোচনা, ঐক্য ও সংগ্রামের নীতিতে ত্রিদলীয় জোট গঠন—এটাকে মানুষ গ্রহণও করেনি। মানুষ দেখেছে, ন্যাপ-সিপিবি আওয়ামী লীগের সঙ্গে আছে। সে জন্য ‘ব্যর্থ সরকার বাতিল করো’—এ বিষয়গুলো মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। মানুষ বুঝতেই পারেনি।
চুয়াত্তরের ডিসেম্বরে জরুরি আইন প্রয়োগ করা হলো, রাজনৈতিক কর্মকা– বন্ধ করা হলো, পরে যখন জানুয়ারি ’৭৫-এ এক দল গঠনের ঘোষণা হলো, একদলীয় সরকার গঠন করা হলো, সব রাজনৈতিক দল বেআইনি হয়ে গেল, চারটি পত্রিকা ছাড়া সব পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেল, অনেক অধিকার সংকুচিত করা হলো, এটা মানুষের মধ্যে নানা রকম প্রশ্ন ও বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। কিন্তু সিপিবি-ন্যাপ তো আনুষ্ঠানিকভাবে এক দলে যোগ দেয়। বাকশাল গঠনে যোগ দেয়। ন্যাপ-সিপিবির প্রকাশ্যে দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা অংশ নেয়। যদিও তাদের সিদ্ধান্ত ছিল, গোপনে নিজস্ব একটা জোট কাঠামো অব্যাহত রাখবে।
টিপু: সিপিবি তো আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশালেই যোগ দেয়...
মতিউর: হ্যাঁ, সিপিবি আনুষ্ঠানিকভাবে বাকশালে যোগ দেয়। তবে সিপিবি ঐক্যজোটের কথা বলেছিল। সংকট সমাধানে ঐক্য জোটই করা ভালো এবং বঙ্গবন্ধুর সামনেও এটা বলার চেষ্টাও ছিল—একদল না করে ঐক্য জোট করলে ভালো হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এটা শোনেননি। শেষ পর্যন্ত ন্যাপ-সিপিবি বাকশালে যোগ দেয়।
পঁচাত্তরের জুন মাসে বাকশাল গঠন করা হলো। আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু নিহত হলেন। এটা একটা বড় রাজনৈতিক তাত্ত্বিক প্রশ্ন, বাকশাল গঠন ঠিক হয়েছিল কি? আমি তো বাকশালের যুবলীগ জাতীয় কমিটির সদস্য ছিলাম। আমি সিপিবির মনোনীত প্রার্থী হিসেবে না, জাতীয় যুবলীগের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে বাকশালে যোগ দিয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা এবং আমার সাংগঠনিক কার্যক্রমের ওপর আস্থা-বিশ্বাসের কারণে মনোনীত হয়েছিলাম। আমি মনে করি, বাকশালে সিপিবির যোগ দেওয়া ঠিক হয়নি। কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ বিলুপ্ত করে একক দলে যোগ দেয়। আমি সিপিবির তৃতীয় কংগ্রেসের আগে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব এনেছিলাম, এটা বলা—বাকশালে যোগদান আমাদের ভুল হয়েছিল।
টিপু: স্বাধীন হওয়ার পর সংকট কি আরও গভীর হতে থাকে?
মতিউর: বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে অনেক সফলতা ছিল, আবার অনেক ক্ষেত্রে সফলতা আসেনি। যে জন্য মানুষের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভও ছিল। এরই সুযোগ নিয়েছিল রাজনৈতিক শত্রুরা। সেটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সফলতার সঙ্গে কিছু ব্যর্থতাও ছিল। আর এমনিতে দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্য, অর্থনৈতিক জীবন-যাপন, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে মানুষের মনে ক্ষোভ ছিল। অন্যদিকে সশস্ত্র বাহিনীর ভেতরে একটা ক্ষোভ ছিল। যারা বাংলাদেশের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, তাদেরকে দুই বছরের সিনিয়রিটি দেওয়া হয়, এটা করে পাকিস্তান থেকে যে বিপুলসংখ্যক সেনাসদস্য ফিরে আসেন, তাঁরা অনেকেই জুনিয়র হয়ে যান। এটা নিয়ে তাঁদের ভেতর একটা বড় রকমের ক্ষোভ ছিল। অন্যদিকে রক্ষীবাহিনী গঠন ও তাদের অবস্থানটা সেনাবাহিনী মানতে পারেনি। এসব নানা কারণে ক্ষোভ ছিল। ১৫ আগস্টের হত্যাকা–ের পর সেনানেতৃত্ব এই অভ্যুত্থ্যানকে মেনে নিয়েছিলেন।
টিপু: আচ্ছা, মুক্তিযুদ্ধের পর দেশে ফিরলেন কবে?
মতিউর: দেখেন, আমরা অনেকেই দেশে, ঢাকায় পৌঁছে গিয়েছিলাম ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়। আমাদের নেতৃত্ব, আমরা জানতে পারছিলাম যে, মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আমরা ১২ বা ১৩ তারিখে আগরতলা থেকে যাত্রা শুরু করলাম আমাদের দলবল নিয়ে। মনে পড়ে আমাদের নেতৃত্বে ছিলেন কমান্ডার রউফ। আগরতলা মামলার আসামি ছিলেন। আমাদের গেরিলা বাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছিলেন। সঙ্গে আরও ছিলেন ডা. সারওয়ার আলী ও প্রকৌশলী মর্তুজা খান প্রমুখ।
মুক্তিযুদ্ধের প্রায় আট মাসই ছিলাম আগরতলায়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের নানা কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম।
টিপু: আগরতলা থেকে রওনা দিলেন কি ১৩ ডিসেম্বর?
মতিউর: ১২ বা ১৩ ডিসেম্বর হবে। আসলে আমাদের নেতৃত্বের কাছে এই তথ্য ছিল যে, স্বাধীনতাসংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে এসেছে। দেশের ভেতরে সবাইকে যেতে হবে, সাধ্যমতো শেষ পর্যায়ের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। আমাদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের দলের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক নৌবাহিনীর কমান্ডার আবদুর রউফ। সেই আগরতলা থেকে কুমিল্লা হয়ে নরসিংদী পেরিয়ে আমরা ঢাকার ডেমরায় পৌঁছাই ১৬ ডিসেম্বর। তখন বিকেল চারটা হবে। পুরোটা কিন্তু হাঁটা পথ। তখন তো যানবাহন বলতে কিছু ছিল না। তাই ডেমরা থেকে হেঁটে হেঁটে যখন ঢাকা শহরের গোপীবাগে পৌঁছাই, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে।
কোথায় যাব, কী করব, তখন কয়েকজন মানিক ভাইয়ের বাসায় যাই। মানিক ভাইয়ের বাসা তখন গোপীবাগে ছিল। ওই বাসায় রাতযাপন করে ঘুম থেকে উঠে সকালবেলা রিকশায় করে টিপু সুলতান রোড হয়ে নবাবপুর হয়ে বাসায় আসি। তখন ভাইবোনরা সবাই ঘুমে। পুরো পথ একদম নিরিবিলি, রিকশা একদম কম। টিপু সুলতান রোড হয়ে নবাবপুর দিয়ে আসার সময় রাস্তায় কিছু মানুষের মৃতদেহ দেখলাম।
টিপু: মুক্তিযুদ্ধের পর দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে, তার শাসনকাঠামো কেমন হবে, মানে রাষ্ট্রটা চলবে কীভাবে—সেটা নিয়ে পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?
মতিউর: আমি ’৭৩ সালে পার্টির কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হই। বড় রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক—এই কাজগুলো করতেন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী, আমি সেখানে ছিলাম না। তবে আমি এটা বলতে পারি, বিভিন্ন সময়ের দলিল বা অন্যান্য প্রকাশনা যা হয়েছে, এগুলো অনেক সময় প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমার হয়তো কিছু ভূমিকা ছিল। সে সময়ে আমাদের সিপিবির ওই অভিজ্ঞতা ছিল না যে বাংলাদেশের মতো একটা নতুন রাষ্ট্রের অবস্থা, পরিস্থিতি এবং ভবিষ্যতের কাঠামোগত বা নীতি-নির্ধারণ, নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে কী হওয়া উচিত, সেটা নির্ধারণ করা—তেমন বড় যোগ্যতা ছিল না। যেটা ছিল, কতগুলো সাধারণ অভিজ্ঞতা বা অর্জিত জ্ঞান থেকে ভাবতাম ও বলতাম—সমাজতন্ত্রই সমাধান। অর্থাৎ বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রের পথে যেতে হবে। কিন্তু তখনকার বাংলাদেশের ৭-৮ কোটি মানুষ, বাংলাদেশের কৃষি, বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিল্প ও কলকারখানা, রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা পররাষ্ট্রনীতি—সব ব্যাপারে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না।
আমরা সাধারণ কতগুলো ধারণা থেকে কথা বলতাম, আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে দেখে শেখা, সমাজতান্ত্রিক কতগুলো ভাবনা-চিন্তা করা, সেটার যতটুকু বাস্তব ছিল—সে সব খুব বুঝে প্রণয়ন করেছিলাম। আর বলা যাবে না যে এগুলো বাস্তবানুগ ছিল, পরে তো সেটা প্রমাণিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতার পরে সংবিধান রচনা করেছে, সেটি খুবই প্রগতিশীল ছিল। অন্যদিকে জাতীয়করণ করল, কৃষিক্ষেত্রে কতগুলো নীতি আনল, শিক্ষানীতি প্রণয়ন করল, শিল্প-কলকারখানা করল, কিন্তু কোনটা শেষ পর্যন্ত ভালোভাবে চলল? হ্যাঁ, প্রথম দু-তিন বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারের দেশ পুনর্গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে, বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেও—আমি বলব বেশ কিছু সফলতা দেখেছি—যেগুলোকে আমরা সমর্থন করেছি। কিন্তু ১৯৭৩ সালের পরে খাদ্যসংকট, ’৭৪ সালের পর থেকে রাজনৈতিক সংকট, বিরোধী দলের রাজনীতির তত্পরতা বা সরকারি দলের ভেতরে দুর্নীতি, বিভেদ, সন্ত্রাস, পরে দুর্ভিক্ষ—এগুলো একটা গভীর সংকট তৈরি করে দেশে।
টিপু: আপনারা তো সরকারকে সমর্থন করেছিলেন?
মতিউর: সিপিবি শুরু থেকেই দেশ পুনর্গঠন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এসবের লড়্গ্যে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারের প্রতি একটা সমর্থনসূচক নীতি নিয়েছিলাম। আমরা জোট গঠন করে দেশ পরিচালনার কথা বলতাম। তিনি ’৭৩ সালে একটা ত্রিদলীয় জোট গঠন করেছিলেন। ওই সেই আবার ওই কথাই—সংসদে তাদের সদস্য সংখ্যা ২৯৩ জন, ৩০০ জনের মধ্যে। তারপরেও তাঁরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন—সরকারের ভেতরে, দলের ভেতরে, বিরোধী দলের দিক থেকে ও মানুষের দিক থেকে। বঙ্গবন্ধু সরকার পেরে উঠছিল না পরিস্থিতি সামাল দিতে। সে কারণেই তারা ত্রিদলীয় জোট গঠন করেছিল। যার কোনো কোনো প্রভাব সৃষ্টিকারী ভূমিকা ছিল না। সেটা কোনো কার্যকর ভূমিকা নিতে পারেনি। পরে ’৭৪ সালে এসে সিপিবি একপর্যায়ে দাবি তুলেছিল, ‘ব্যর্থ সরকার বাতিল করো...।’
টিপু: কিন্তু মানুষ কি এটা নিয়েছিল...
মতিউর: প্রথমত, মানুষ বোঝেনি যে, আমাদের নীতি এই—‘ঐক্য সংগ্রামের নীতি’—ঐক্য করব আবার সংগ্রামও করব। দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা ঐক্য করব, আবার ব্যর্থ নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামও করব। সে জন্য শুরু থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের কোনো নীতিগত ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রের ভালো-মন্দের ক্ষেত্রে বা কোনো পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিপিবি ও ন্যাপ কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি। অথচ সহযোগিতার নীতি, ত্রিদলীয় জোটের ঐক্যের নীতির কারণে সরকারের ব্যর্থতার দায় কিন্তু নিতে হয়েছে সিপিবি-ন্যাপকেও। এবং ছাত্র ইউনিয়নকেও নিতে হয়েছে।
’৭৪ সালের পর থেকে তো ধীরে ধীরে ডিসেম্বরে জরুরি অবস্থা জারি, জানুয়ারিতে সংবিধান পরিবর্তন, এক দলের সিদ্ধান্ত, পরে জুন মাসে গিয়ে একদল গঠন ও কমিটি গঠন—এগুলো করা হলো। এদিকে বঙ্গবন্ধু একদলীয় শাসনব্যবস্থার দিকে চলে গেলেন।
সাধারণভাবে মানুষ এ রকম বড় পরিবর্তনের পক্ষে ছিল বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে জন্য এই কার্যক্রম জনপ্রিয় হয়নি। ন্যাপ-সিপিবির আনুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল, আমরা বঙ্গবন্ধুকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে একটা ঐক্য করেন, ঐক্যজোট করেন, ঐক্যজোটের মধ্যে আমরা সবাই থাকি। সেভাবে দেশ পরিচালিত হবে। এটাও খুব জোরালোভাবে আমরা তুলে ধরতে পারিনি। এটা বোঝানো যায়নি, এটা শুনতেও চাননি, কেননা তখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। ওই অবস্থায় ন্যাপ-সিপিবি এই একদল বাকশাল ব্যবস্থাকে সমর্থন করে এবং তাতে যোগ দেয়। এসব পরিবর্তন হচ্ছিল উপরতলায়। কেউ তেমন কিছু জানত না। মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও অবিশ্বাস ছিল। তখনো কিন্তু বাংলাদেশের প্রধান বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা পরে আবার আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ঠ ও বড় সমর্থক হয়ে ওঠেন, তাঁরা কিন্তু একদলের এই গঠনকে তখন সমর্থন করেননি।
যে দল আওয়ামী লীগ—২৪ বছর লড়াই-সংগ্রাম করল ব্যক্তি ও মতপ্রকাশের জন্য, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য, স্বাধীনতার জন্য—তারপরও স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধে এত ত্যাগ-রক্ত, আত্মত্যাগের পরে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে পুরো ব্যবস্থার পরিবর্তন—এটা একটা আকস্মিক ছিল। আর পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নৃশংস হত্যাকা–ের পর বড় পরিবর্তন ঘটল! বঙ্গবন্ধু হত্যা, সপরিবারে নিহত হওয়া—এগুলোকেও মেনে নেওয়া যায় না। দেশের রাজনীতির সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেলো।
টিপু: বামপন্থীদের লড়াই-সংগ্রামে ত্যাগ তো অনেক। কিন্তু রাজনীতিতে দাঁড়াতে পারলেন না কেন ?
মতিউর: সিপিবি-ন্যাপ কর্মী-সমর্থক, নেতৃত্ব—মানুষগুলো তো সৎ, নিষ্ঠাবান ছিলেন। অনেক কষ্ট তাঁরা করেছেন। বছরের পর বছর জেল খেটেছেন। নির্যাতিত হয়েছেন। পরিবারের পর পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে। তাঁরা কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্রের সংগ্রাম, প্রগতির সংগ্রাম, শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম, ছাত্রদের সংগঠিত করা—এসবে অগ্রণী ছিলেন। তবে নতুন একটা রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে বিকল্প চিন্তা, বিকল্প ভাবনার ক্ষেত্রে বলব না যে, খুব পরিষ্কার ধারণা ছিল। তবে এটা ছিল, আমরা সমাজতন্ত্র চাই। মানুষের মুক্তি ও কল্যাণ চাই। সমাজতন্ত্র মানে আমরা সোভিয়েতপন্থী ছিলাম অর্থাৎ মস্কো মডেল বা তাদের প্রদর্শিত পথ এখানে কাজ করবে।
তখন একটা তত্ত্ব—যেটা আগেই থেকেই ছিল—আমাদের মতো দেশগুলো, মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকার দেশগুলো প্রগতিশীলেরা প্রধান শক্তি হিসেবে যেখানে তাদের উপস্থিতি আছে, সেখানে তাদের সাহায্য-সমর্থন করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক শক্তি। সে জন্য ঠিক একই পথে, সামন্তবাদ থেকে ধনবাদ, তারপর পুঁজিবাদ অতিক্রম করে সমাজতন্ত্র হবে—দীর্ঘ সেই কঠিন যাত্রাপথের দরকার নেই। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সমর্থনে পুঁজিবাদের এই পর্যায়কে অতিক্রম করে অ-ধনবাদী পথে সমাজতন্ত্রে যাওয়া সম্ভব। যদিও তখনো কোনো রাষ্ট্রে এ রকম দেখা যায়নি। আলজেরিয়া, ইরাক ও সিরিয়ার কথা বলা হতো। দক্ষিণ ইয়েমেনের কথা বলা হতো। এসব দেশে যেসব কমিউনিস্ট পার্টি ছিল, তাদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন শুরু হয়ে গেছে। এটা একটা বড় ভুল ছিল সোভিয়েত বিশ্লেষক ও তাত্ত্বিকদের। আবার আফ্রিকার কতগুলো দেশ—ইথিওপিয়া, সোমালিয়া বা বুরকিনা ফাসো এবং মোজাম্বিক, এঙ্গোলা, গিনি [বিসাউ] সশস্ত্র সংগ্রাম করে মুক্তি আন্দোলনে বিজয়ী হলো। বলা হতো, এ দেশগুলো অ-ধনবাদী পথে এগিয়ে চলছে। পুরো ধারণাটাই অবাস্তব ছিল। এটা পরে প্রমাণিত হলো। আমরা আমাদের মতো করে এর ব্যাখ্যা দিতাম, দেওয়ার চেষ্টা করতাম। কেউ কিন্তু বুঝতে পারতো না। অ-ধনবাদী পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উদাহরণ হিসেবে মঙ্গোলিয়ার কথাও বলা হতো। সেটাও তো সোভিয়েত ইউনিয়ন পাশের দেশকে দখল নিয়ে তারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর। সেই অবস্থাও এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোনোটাই টিকল না। তারপরে আফগানিস্তানে যদি দেখি, সেখানে কী নির্মম পরিস্থিতি!
টিপু: তাহলে পথ কী হবে? কী পথ হতে পারে?
মতিউর: এখানে আমার মনে হয়, স্বাভাবিক ধারায় যদি একটা দেশ অগ্রসর হয়ে যায়, দেশের ভেতরে রাজনৈতিক সংগ্রাম, অর্থনৈতিক সংগ্রাম, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও ব্যক্তির অধিকার, মানুষের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের অধিকার এবং তাদের লড়াই-সংগ্রাম, তাদের চাহিদা, তাদের দাবিদাওয়া—এসবের পক্ষে জনমত তৈরি করা, তার ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন তৈরি করা, সেটা রাজনৈতিক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়া, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তন নিয়ে আসা—এগুলো স্বাভাবিক পথ। এর চেয়ে ভালো পথ তো এখনো কোথাও বের হয়নি। এগুলোই হলো ইতিহাসের স্বীকৃত সত্য। আর এখন পর্যন্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের চেয়ে তো ভালো ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। যতই এর ভুলত্রুটি থাকুক না কেন, এর বাইরে অন্য কোনো পথে যাওয়া মানে হলো এটাকে একটা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া।
আমরা যদি আফগানিস্তানের কথা বলি, সেখানে রাজতন্ত্র ছিল। পরে দাউদ ক্ষমতা দখল করেন। আমরা জানি, লেনিনের সময় থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আফগানিস্তানের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। ১৯২১ বা ২২ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আফগানিস্তানের চুক্তি হলো। আমরা জানি যে আফগানিস্তানের তেল, খনিজ সম্পদ আহরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সোভিয়েতেরই অবদান ছিল বেশি। সেখানে সেনাবাহিনীর ভেতরে অল্পসংখ্যক হঠকারী বামপন্থী বা মার্কসবাদী সংগঠিত হয়ে শাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। পরে নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও খুনোখুনি করছিল—এই পটভূমিতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরি হস্তক্ষেপ করে। সোভিয়েত বাহিনী পরাজিত হয় সেখানে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসে আফগানিস্তানের ধ্বংস প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত করল। দেশটাকে কোথায় নিয়ে গেল! এখন তালেবানের হাতে সর্বময় ক্ষমতা। এটাই হলো বাস্তবতা।
যে জন্য আজকে দেখা যাচ্ছে, ওই যে দেশগুলো, অ-ধনবাদী পথে অগ্রসর হওয়া দেশ, তথাকথিত ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া—এখন আর দেশ হিসেবেই তো টিকে থাকতে পারছে না। ইরাকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ইয়েমেন তো দেশ নেই। ইথিওপিয়া তো বিভক্ত, দুর্ভিক্ষে জর্জরিত। সোমালিয়ার তো রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব নেই! অ্যাঙ্গোলা আর মোজাম্বিকে তো যাচ্ছেতাই পরিস্থিতি, দুর্নীতি ও স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এগুলো আসলে কী হলো! মাঝে মাঝে তো প্রশ্ন জাগে, আরোপিত কোনো ব্যবস্থা, বহিঃশক্তি বা বহির্বিশ্বের হস্তক্ষেপ, তাদের অস্ত্র, তাদের অর্থ, তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে কোনো দেশের আদৌ কি কোনো অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে? যদি না নিজ দেশের মানুষ তার মতো করে নিজেরা লড়াই-সংগ্রাম করে পরিবর্তন না করে।
আজকে যদি আমরা চীনের দিকে তাকাই, ভিয়েতনামের দিকে তাকাই—এই যে তারা পরিবর্তন নিয়ে আসছে, এখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী কি না, ভিয়েতনাম মার্কসবাদের পথে আছে কি না—নিশ্চয়ই এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তবে যদি দেখি, চীনের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে, রাষ্ট্রের অগ্রগতি হয়েছে, অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটেছে, লেখাপড়া ও বিজ্ঞান জগতে অগ্রগতি আছে, ক্রীড়া জগতে অগ্রগতি আছে—মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তো পরিবর্তন আছে, অগ্রগতি আছে। ভিয়েতনাম এখন অনেক অগ্রসরমাণ দেশ। বলতে পারি যে, কিউবাও এখনো টিকে আছে নিজের শক্তিতে। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ওদের নির্ভরতা ছিল অনেক। কিউবার অর্থনীতিটা রুগ্ন হয়ে পড়ছে। এই পথে কিউবার টিকে থাকার বাস্তবতা বা সম্ভাবনার ব্যাপারে প্রশ্ন আছে। তবে আশা করব, কিউবার কমিউনিস্ট পার্টি যদি কিউবার জনগণের কল্যাণ ও মুক্তির পথে থাকতে পারে, তারা সফল হয়, তাদের প্রতি আমাদের সব রকমের সহানুভূতি থাকবে। আজকের দুনিয়াতে এই বাস্তবতার বাইরে গিয়ে, অন্য কারও সমর্থন ও সহযোগিতা বা চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।
টিপু: তাহলে এখন সোভিয়েত সম্পর্ককে কীভাবে মূল্যায়ন করবেন?
মতিউর: এই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি—আমাদের তো সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়া, বিভিন্ন স্তরের গণসংগঠনের, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। এটা বলব, অন্ধভাবে আমরা সোভিয়েত নীতি সমর্থন করেছি। বুঝে, না বুঝে সমর্থন করেছি। তারা যতই বলুক, প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীন, তারাই সিদ্ধান্ত নেয়, আসলে এটা সত্য ছিল না। আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নিয়েছি, তারা পরামর্শ দিয়েছে। তাদের পরামর্শেই আমরা চলার চেষ্টা করেছি। আর যেখানে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি নিজের দেশেই সমাজতন্ত্র রাখতে পারল না, সক্ষম হলো না, তখন তারা অন্য দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, অন্য দেশের পরিবর্তন আনবে, সেটা অবাস@ব ছিল। আফগানিস্তান তো প্রমাণ করল, তাদের কোনো ধারণাই ছিল না আফগানিস্তান রাষ্ট্র, সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে। তাদের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ছিল—উজবেকিস্তান, কাজাকিস্তান, কিরগিস্তান, এসেত্মানিয়া, লাটভিয়া প্রভৃতি—যা-ই বলি না কেন, ইউক্রেন, বেলারুশ বা জর্জিয়া বাদ দিয়ে ওই দূরের প্রজাতন্ত্রগুলো যদি দেখি—এটার তো কোনো বাস্তবতা ছিল না। এটা তো পরে প্রমাণিত হলো এবং পুরো ব্যবস্থাই ভেঙে গেল। যারা নিজেরা নিজের দেশকে রক্ষা করতে পারল না—অনেক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে, অনেক বিরোধিতা থাকতে পারে, অনেক রকমের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত থাকতে পারে—বাস্তবতা হলো যে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারল না। এটা টিকে থাকল না। এটা ভেঙে পড়ল। বর্তমান ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার চলমান হামলা ও যুদ্ধ প্রমান করছে যে, তাদের মধ্যেও উগ্রতা ও জাতীয়তাবাদের গভীর প্রভাব রয়েছে।
এখন যদি বড় কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না-ও করি, শুরু থেকে সোভিয়েত শাসনব্যবস্থা যে একটা জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থা ছিল, একটা চাপিয়ে দেওয়া শাসনব্যবস্থা এবং একটা একদলীয়ভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যবস্থা, যেখানে ভোট নেই, নির্বাচন নেই, স্বাধীন মতপ্রকাশের জায়গা নেই, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই—এ রকম রাষ্ট্র তো এ দুনিয়ায় বর্তমান সমাজে আমরা ভাবতে পারি না। এটা গ্রহণযোগ্যও নয়। হ্যাঁ, কেউ বলতে পারে যে, চীনে কি সবাই কথা বলতে পারে? ভিয়েতনামে সবাই কি পারে? এসব নিয়ে তো তর্ক-বিতর্ক আছেই। কিন্তু আমরা দেখি, এটা চলে নাই, এটা হয় না, এটা হয়নি। এখানে আমাদের বড় ভুল হয়েছে; কারণ, আমরা আদর্শগতভাবে তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। আর্থিকভাবেও ছিলাম। এভাবেই সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট পার্টিকে একটা কেন্দ্র থেকে—আগে লেনিনের সময়ে ১৯১৮ সালে যে কমিন্টার্ন [কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল] করল, সেটার লক্ষ্যই ছিল, একটা কেন্দ্র থেকে সারা বিশ্বের সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম পরিচালিত হবে এবং নিয়ন্ত্রিত হবে। তাদের কথামতোই কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিগুলোকে চলতে হবে। যদিও ১৯৪২ সালে এসে এটা ভেঙে দেওয়া হয়। তবু পরে ওই ব্যবস্থাটাই কার্যকর থাকে ভিন্নভাবে।
বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল এবং বিশ্বব্যাপী তারাই এটাকে প্রভাবিত করত, পরিচালনা করত। এইভাবে একটা কেন্দ্র থেকে বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করার চিন্তাধারা ভুল, এটা সম্ভব নয়। প্রতিটি দেশ নিজের মতো করে—সেটা গণতন্ত্র হোক, সমাজতন্ত্র হোক, এই লড়াই-সংগ্রামকে এগিয়ে নেবে। পরিচালনা করতে হবে। আসলে বাংলাদেশের দিকে যদি আমরা তাকাই, ১৯৫২ সাল, ১৯৬২ থেকে ১৯৭১ সাল দেখি, এই সময়ে যে বাংলাদেশে সংগ্রামটা গড়ে উঠেছিল—এটা কিন্তু আমাদের নিজের দেশের অভ্যন্তরেরই উদ্যোগ আর চিন্তা ছিল প্রধান। আমাদের সিপিবির যতটুকু ভূমিকা ছিল, এটা যে সোভিয়েতের প্রভাবে করেছে, এটা আমরা বলব না। আমাদের অবস্থানটা তখনো আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী চলতাম। কষ্ট হলেও নিজেদের অর্থ সংগ্রহ নিজেদের করতে হতো। ষাটের দশকে কোনোভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে সোভিয়েত পার্টির সঙ্গে ক্ষীণ একটা যোগাযোগ ছিল বা ও রকম একটা কিছু ছিল। কিন্তু পরে যেটা দেখলাম, স্বাধীনতার পরে প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের পরামর্শ, আলোচনা ও সহযোগিতার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লাম। তবু বলব, পঞ্চাশ বা ষাট দশকের আন্দোলন ও সংগঠন স্বাধীনভাবেই আমরা পরিচালনা করতে পেরেছিলাম। যে জন্য আমি মনে করি—সিপিবি ছোট দল, গোপন দল, ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে, শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের মাধ্যমে, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে একটা বৃহত্তর আন্দোলনকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। এটা খুব একটা ভালো তাত্পর্যপূর্ণ অবস্থান বলে আমাদের কাছে মনে হয়।
টিপু: এখানকার যে সাহিত্য, তার অনেকটাই বামপন্থী চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের কিংবা পশ্চিমবঙ্গের...
মতিউর: এমনিতেই ধরেন, সব দেশেই সাহিত্য, শিল্পকলা আপন আপন ধারায় বিকশিত হয়। আমাদের দেশে বা এই অঞ্চলে—তখন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব বাংলা-পশ্চিম বাংলা মিলিতভাবে বললে—আমাদের এই অঞ্চলের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী বেশ বড় একটা ধারাই ছিল। পাকিস্তান ও ভারত বিভক্তির পরে এ ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা দুর্বল হয়ে যাই। তবে তখনো আগের প্রগতিশীল ধারার একটা প্রভাব ছিল। আবার বাম বা প্রগতিশীল ধারার বাইরেও অনেক সাহিত্যধারা ছিল, সাংস্কৃতিক ধারা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও বড় ছিল। তবে ঢাকায় যে প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন বা তখনকার যে গণনাট্য সংঘ বা প্রগতি লেখক গোষ্ঠী, তার একটা প্রভাব ছিল, এবং তারা সক্রিয় ছিল। তাদের উদ্যোগ ছিল।
আমরা যদি আজকে দেখি, ভারত ভাগের পরে সেই ’৪৮, ৫১, ৫২ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চলে সাহিত্য আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার ছিল। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক আন্দোলন ভালো ছিল। ফরিদপুর, বরিশাল—এসব অঞ্চলে ছিল। উত্তরবঙ্গেও ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখি—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক দেখা, পড়া—গবেষণা-প্রকাশনার সূত্রে গিয়ে দেখি—প্রতিটির পেছনেই, প্রতিটি জায়গাতেই কোনো না কোনো সময় যাঁরা প্রগতিশীল, বামপন্থী রাজনীতি বা চিন্তাভাবনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরাই উদ্যোগগুলো নিয়েছিলেন—সেটা খেলাঘরের মাধ্যমে, সেটা পরে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে বা অন্যান্য নানা পরিচয়ে। ’৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতি সংসদ গঠিত হলো। চট্টগ্রামের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে মাহবুব আলম চৌধুরী, কলিম শরাফী, আরও অনেকের একটা ভূমিকা ছিল। এভাবে কিন্তু ’৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একঝাঁক তরুণ লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁরাই কিন্তু বাংলাদেশে পরে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে—কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, শিল্পী, গান, নাচ পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তাঁদের মধ্য দিয়েই এই নেতৃত্বটা চলেছে। এঁদের দিয়েই ’৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উদ্্যাপন, পরপর ছায়ানট গঠন, ’৬২-র আন্দোলন। তাঁরাই কিন্তু ’৬৯-এ রাস্তায়, তাঁরাই কিন্তু ’৭০/৭১-এ রাজপথে সকল সংগ্রামে, তাঁরাই কিন্তু ’৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই দীর্ঘ সময় তাঁরাই কিন্তু দেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সব কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এটা আমরা বলব—বাংলাদেশের প্রগতিশীল সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন বামপন্থী-প্রগতিশীলেরা। আরও অনেকেই করেছেন। ধরেন, ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক কর্মকা– বা চট্টগ্রামে ’৫১ সালে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ভুল না হলে ’৫৩ সালে কুমিল্লার সাহিত্য সম্মেলন উল্লেখযোগ্য। ’৫৪-র ঢাকার সাহিত্য সম্মেলন—যেখানে কলকাতা থেকে সেরা লেখকেরা অংশ নিয়েছেন। তারপর, ১৯৫৭ সালে ভাসানীর নেতৃত্বে কাগমারীর বিরাট রাজনৈতিক সম্মেলনের পাশাপাশি যে একটা সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, দেশি-বিদেশি শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের অংশ গ্রহণ, এভাবেই তো আন্দোলনটা দাঁড়িয়েছে।
আর ’৬২ সাল থেকে তো আমাদের চোখে দেখা—যত ভালো সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে ওঠে, সবই বামপন্থী প্রগতিশীলদের কাজ। জমায়েত বিরাট, প্রভাব বিরাট। এটা বিশ্বাস করতে এখন কষ্ট হতে পারে—এই সংগঠগুলোর কার্যক্রমে, গানের অনুষ্ঠানে, নাচের অনুষ্ঠানে কোনো সময়ে দেশের গানের বাইরে কোনো গান হতো না, দেশের জন্য কবিতা ছাড়া কোনো কবিতা আবৃত্তি হতো না, দেশের আন্দোলনের সপক্ষ ছাড়া কোনো নৃত্যনাট্য হতো না, কোনো নাটক হতো না। নাটক হতো ‘তাসের দেশ’, ‘রক্তকরবী’— এই সব। বাছাই করা হতো, কোথায় একটা বাণী আছে, যেটা আমাদের সংগ্রামকে সাহায্য করবে। নজরুলের বিদ্রোহী গান, বিদ্রোহী নৃত্যনাট্য, দেশের গানগুলো—এভাবেই কিন্তু ‘আমার সোনার বাংলা’ জনপ্রিয় হয়ে গেল। ছায়ানটের বিরাট ভূমিকা। সংস্কৃতি সংসদের বিরাট ভূমিকা। কামাল লোহানীরা পরে করলেন ক্রান্তি। তারও বিরাট ভূমিকা ছিল। এমনিভাবে—ওয়াহিদুল হক ও সন্জীদা খাতুনের কথা বলা যায়। শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান বা আলতাফ মাহমুদ প্রমুখ অমর থাকবেন। একই সঙ্গে আমরা কোনো দিন ভুলতে পারব না, বামপন্থী চিন্তায় প্রভাবিত মুনীর চৌধুরী ও আনিসুজ্জামানের কথা। স্মরণীয় থাকবেন রণেশ দাশগুপ্ত ও সত্যেন সেন। পরে আরও অনেকেই।
টিপু: রাজনীতি তো ঠিক হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কৃতি ঠিক না হয়...
মতিউর: এটা কিন্তু এখন আওয়ামী লীগের কেউ কেউ বলছেন, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীগুলোও বলছে, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটও বলছে। তার মধ্যে দেখলাম, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলছেন এটা। কী হয়, কী হচ্ছে! সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা হেরে গেছি। এ আর রাহমানকে নিয়ে এসে কত কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তার আগে ‘জয় বাংলা’ উত্সব কনসার্ট হয়েছে, কী হয়েছে এগুলো। গোলাম কুদ্দুছ বলেছেন ভালো, ‘আমাদের কোনো টাকা দিল না, অথচ জয় বাংলা উত্সবে কত টাকা খরচ হয়ে গেল।’ এই তো কালচার এখন!
দেখুন, সংস্কৃতিতে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ধারাটাই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওই ধারাটাকে রাষ্ট্রীয়ভাবেই উত্সাহিত করা হচ্ছে। যদিও রাষ্ট্রীয়ভাবে, কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় ও বিভিন্ন জেলায়, সরকারি সাহায্যে অনেক অনুষ্ঠান হয়। অনেক টাকাও ব্যয় হয়। অনুষ্ঠানগুলো কি মানসম্পন্ন হয়? অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে কি দেশ থাকে? অনুষ্ঠানগুলো কি মানুষের প্রগতিশীল চিন্তাধারার পক্ষে থাকে? এগুলো তো আজকাল সরকারি নেতৃবৃন্দই বলছেন, আমরা তো এখানে ব্যর্থ হয়ে গেছি। যে কথাটা আজকে—বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থায় যা চলছে—যে কথাগুলো আসছে—যদি গণতান্ত্রিক শিক্ষা বা প্রগতিশীল সংস্কৃতির প্রসার না ঘটে, তবে এ দেশের এই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। এটা শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হবে না, এটার পাশাপাশি জোরদার একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন লাগবে। এই জায়গায় আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। সেখানে আমাদের একটা বিরাট পরাজয় ঘটে গেছে। পরাজয়টা আমাদের রাজনীতির ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।
টিপু: আপনার সময়কে কীভাবে দেখেন?
মতিউর: আমার জীবনে, ওই ষাটের দশকে প্রকাশ্যে ছাত্র ইউনিয়ন ও ভেতরে কমিউনিস্ট পার্টি সমান্তরালভাবে কাজ করেছে। দুটোর প্রতি আমার সমান অনুভূতি কাজ করে। ওই ছাত্র আন্দোলনের সময় আমি কখনো মঞ্চে উঠিনি, কখনো কোনো বক্তৃতা দিইনি। কিন্তু আমি সবকিছুতেই থাকতাম। আমি প্রথমে ছাত্র ইউনিয়নের দপ্তর সম্পাদক ছিলাম, পরে কোষাধ্যক্ষ হই। আর আমার মূল কাজ ছিল সংগঠনের ভেতরে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, দলিলপত্র তৈরি, ব্যবস্থাপনা, প্রকাশনাসহ অন্য অনেক কিছুই। আমি বা আমরা দেশের রাজনীতির সবচে গুরুত্বপূর্ণ দশকে কর্মী হিসেবে কাজ করতে পেরেছি, এটা অনেক গৌরবের।
শ্রুতলিখন: মামুন মাহবুব, আলমগীর নিষাদ ও সোহেল তারেক
আরও পড়ুন
- পক্ষপাতমূলক সাংবাদিকতা কখনো সফলভাবে টিকে থাকতে পারে না
- সেনাশাসন আমাদের কাম্য নয়
- দেশের অগ্রগতির জন্য নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি জরুরি
- Vision Statement
- প্রিন্ট আর ডিজিটালের সমন্বয়ের মধ্যেই সংবাদপত্রের ভবিষ্যৎ নিহিত
- বাংলাদেশে সত্যিকারের রেনেসাঁর সময় হলো ষাটের দশক
- জনকল্যাণেও ভালো কাজ করছে গণমাধ্যম
- Predisposed journalism can never grow and sustain