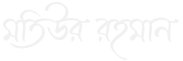রণেশ দাশগুপ্ত: অন্তর্যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চলেছেন
সদাজাগ্রত এক মানুষ ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। বাঙালির ছয় দশকের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিশীল সংস্কৃতির ভান্ডার থেকে আহরণ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ শিল্প-সাহিত্যের নির্যাসগুলো। শুদ্ধ রুচি গড়ে তুলেছেন অসংখ্য পাঠকের। সেতুবন্ধ তৈরি করেছেন বিশ্বের সঙ্গে বাংলার। রণেশ দাশগুপ্ত সবাইকে ছেড়ে গেলেন ১৯৯৭ সালের ৪ নভেম্বর।
মনে পড়ে, ১৯৭০ সালের কোনো এক সময়ে, লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় লুই আরাগঁর ‘অঁরি মাতিস: আ নভেল’ নামক বিশাল গ্রন্থের একটা মনোগ্রাহী আলোচনা বের হয়েছিল। ‘সংবাদ’ অফিসে তখন সেই পত্রিকাটি নিয়মিত আসত। এক সন্ধ্যায় সেটা পড়ে রণেশদা আমাকে দিয়েছিলেন। সেই থেকে ‘অঁরি মাতিস: আ নভেল’ খুঁজেছি। অনেক বছর পেরিয়ে ১৯৯৭ সালে লন্ডনে বইটি পেয়ে যাওয়ার পর রণেশদার কথাই প্রথম মনে পড়েছে। দুই খণ্ডের বিশাল বইটি কিনেছিলাম ১৫০ পাউন্ড দিয়ে।
এই একটা গ্রন্থ শুধু নয়, এই যে লুই আরাগঁ বা পল এল্যুয়ারের কবিতা আর সংগ্রামের কথা, পাবলো নেরুদার কবিতার প্রথম বই টুয়েনটি লাভ পয়েমস অ্যান্ড আ সং অব ডেসপেয়ার, সেজার ভালেখোর সেই কবিতা ‘এক বৃহস্পতিবার বৃষ্টির দিনে আমার মৃত্যু হবে’, শেক্সপিয়ারের ‘রোমিও-জুলিয়েট’-এর নতুন কোনো ব্যাখ্যা, মার্কিন দেশে চার্লি চ্যাপলিনের জীবনের দুঃখজনক অধ্যায়, স্পেনের গৃহযুদ্ধে নিহত লেখক ক্রিস্টোফার কডওয়েল আর র্যালফ ফক্সের সংগ্রাম বা ডলোরেস ইবারুরির লা পাশিওনারিয়ার জীবনকথা, জ্যাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদ নিয়ে নতুন কোনো চিন্তা, সের্গেই এসেনিনের সঙ্গে ইসাডোরা ডানকানের অমর প্রেম, গিওর্গি লুকাচের সাহিত্যবিচারের পদ্ধতি, সের্গেই আইজেনস্টাইনের ব্যাটেলশিপ পটেমকিন, ইতালির আন্তোনিও গ্রামসির চিন্তা কেন আমাদের জন্যও জরুরি, লাতিন আমেরিকার বিপ্লবের সম্ভাবনা, কালো আফ্রিকার সাহিত্যের নতুন পথ অন্বেষণ—আরও কত কিছু সম্পর্কে আমরা রণেশদার কাছ থেকে শুনেছি। তার হিসাব কষতে বসে দেখি, এখন অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছি। আমরা তাঁর কাছেই থিওডোর ড্রেইজার আর জ্যাক লন্ডনের গল্প-উপন্যাসের কথা প্রথম শুনেছি। স্পার্টাকাস থেকে শুরু করে হাওয়ার্ড ফাস্টের সব গ্রন্থ, যেকোনো সাম্প্রতিক গ্রন্থ পেলেই তিনি পড়েছেন। একদিকে রমাঁ রোলাঁ, জর্জ বার্নার্ড শ থেকে শুরু করে বেট্রল্ট ব্রেখট, স্যামুয়েল বেকেট, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, শরত্চন্দ্র বসু, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি জীবনানন্দ দাশকে কতভাবেই না দেখেছেন রণেশদা। সূক্ষ্ম অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে কত মণিমানিক্য তিনি বের করে এনেছেন তাঁদের সব লেখা থেকে। আর সত্যেন সেন, শহীদুল্লা কায়সার, জহির রায়হান, শামসুর রাহমানের জীবন ও কবিতায়, লেখায় বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বপ্নকে খুঁজে পেয়েছেন। মুনীর চৌধুরীকে তিনি ‘কমিউনিস্ট বিপ্লবী প্রগতিবাদী’ লেখক হিসেবেই দেখেছেন সব সময়। আসলে, বহু আলোচনায় তিনি বারবারই তাঁর প্রিয় মুনীরের কথা বলেছেন। শওকত ওসমানকে উচ্চ মূল্যায়ন করতেন। সেলিনা হোসেনের নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি খুব পছন্দ করেছিলেন। দীর্ঘদিন কলকাতায় থেকেও ঢাকার নতুন লেখক-কবিদের লেখার খোঁজখবর রাখতেন নিয়মিত। আধুনিক চিত্রকলা, সিনেমার নতুন নতুন নিরীক্ষা, সব ধরনের নাটক আর গানেই প্রবল আগ্রহ ছিল রণেশদার।
রণেশদা তো কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস আর লেনিন থেকে শুরু করে ইতালির পালমিরো তোগলিয়াত্তি, ফরাসি দেশের রজার গারোদি বা অস্ট্রিয়ার আর্নেস্ট ফিশার, বিপ্লবী চে গুয়েভারা বা অন্য আরও যেকোনো তাত্ত্বিকের যা কিছু পেয়েছেন সব পড়েছেন, আত্মস্থ করেছেন। এমনকি মিখাইল গরবাচভের পেরেস্ত্রাইকার সময়েও তিনি আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন (১ জানুয়ারি ১৯৮৮), ‘ওরা যে গ্লাস্তনস্ত করতে গিয়ে “বড় কলেজের” উদারতা খাটিয়ে লড়াইয়ের খনি খুঁড়ে খুঁড়ে দারুণ দারুণ জিনিস বের করছে, এটা আমাদের খুবই কাজে লাগবে।’
আসলে বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সেটা যত ক্ষুদ্র ও বৃহৎই হোক না কেন, তিনি তা থেকে আকাড়া মালমসলা বের করে এনেছেন। তাঁর চিন্তাজগেক সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে ঝালাই করে নিয়েছেন, হৃদয়কে উত্তপ্ত করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, সেসব হিরে-জহরত সবার জন্য আবার উদার হস্তে ছড়িয়েও দিয়েছেন। আমার মনে হয় না, কখনো কেউ তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু না শুনে বা না জেনে ফিরে এসেছেন বা নতুন কোনো পথের সন্ধান না পেয়ে ফিরে গেছেন। সে জন্যই তিনি সব দলমত ও চিন্তার মানুষের খুব কাছের ছিলেন, পরম নিকটাত্মীয় হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আজীবন বিপ্লবী মার্ক্সবাদী ছিলেন, কমিউনিস্ট ছিলেন ঠিকই, কিন্তু কোনো সময়ই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে কখনো কোনো নিয়মে বাঁধতে পারেনি। ষাট আর সত্তরের দশকে আনুষ্ঠানিক যোগাযোগও কমে গিয়েছিল। সে জন্য পার্টির কোনো কংগ্রেসে, এমনকি ১৯৭৩ সালে সবচেয়ে খোলামেলা সময়েও তাঁকে দেখা যায়নি কংগ্রেসের কোনো অনুষ্ঠানে। তবে তিনি সব সময়ই দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক ও প্রগতির সংগ্রামে শরিক থেকেছেন তাঁর মতো করেই। দূরে গিয়ে নয়, পাশাপাশি থেকেই কাজ করে গেছেন নিরন্তর। এমনভাবেই তিনি কয়েক প্রজন্মের কবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, বামপন্থী শুধু নয়, নানা মতের, নানা চিন্তার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর জন্য এক অনুপ্রেরণার বড় আধার হয়ে উঠেছিলেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মও অনুপ্রাণিত হবে তাঁর বিশাল কর্মজীবন থেকে। রণেশদা আবার প্রমাণ করলেন, যৌথ নেতৃত্ব বা সংগঠনের চেয়েও একজন ব্যক্তি কত বড় হয়ে উঠতে পারেন এবং একজন মানুষ কতটা দিতে পারেন।
রণেশদার সঙ্গে কবে কখন পরিচয় হয়েছিল, তা আর মনে নেই। আমি তো সেই ১৯৫৮ সাল থেকেই ‘সংবাদ’ অফিসে যাওয়া-আসা করি। ওই সময় আমরা থাকতাম বংশাল রোডে। মনে পড়ে, ১৯৫৪ সাল থেকেই খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে গিয়ে দেয়ালে সাঁটানো ‘সংবাদ’ পড়তাম। ১৯৫৯ সালে শহীদ সাবের অসুস্থ হয়ে পড়লে রণেশদা ‘সংবাদ’-এ যোগ দেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে। হতে পারে ওই সময়েই পরিচয়, অথবা ১৯৬১ সালে কলেজপড়ুয়া হিসেবে ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যখন জড়িয়ে পড়ি তখন থেকে। তবে এটা নিশ্চিত বলতে পারি, ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের সময় রণেশদা গ্রেপ্তার হয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে আসার পর থেকেই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। যেকোনো কাজে বা অপ্রয়োজনে সকাল, দুপুর, বিকেল বা সন্ধ্যায়, যখন-তখন ঢুকে পড়েছি সংবাদ-এ। উদ্দেশ্য একটাই, রণেশদার সঙ্গে সময় কাটানো। তখন আবার একটু-আধটু লেখারও চেষ্টা করছি, বিশেষ করে কবিতা। তাঁরও উত্সাহ ছিল তাতে। আর ‘সংবাদ’-এ প্রথম একসঙ্গে তিনটি কবিতা বের হয় সাহিত্য সাময়িকীতে। সন-তারিখ কিছু মনে নেই, হতে পারে ১৯৬৪ সালের কোনো এক রোববারের সাহিত্য সাময়িকীর পৃষ্ঠায়। রণেশদা তখন ‘সংবাদ’-এর সাহিত্য সম্পাদকও। তিনিই বাছাই করে কবিতাগুলো ছেপেছিলেন। পরে আমার আরও গদ্য-পদ্য ছাপেন তিনি।
রণেশদা কত দিন এসেছেন আমাদের বংশালের বাসায়, বিশেষ করে ঈদের নেমন্তন্নে বা অন্য কোনো সময়ে! আম্মা সব সময় সে কথা স্মরণ করেছেন। একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন আম্মা, দেখা করেছিলেন রণেশদার সঙ্গে। সেদিনও আম্মার রান্নার স্বাদের কথা রণেশদা বলেছিলেন রমেন মিত্র আর ইলা মিত্রকে।
মনে পড়ে, সেই ষাটের দশকে কত ছোট কাজ, কত আবদার, কত দাবি নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছি। কোনো রকম আপত্তি না জানিয়ে আমাদের সমস্ত অত্যাচার তিনি সদাহাস্যমুখে মেনে নিয়েছেন। ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সম্মেলন থেকে শুরু করে থানা সম্মেলনে পর্যন্ত অতিথি হয়ে গেছেন। ছায়ানট, উদীচী, সৃজনী লেখক-শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি সংসদের আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথি হয়েছেন। এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে, সাংবাদিক আহমেদুর রহমানের স্মরণে উদয়ন স্কুলে অনুষ্ঠিত ছায়ানটের আলোচনায় ‘শিল্পীর স্বাধীনতা ও সততা’ প্রবন্ধটি কী বলিষ্ঠ ভাষা আর উচ্চারণে পাঠ করেছিলেন! সেই ষাটের দশকে একুশে ফেব্রুয়ারি বা অন্য নানা দিবস উপলক্ষে কত লেখা লিখেছেন, সে হিসাব কেউ বের করতে পারবেন না। এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য, ষাটের দশকে তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় প্রতিটি একুশে সংকলনের উজ্জ্বল নামগুলো দিয়েছিলেন রণেশদা। সেগুলোর মধ্যে আছে ‘সূর্যজ্বালা’, ‘বিক্ষোভ’ (প্রেস থেকে পুলিশ ছাপানো সব ফর্মা তুলে নিয়ে গিয়েছিল), ‘ঝড়ের খেয়া’, ‘অরণি’, ‘নিনাদ’ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটা সময়ে জমিল শরাফী নামে কিছু বিশেষ লেখাও লিখেছিলেন তিনি।
রণেশদার বই পড়ার একটা বিশেষ ধরন ছিল। বই পড়তে পড়তে তিনি লাইনের পাশে টিকচিহ্ন দিতেন। কখনো লাইনের নিচেও দাগ দিতেন। কখনো কখনো পাশে নানা মন্তব্য লিখে রাখতেন। ষাট বা সত্তরের দশকে আমার সংগ্রহের অনেক বইয়ের তিনি ছিলেন প্রথম পাঠক। এগুলোর মধ্যে এখনো বেশ কয়েকটি আমার কাছে আছে। সেগুলো আমার কাছে পরমাত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে শুধু রণেশদার স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে বলে। আমার দুঃখ, সে রকম অনেক বই এখন আর আমার কাছে নেই। যেগুলো এখনো রয়েছে, সেগুলো হলো রোল্যান্ড পেনরোজের পিকাসো: হিজ লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক, হেলেন পারমেলিনের পিকাসো সেইজ, ইলিয়া এরনবুর্গের পিপল অ্যান্ড লাইফ, কবি সালভাতোরে কোয়াসিমোদোর সিলেক্টেড পয়েমস, ব্রায়ান সায়মন সম্পাদিত দ্য চ্যালেঞ্জ অব মার্ক্সিজম এবং বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ রজনী পাম দত্তের দি ইন্টারন্যাশনাল। বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখলে বোঝা যায়, কী যত্নে, কী গভীর অন্বেষণে সেগুলো তিনি পড়েছেন!
ষাট ও সত্তরের দশকে রণেশদা তাঁতীবাজারে হরিলাল বসাকের যে বিখ্যাত ঘরে থাকতেন—তিনিই বলেছিলেন, সন্তোষদা নাকি রসিকতা করে বলতেন, ‘যে ঘর থেকে পা বেরিয়ে যেত’—সেখানে বহুবার গিয়েছি। আসলে মাথা নিচু করে কোনো রকমে ঘরে ঢুকেই মাটিতে তোশক-পাতা বিছানায় বসে পড়তে হতো, দুই পা সোজা করে বসা যেত না। আর ওই বিছানার চারপাশে বই, খাতা, কত কাগজ, পত্রিকা ইত্যাদি। এর মধ্যেই বিশ্রাম, ঘুম আর লেখাপড়া; কী বিস্ময়! সেখানে থেকেই কত কিছু না তিনি লিখেছেন, যা আজও আমাদের পথ আলোকিত করে চলেছে, সুন্দরের স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করছে।
ষাটের দশকে ওই ঘরে বসেই তিনি মূল উর্দু থেকে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতাগুলো অনুবাদ করেছিলেন। আমরা জানি, তিনি কারাবাসকালে উর্দু শিখেছিলেন। ছাপার আগে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি, কবিতার বাঁধানো খাতাটি বহুদিন আমার কাছে ছিল। প্রকাশ ভবন বইটি প্রকাশ করেছিল পরে। মনে পড়ে, ১৯৬৯ সালে বইটির দুই রঙের প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরীর কাছ থেকে করিয়ে এনে তাঁতীবাজারের একটা প্রেস থেকে ছেপেও দিয়েছিলাম।
১৯৭০ সালে জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর পক্ষ থেকে অধ্যাপক ও লেখক আবদুল হালিম রণেশ দাশগুপ্তের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রবন্ধগুলোকে একত্র করে আলো দিয়ে আলো জ্বালা গ্রন্থ বের করেছিলেন। মনে পড়ে, সে সময় বিভিন্নজনের কাছে গিয়ে পুরোনো কাগজ, পত্রিকা খুঁজে বের করে অনেক লেখা সংগ্রহ করেছিলাম। এ কথা রণেশদার ঠিক স্মরণে ছিল। সে কথা মনে করে তিনি এক চিঠিতে আমাকে (১৯ জুলাই ১৯৮৬) লিখেছিলেন, ‘...মতিউর, মনে পড়ে যায়, বিশেষ করে তোমার ও তোমার তখনকার সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের সেই ভালোবাসার কথা, যার মধ্যে আলো দিয়ে আলো জ্বালা আর ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা একত্র হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল।’ তারও আগে, ওই ষাটের দশকেই, ১৯৬৬ সালে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে বইটি প্রথম বের করেছিল মুক্তধারা প্রকাশনী। প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পী আবদুল মুক্তাদির। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী সাহিত্যপত্রিকা ‘সমকাল’-এ সমালোচনা লিখেছিলেন বইটির।
ওই ষাটের দশকের শেষের দিকের একটা ঘটনার জন্য, দুর্ঘটনাই বলব, আজও মন বড় বিষণ্ন হয়ে যায়। ষাটের দশকের মাঝামাঝি কোনো এক সময়ে মোহাম্মদ শাহজাহান সম্পাদিত একটা লিটল ম্যাগাজিনে রণেশদার একটা লেখা ছিল ‘অব্যাহত কবিতার জন্য’, কবিতায় প্রকাশ্য ও স্বগতোক্তির বিষয় নিয়ে। ফরাসি দুই কবি পল এল্যুয়ার ও লুই আরাগঁ এবং বাংলার সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে আলোচনা ছিল ওই নিবন্ধে। সেটা পরে আলো দিয়ে আলো জ্বালা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। নিবন্ধটি আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। বহুদিন রণেশদাকে অনুরোধ করেছিলাম, ওই বিষয়টি নিয়ে বড় একটা লেখা তৈরি করতে, যার সঙ্গে অনেক কবিতার অনুবাদ থাকবে। পরে সবটা মিলিয়ে একত্রে বই করা যাবে। সে অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। তিনি অনেক খেটেখুটে বইটির একটা করে পরিচ্ছেদ লিখতেন আর আমাকে দিয়ে দিতেন। এভাবে অব্যাহত কবিতার জন্য বইটি লেখা শেষ করেছিলেন। তারপর ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, স্প্যানিশ, ইতালি, আফ্রিকান কবিতার অনুবাদ করেছিলেন বইটির জন্য। সেগুলোর সংখ্যা হবে ১০০-এর মতো, হতে পারে তার চেয়েও বেশি। সব মিলিয়ে পুরো পাণ্ডুলিপি আমার কাছে ছিল বেশ কিছুদিন। পরে ১৯৭০ সালের কোনো এক সময়ে রণেশদা বললেন, একজন প্রকাশক আগ্রহী হয়েছেন বইটি বের করতে। পুরো পাণ্ডুলিপি প্রকাশককে দিয়ে এলেন রণেশদা। তারপর তো সেই একাত্তর চলে এল, শুরু হয়ে গেল মুক্তিসংগ্রাম। আমরা আর কিছু জানতে পারিনি। যুদ্ধ শেষে রণেশদা ফিরে এসে খোঁজ করে পাণ্ডুলিপিটি আর উদ্ধার করতে পারেননি। সে দুঃখ আজও আমার রয়ে গেছে। প্রায়ই মনে হয়, একটা মহৎ সৃষ্টি থেকে আমরা সবাই বঞ্চিত হয়েছি। এ রকম একটা সৃষ্টিশীল গ্রন্থ রচনা আর কারও পক্ষে কি সম্ভব হবে?
এ রকমই ঘটনা ঘটেছিল আরেকটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে। সেদিন সকালে ঢাকায় বইয়ের পাণ্ডুলিপি একাত্তরে হারিয়ে গেলেও খান ব্রাদার্স প্রকাশনা সংস্থা অনেক দিন পর সেটি পেয়ে ১৯৮৬ সালে প্রকাশ করেছিল।
আসলে রণেশদা লিখে গেছেন নিরন্তর—মনের প্রবল তাগিদ নিয়ে, বন্ধুদের চাপে বা কখনো বিশেষ কিছু বলার জন্য। বই করতে হবে, সে জন্য প্রকাশকের কাছে যেতে হবে, এ রকম কোনো ভাবনা বা ইচ্ছে তাঁর ছিল না কোনো সময়। তবে বই প্রকাশিত হলে তিনি খুশি হতেন। এখানে স্মরণ করব, আশি আর নব্বইয়ের দশকে আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, রহমানের মা ও অন্যান্য, সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের কবিতা ইত্যাদি কিছু নতুন ও পূর্বে প্রকাশিত বইয়ের পুনর্মুদ্রণ করে মফিদুল হক আমাদের সবাইকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আর মালেকা বেগমের স্বল্পস্থায়ী প্রকাশনা সংস্থা জ্ঞান প্রকাশনী থেকে ১৯৮৯ সালে বের হয়েছিল মুক্তিধারা নামে তাঁর একটা প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ।
সেই প্রায় একইভাবে তাঁতীবাজারের বাসার মতোই, রণেশদা থাকতেন কলকাতার প্রায় পরিত্যক্ত লেনিন স্কুলের একটা ঘরে—চৌকির বিছানার প্রায় একদিকে পুরোটাই বই, ম্যাগাজিন, কাগজ কত কিছু। কিছু বই থাকত টুলের ওপর। এসব কিছু থেকেই কত অমূল্য রত্নভান্ডার বের করে দেখাতেন আমাদের, পড়তে দিতেন। ওই বিছানাতেই কোনো রকমে দুই পা সোজা করে বিশ্রাম আর ঘুম। আবার তারই ওপর পা ঝুলিয়ে বসে লেখাপড়া। আর সকালে সেই ঘর থেকে বের হয়ে যেখানে একচিলতে সূর্যের আলো আসত, সেখানে টুলে বসে আবার লেখাপড়া।
সেই দিনগুলোতেও রণেশদা অসংখ্য লেখা লিখেছেন কলকাতা ও ঢাকার পত্রপত্রিকা, সাময়িকী বা লিটল ম্যাগাজিনে। সেসবের সংখ্যা কত, সে হিসাব বের করা খুব কঠিন। তবে কলকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কালান্তর, পরিচয়, সাহিত্যচিন্তা, মূল্যায়ন, ঐকতান, অর্কিড, লেখক সমাবেশ প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক লিখেছেন। এর বাইরেও লিখেছেন তিনি। ভারতকথা নামে অধুনালুপ্ত একটা দৈনিকে ‘বাংলাদেশ আলেখ্য’ বলে কলাম লিখেছেন বেশ কিছুদিন। আর এসব লেখার অধিকাংশেরই বিষয় ছিল বাংলাদেশের কোনো ঘটনা, ঐতিহাসিক দিবস, কোনো বই বা ব্যক্তিকে নিয়ে। ঢাকায় সংবাদ, ‘ভোরের কাগজ’, সাপ্তাহিক ‘একতা’, মাসিক মুক্তির দিগন্তসহ আরও কিছু কাগজে কলকাতা থেকে পাঠানো রণেশদার লেখা ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশের যিনি যখন অনুরোধ করেছেন, তিনি লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি কারও অনুরোধ রাখেননি, এমনটি কখনো শুনিনি। কবি শামসুর রাহমানের বয়স ষাট বছর পূর্ণ হলে মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার জন্য একটা লেখা এনে দিয়েছিলাম। লেখাটির শিরোনাম ছিল ‘শামসুর রাহমানকে অভিনন্দন: এত ভালোবাসা ঘৃণা রক্তধারা প্রত্যয় বিদ্রোহ প্রজ্ঞা সহজিয়া সাধনা’।
রণেশদা সবার সব চিঠির জবাব দিয়েছেন। কতজনকে যে কত চিঠি লিখেছেন! যখনই কেউ বাংলাদেশ থেকে গেছেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিচিত সবার খোঁজখবর নিয়েছেন। কলকাতা থেকে আমাকে লেখা প্রায় সব চিঠি শেষ করেছেন এভাবে, ‘মালেকা, সাশা, তাতা, তাতার পুত্র ও তার বর এবং তোমাদের দুই আম্মাসহ সকলকে আমাদের শুভেচ্ছা ভালোবাসা আশীর্বাদ দিও।’ তিনি কখনো বলতেন না ‘আমার’, বলতেন ‘আমাদের’। লিখলেও সেভাবেই। আসলেই তো, রণেশদার ‘আমি’ বলে তো কিছু ছিল না।
পঁচাত্তরের অক্টোবরে রণেশদা ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অনেক দিন সরাসরি যোগাযোগ হয়নি। আমাদের জন্য সে সময়টা ছিল বলা যায় এক ঝোড়ো সময়—নানা উত্থান-পতনের ঘটনা ঘটেছে একের পর এক। এভাবেই দেখতে দেখতে এক দশক সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।
১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ কলকাতায় যাই চিকিত্সার জন্য। দেখা হয় রণেশদার সঙ্গে। সেই অন্তরঙ্গতা, আর কত গল্প, কত বইয়ের কথা। এর পরের প্রায় ছয় বছর তো চিকিত্সা এবং অন্যান্য উপলক্ষে কলকাতায় অনেকবার গিয়েছি। তখন সেখানেও রণেশদাই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। কলকাতায় গেলে দুবেলাই তাঁর ডেরায় গিয়েছি। প্রতিবারই তাঁর সেই হাসিমুখ, সাদর সম্ভাষণ আর অফুরন্ত গল্প। ঢাকায় ফিরে এসেই পেয়েছি চিঠি আর লেখা। কোনো সময় হাতে হাতে, কখনো আবার ডাকে।
একদিন রণেশদা তাঁর একটা ফটো অ্যালবাম দেখালেন। সে অ্যালবামে তিনি পত্রিকা-ম্যাগাজিন থেকে কেটে কেটে কিছু ছবি রেখেছেন। তাঁর প্রিয় মানুষ, যাঁদের তিনি শ্রদ্ধা করেন, যাঁদের লেখা তিনি ভালোবাসেন, তাঁদের ছবি রেখেছেন অ্যালবামে। একবার রণেশদার প্রিয় অ্যালবামটি চেয়ে ফেললাম। পরেরবার যেতেই সেটা তিনি আমাকে দিয়ে দিলেন। আজও সেটা যত্নে আছে আমার কাছে। অ্যালবামটি থেকে আমি রণেশদার ঘনিষ্ঠ ছোঁয়া পাই। কাদের ছবি আছে তাতে? শুরুতেই চিলির পাবলো নেরুদা, তারপর বুলগেরীয় নেতা গিওর্গি দিমিত্রভ ও রুশ লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি একসঙ্গে, জার্মান নেত্রী ক্লারা জেৎকিন আর ফরাসি লেখক আঁরি বারবুস, উর্দু সাহিত্যের খাজা আহমদ আব্বাস, কৃষান চন্দর, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, ইতালির আন্তোনিও গ্রামসি, পর্তুগালের কমিউনিস্ট নেতা আলভারো কুনহালের ড্রয়িং, তুর্কি কবি নাজিম হিকমত, হাঙ্গেরীয় চিন্তাবিদ গিওর্গি লুকাচ, কিউবার বিপ্লবী ও কবি হোসে মার্তি, গ্রিক কবি ইয়ান্নিস রিতসস এবং মিকিস থিওডারাকিস হাভানায় পরিচালনা করছেন পাবলো নেরুদার কবিতা ‘কান্টো জেনারেল’-এর ওপর ভিত্তি করে বৃন্দগান, বৃন্দবাদ্য ইত্যাদি।
বর্ণাঢ্য আর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরা জীবন ছিল রণেশদার, কমরেড রণেশ দাশগুপ্তের। আশির দশকের বিভিন্ন সময়ে কলকাতায় রণেশদার দীর্ঘ চারটি সাক্ষাত্কার নিয়েছিলাম। বহু কথা, বহু আলোচনা হয়েছে সেগুলোতে তাঁর সঙ্গে। তাঁর জন্ম ১৯১২ সালে। বাঁকুড়া, বরিশাল আর রাচিতে পড়াশোনা করেছেন, থেকেছেন। ছোটবেলা থেকেই গান করা, ছবি আঁকায় আগ্রহ ছিল। অষ্টম শ্রেণীতেই লেভ তলস্তয়ের আনা কারেনিনা পড়ে ফেলেছিলেন রণেশদা।
রণেশদা তাঁর মা ইন্দুপ্রভা দেবীর (বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল) কাছ থেকে গল্প শুনতেন খেতে খেতে। তিনি বলেছেন, ‘এভাবে ডাবল সার্ভিস পেতাম। মা ভীষণ পড়ুয়া ছিলেন, খুব শান্ত ছিলেন।’ মায়ের খুব সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি। সে জন্য রণেশদা বলেছিলেন, ‘এখন মায়ের জন্য খুব দুঃখ পাই। আমি জেলে। বোনদের নিয়ে মা কলকাতায় চলে যান অত্যন্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে। দারুণ কষ্টে মারা গেলেন।’ আরেকবার রণেশদা বলেছিলেন, ‘বাবা রিটায়ার করে ঢাকায় চলে আসেন। আমার কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাননি। আমার ওপর নির্ভর করে মারা যেতে পারেননি। অনেক সময় মনে হয় এ রকম সরে আসাটা কেমন হলো?’ প্রবাসে কলকাতায় রণেশদা ঘুরেফিরে বোনদের বাসায় থেকেছেন, খেয়েছেন। অসুস্থ হয়ে চিকিত্সাধীন অবস্থায় থেকেছেন। ভাইবোনের ছেলেমেয়েরা আদরযত্ন করেছেন। রণেশদার সঙ্গে কলকাতায় তাঁর তিন বোনের বাসায় গিয়েছি, খেয়েছি, যত্ন পেয়েছি। এভাবেই হয়তো শেষ জীবনে ভাইবোনের কাছাকাছি থেকে রণেশদা পুরোনো দুঃখ-বেদনাকে কিছুটা ভুলে থাকতে চেয়েছেন।
১৯৩৫ সালে সরাসরি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন রণেশদা। সোনার বাংলা পত্রিকায় চাকরি নেন। বেতন পেতেন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা। ১৯৩৮ সালে বাবা মারা যাওয়ার পর ইনস্যুরেন্স কোম্পানির চাকরিতে যান। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ওই চাকরিতেই ছিলেন। বেতন ৫০ থেকে ২০০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের মার্চে প্রথম জেলে যান। তিন দিন পর ছাড়া পান ছাত্রদের সঙ্গে। ’৪৮ সালের জুন মাসে গ্রেপ্তার হয়ে আবার ছাড়া পান ’৫৫ সালের অক্টোবরে। ওই সময়ে একবার আটান্ন দিনের অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। সেবার ছিলেন ঢাকা, যশোর আর রাজশাহী জেলে।
জেল থেকে বের হয়ে রণেশদা কিছুদিন সাপ্তাহিক ‘ইত্তেফাক’-এ কাজ করেছেন। তারপর প্রায় দুই বছর ফ্রি-ল্যান্স হিসেবে ছিলেন। ১৯৫৮ সালে পুরান ঢাকা থেকে পৌরসভার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার হন। মুক্তি পান ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বরে। পুনরায় গ্রেপ্তার হন ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে। বের হয়ে আসেন ১৯৬৮ সালে। এই জেলে আসা-যাওয়ার সময়গুলোয় তাঁর ভান্ডারে সঞ্চয় হয়েছিল বহুমুখী অভিজ্ঞতা। বহুজনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, অনেক পড়াশোনা করেছেন। আবার জেলের কথা বলতে গিয়ে খাপড়া ওয়ার্ডের শহীদ আনোয়ার হোসেনের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি বলেছেন নগেন সরকারের কথা, মুনীর চৌধুরী, সরদার ফজলুল করিম, শহীদুল্লা কায়সার এবং আরও অনেকের কথা। তাঁদের সাহসী আর সুন্দর জীবনকাহিনি শুনিয়েছেন। লিখেছেনও অনেকের কথা।
এই জেলে যাওয়া আর বাইরে আসার মধ্যে ১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত রণেশদা ‘সংবাদ’-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। শুধু ওই দায়িত্বই নয়, তিনি আরও অনেক কিছুই করেছেন। সংবাদকে কেন্দ্র করে অন্যান্য প্রসঙ্গে তিনি কতবার কত বিষয়ে জহুর হোসেন চৌধুরী, সৈয়দ নূরুদ্দিন, শহীদুল্লা কায়সার, আহমদুল কবিরের নানা গুণ আর সাহসের কথা বলেছেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা লেগে গেলে রণেশদাকে আহমদুল কবির তাঁতীবাজারের বাসা থেকে নিজ বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন।
একাত্তরের এপ্রিলের কোনো এক সময়ে, হয়তো মাঝামাঝিতে, আমি ঢাকায় এসে রণেশদাকে মাদারটেক থেকে নৌকায় করে বেরাইদে নিয়ে যাই। সেখান থেকে হেঁটে, তারপর নৌকায়, তারপর আবার হেঁটে নরসিংদী থেকে রায়পুরায় পৌঁছে দিয়েছিলাম কমিউনিস্ট পার্টির হেফাজতে। সেখানে নবীন-প্রবীণ অনেকেই জমায়েত হয়েছিলেন। সেখান থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে কীভাবে কোন পথে কলকাতায় গিয়েছিলেন তিনি, তা আর এখন মনে নেই। তবে ২৫ মার্চের গণহত্যার পর অধ্যাপক আবদুল হালিম রণেশদাকে ঢাকার গোপীবাগে এক বাসায় লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর ভাই আবদুর রহীমই রণেশদাকে সঙ্গে করে এনে আমার কাছে মাদারটেকে নদীর ঘাটে পৌঁছে দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর আহমদুল কবির আবার নিজে গিয়ে রণেশদাকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলেন। এখানে একটা কথা বলা যায়, রণেশদা যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন, যাঁদের সঙ্গে মিশেছেন, সব সময়ই তাঁদের ভালো সুন্দর দিকগুলোকে উচ্চ মূল্য দিয়েছেন, সেগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছেন। কোনো দিন কারও সম্পর্কে কোনো কটূক্তি বা নিন্দা শুনিনি তাঁর কাছ থেকে। এ রকমই এক অনুকরণযোগ্য বিরল মানবগুণের অধিকারী ছিলেন তিনি।
‘সংবাদ’-এ রণেশদা সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় লিখেছেন। ‘মনে মনে’ শিরোনামে ব্যক্তিগত একটা কলাম লিখেছেন মধুব্রত নাম দিয়ে। কলামটি একসময় লিখতেন সৈয়দ নূরুদ্দিন। সে জন্য ওই লেখাগুলো নিয়ে যে বই সেদিন সকালে ঢাকায় বেরোয়, সেটা সৈয়দ নূরুদ্দিনকে উত্সর্গ করেন। এসবের বাইরে তিনি স্বনামে অনেক লিখেছেন, বিশেষভাবে লিখেছেন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রয়োজনে। পাঠককে, দেশের মানুষকে পথ দেখাতে আর অনুপ্রাণিত করতেও লিখেছেন বারবার। ষাটের দশকের শুরুর দিকে আলজেরিয়ায় কমিউনিস্ট নেতা হেনরি অ্যালেগের নির্যাতিত জীবনের কাহিনি জিজ্ঞাসা অনুবাদ করে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন সংবাদ-এ। সে সময় সেটা বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। পরে সেটা বই হয়ে বেরিয়েছিল। একইভাবে ষাটের দশকের শেষ ভাগে চে গুয়েভারা এবং বলিভিয়ায় বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টার পর লাতিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম নিয়ে দীর্ঘ লেখা লিখেছিলেন। পরে সেটা ছোট একটা বই হিসেবে বের হয়েছিল। মনে পড়ে, ১৯৬৮ সালে যখন প্যারিসে রাস্তায় রাস্তায় লড়াই চলছিল, তার পটভূমি হিসেবে ফরাসি বিপ্লব থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ে তথ্যবহুল দীর্ঘ ধারাবাহিক রচনা লিখেছিলেন রণেশদা।
এসবের পাশাপাশি কবিতা অনুবাদ, বই নিয়ে আলোচনা, কত কিছুই না করেছেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, স্বাধীনতার পর রণেশদা মাসিক গণসাহিত্য পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে সময় একটা নাটক লিখেছিলেন, ফেরী আসছে। রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত ‘থিয়েটার’-এ সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। নাটকটি রেডিও-টিভিতে অভিনীত হয়েছিল। এর অনেক আগে, সেই ১৯৪৩ সালে লেখা রণেশদার দুটি নাটক অভিনীত হয়েছিল—জানালা আর আমন ধান। এর পরের বছর আরেকটি নাটক লিখেছিলেন, বড় বাড়ি। এসব তথ্য পেয়েছি রণেশদার কাছ থেকেই।
১৯৮৮ সালের নভেম্বরে দেওয়া এক সাক্ষাত্কারে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম তাঁর প্রিয় বই, লেখক, শিল্পী ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে। সেখান থেকেও রণেশদার জীবনের বহুমুখী ভালোবাসা আর ভাবনাগুলোর পরিচয় আমরা পেয়ে যাই।
প্রথমে আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম তাঁর প্রিয় বই কী? রণেশদার দ্রুত উত্তর ছিল, ‘আইরিশ নাট্যকার সিয়ান ও কেসির নাটক দ্য প্লাউ অ্যান্ড দ্য স্টার এবং স্টারস টার্ন রেড।’ তার পরই বললেন, ‘এই বই আমি মুনীরকে পড়তে দিয়েছিলাম। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট লেখক ক্রিস্টোফার কডওয়েলের ইলিউশন অ্যান্ড রিয়্যালিটি বইটিও প্রিয় ছিল।’ তারপর তিনি বলেন, ‘পনেরো-ষোলো বছর বয়সে তখন রাঁচিতে থাকি, পকেটে থাকত কবি নজরুলের অগ্নিবীণা।’ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর? রণেশদার উত্তর, ‘রবিঠাকুর শেষ পর্যন্ত অফুরন্ত ব্যাপার। তাঁকে ছাড়া চলবে না। কবি সাজ্জাদ জহীর ঠিকই বলেছিলেন, রবিঠাকুর এখনো আমাদের “মাশালে রাহে” অর্থাৎ “পথের আলো”।’ রবীন্দ্রনাথের কোন চরিত্র রণেশদার প্রিয় ছিল? তিনি বলেন, ‘ঘরে-বাইরের অমূল্য। সে মারা গেলে খুব দাগ কেটেছিল মনে। তার চরিত্রে সূক্ষ্মতা ছিল। তবে গিওর্গি লুকাচ নাকি তাঁর নোটসে লিখেছিলেন, বইটা কিছুই না। ওর প্রতিক্রিয়া বুঝি। তখন তো লুকাচরা বিপ্লব করতে চাইছেন।’
শরত্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্যে রণেশদার প্রিয় চরিত্র হলো ‘চরিত্রহীন’-এর কিরণময়ী। তিনি বলেন, ‘কিরণময়ী অমর হয়ে গেছে। শরত্চন্দ্রের চেয়েও অনেক বেশি অমর।’ তিনি আরও বলেন, ‘আসলে ঔপন্যাসিক একদম জীবন থেকে নিয়ে আসে যাদের, সেসব চরিত্রই অমর হয়ে যায়। এ রকম অনেক চরিত্র আছে।’
রণেশদা বলেন, ‘একসময় ভিক্তর হুগোর উপন্যাস প্রিয় ছিল। যেমন টয়েলার অব দ্য সি, আর লা মিজারেবল তো দুর্দান্ত বই। আসলে উপন্যাসে মানুষকে বিস্তৃতভাবে আনা যায়। সেভাবে তো অনেক বই, বহু নায়কের কথাই মনে আসে।’
আর, আর কোনো প্রিয় চরিত্র? রণেশদার উত্তর, ‘লেভ তলস্তয়ের যুদ্ধ ও শান্তির কারাতায়েভ। একজন গণনায়ক।’ তিনি বলেন, ‘দেখো, বিভিন্ন সময়ে নানা অবস্থায় কতজনের সঙ্গে মিশেছি, কতজনকে যে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি, তাদের কথা মনে আসে। তাদের অনেককেই আমার বই উত্সর্গ করেছি।’
রণেশদার কাছে গান সব সময়ই প্রিয়। নিজেও গান গাইতেন। নিজেকে তিনি বলেছিলেন ‘প্রাকৃতিক গায়ক’। বড় বোন হারমোনিয়াম বাজাতেন, তিনি গাইতেন। পরে হারমোনিয়াম বাজানোও শিখেছিলেন। রাঁচির ব্রিজে দাঁড়িয়ে গাইতেন তাঁর প্রিয় গান ‘শাসানো সংযত কণ্ঠ জননী/ গাহিতে পারি না গান’। রবীন্দ্র আর নজরুলের গানও গাইতেন। প্রিয় গায়ক ছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। পরে গণসংগীত ভালোবেসেছেন। আবার বলেন রণেশদা, ‘মুনীর তো ছিল গানপাগল।’
আর শিল্পকলা? রণেশদা বলেন, ‘আমি তো শিল্পকলা নিয়ে অনেক লিখেছি। আমার প্রিয় শিল্পী ভ্যান গগ। ভালো লাগত পল গগাঁকে। গগাঁর ওপর সমারসেট মমের উপন্যাস পড়েছিলাম। খুব বিখ্যাত বই। নামটা এখন মনে করতে পারছি না।’
আর পাবলো পিকাসো? রণেশদার উত্তর, ‘তাঁকে আমার একজন নায়ক বলা যায়। পিকাসো ছিলেন অসম্ভব পরিশ্রমী একজন শিল্পী। মানুষ যে কটি আঙুল পেয়েছে, তার সর্বাত্মক ব্যবহার করেছেন পিকাসো। তাঁর মধ্যে কোনো জিনিসকে অনবরতভাবে দেখার অসম্ভব একটা ব্যাপার ছিল। ঐতিহাসিক সেই গোয়ের্নিকা নিয়ে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন, সেটা কি সহজ কথা!
একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম জীবনকে পেছন ফিরে দেখা নিয়ে। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ‘কবিতার মৃত্যু হয় না কখনো। আমি তো শুধু ঘটনাবলির দর্শক ছিলাম না, আমি একজন অংশগ্রহণকারী। কত সাফল্য, কত মহৎ চিন্তা, কত রং, ভাষার মাধুর্য বলো, মনুষ্যত্ব বলো—আমি তো এসবেরই মধ্যে রয়েছি। আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই।’
রণেশদা আরও গভীরভাবে বলতে থাকেন, ‘আমি তো শুধু পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন দর্শক নই, আমি সবকিছুর মধ্য দিয়ে চলেছি।’ তাঁর কণ্ঠ আরও গভীর হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, ‘আমি বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি।’ বলেন, ‘আমি সব যন্ত্রণা, অন্তর্যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চলেছি। বহির্যন্ত্রণাও কম ছিল না। এসব সত্ত্বেও মানুষের যে আত্মিক, মানবিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি, এককথায় মনুষ্যত্বের কথা যদি বলো, সেটা তো বাড়ছে। দেখো, দুনিয়াটা কোথায় চলে গেছে। আমি এর মধ্যেই বেঁচে আছি।’ যখন তিনি শেষ করেন, তখন কলকাতার সুন্দরীমোহন স্ট্রিটে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। সেই আলো-ছায়া অন্ধকারে রণেশদার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করতে থাকে। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি। রণেশদার দুই হাত চেপে ধরি। বলি, রণেশদা, এগিয়ে চলুন। তিনি বলেন, ‘আজকের সময়ের প্রচণ্ড গতিধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব না, সুতরাং একটু পাশে থাকাই ভালো।’ একটু পাশে নয়, তিনি আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। তিনি অনেকটা দূরই এগিয়ে ছিলেন।
১৯৮৬ সালের ১৯ জুলাই আমাকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, ‘ফয়েজ আহমদ ফয়েজ তাঁর হে সুহৃদ শহরে সন্ধ্যা কবিতার বইটির গোড়ার দিকে ইকবালের ফারসি কবিতার দুটি লাইন বসিয়েছেন, এর বাংলা হচ্ছে:
এ কথা কোনোমতেই ভেবো না যে সাকীর কাজ
সাঙ্গ হয়ে গেছে
আরও আঙুরলতার কোষে কোষে জমা আছে
হাজার হাজার ফোঁটা মদিরা পিপাসীর অপেক্ষাতে।
অর্থাৎ ফয়েজের বক্তব্য ছিল, জীবনসায়াহ্নেও পিপাসীদের দিয়ে যেতে হবে জীবন-মদিরা। ফয়েজের এই উদ্ধৃতিটি আমি এখানে খুব আওড়াচ্ছি। আমি মাঝে মাঝে গুরুতরভাবে অসুস্থবোধ করি, তখন এই লাইন দুটি মকরধ্বজের কাজ করে। আর বাংলাদেশের কাছে তো অনেক প্রত্যাশা।’ তারপর দেখি, সে বছরের ৩১ আগস্টে আমার অটোগ্রাফ বইতেও সেই লাইন দুটি লিখে তিনি নাম স্বাক্ষর করেছেন।
প্রতিবার কলকাতা থেকে ফেরার কালে দেখা করে বিদায় নেওয়ার সময় বুক ভেঙে যেত, কান্না এসে যেত দুই চোখে। শেষবার বিদায় নিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার তাঁর কাছে ফিরে গিয়েছিলাম। কেন জানি মনে হয়েছিল আর দেখা না-ও হতে পারে। বলেছিলাম, রণেশদা, আমরা ভালো নেই। আমার দুই হাত তিনি বলিষ্ঠভাবে চেপে ধরে বলেছিলেন, ‘আবার দেখা হবে, ভালো থেকো।’ দূরে এসে ফিরে দেখি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছেন রণেশদা। যতক্ষণ দেখা যায়, তাকিয়ে থাকলাম। আর বারবার উচ্চারণ করলাম, রণেশদা, ভালো নেই। রণেশদা, আমরা ভালো নেই।