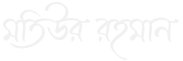সুভাষ মুখোপাধ্যায়: তিনি তো আমাদেরই লোক
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শেষ লেখা পড়েছি ২০০৩ সালের ৪ এপ্রিলের ‘দেশ’ পত্রিকায়। জ্যোতিভূষণ চাকীর বই ‘বাগর্থকৌতুকী’ নিয়ে লেখা একটা ছোট্ট আলোচনা, ‘ঘুঙুর বাঁধা এক হরবোলা’। লেখাটি সব মিলিয়ে মাত্র চুয়াল্লিশ লাইন বা আরও কম, তাতেই পুরো বইটির পরিচয় জানা হয়ে যায়। আর এই লেখাটুকু পড়েই ‘পড়ি কি মরি’ শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেট থেকে বইটি সংগ্রহ করি। কেন জানি সেদিনই বারবার মনে হচ্ছিল, এটাই কি হবে আমাদের জন্য সুভাষদার শেষ লেখা, অমৃতের সন্ধান?
বেশ কিছুদিন ধরেই শুনছিলাম, সুভাষদার শরীর-স্বাস্থ্য তেমন ভালো যাচ্ছে না। মাত্র কয়েক দিন আগে পত্রিকা পড়ে জানতে পারি, তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, অবস্থা ভালো নয়। বয়স হয়েছিল চুরাশি বছর। তারপর তো ৮ জুলাই এল সেই খবর, ‘পদাতিক’-এর কবি চিরযাত্রা করেছেন। এর পর থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভেবে চলেছি আমাদের একান্ত আপনজন সুভাষদাকে নিয়ে। আর সারাক্ষণ কখনো অস্পষ্ট স্বরে, কখনো বা আপন মনে আবৃত্তি করে চলেছি:
আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা-গাঁথা
এক নদীর নাম
আমি যত দূরেই যাই।...
পরে জানতে পেরেছি, সুভাষদার শেষ যাত্রার আগের মাসগুলোতে সংবাদ হয়েছিল তাঁর শারীরিক দুর্ভোগ আর অর্থসংকট নিয়ে। আসলে সারা জীবনই সুভাষদাকে আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়েছে। নানা ধরনের লেখালেখি করেই তাঁকে সংসার চালিয়ে নিতে হয়েছে। ‘পদাতিক’-এর কবি থেমে থাকতে পারেননি কোনো দিন।
সুভাষদার মৃত্যুসংবাদের পর থেকে তো আর তেমন কিছুই করতে পারিনি গতানুগতিকের বাইরে। সারা বাড়ি আর অফিসের তাকগুলো খুঁজে খুঁজে বের করেছি তাঁর লেখা বইগুলো—সংখ্যায় ২৪। এর বাইরে যেসব বই ছিল কিন্তু খুঁজে পাইনি, তার সংখ্যা হবে ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মোট বইয়ের সংখ্যা কত ছিল? কোথায় যেন পড়েছিলাম ৭০। এসবের মধ্যে রয়েছে কবিতা, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি, আত্মস্মৃতি, ছড়া, অনুবাদ, ইতিহাস আর বিচিত্র বিষয়ের গদ্য নিয়ে গাঁথা কিছু বই। সুভাষদার ভাষায়, ‘নানা রঙের কাপড়ের ছাঁট জোড়া দেওয়া এ যেন ফকিরের আলখাল্লা।’
সুভাষদার জনপ্রিয় কবিতার বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘পদাতিক’ থেকে শুরু করে ‘অগ্নিকোণ’, ‘চিরকুট’, ‘ফুল ফুটুক’, ‘যত দূরেই যাই’, ‘কাল মধুমাস’, ‘এই ভাই’, ‘ছেলে গেছে বনে’, ‘একটু পা চালিয়ে ভাই’, ‘জল সইতে’, ‘চইচই-চইচই’, ‘বাঘ ডেকেছিল’ ইত্যাদি। বিদেশি যেসব কবির বই তিনি অনুবাদ করেছেন তাঁরা হলেন তুরস্কের নাজিম হিকমত, চিলির পাবলো নেরুদা, কাজাখস্তানের ওলঝাস সলেমানভ, ইরানের হাফিজ; করেছেন সংস্কৃত কবিতা ও চর্যাপদের অনুবাদও। এর বাইরেও অনুবাদ করেছেন আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনসহ বিদেশি অনেক লেখকের কবিতা ও অন্যান্য রচনা। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে আছে হাংরাস, কে কোথায় যায়, অন্তরীপ, কমরেড কথা কও, কাঁচাপাকা ইত্যাদি। সুভাষদা রুশ দেশে অধিক পরিচিতি পেয়েছিলেন গদ্যলেখক হিসেবে। তাঁর তিনটি উপন্যাস রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তাঁর রিপোর্টাজধর্মী গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে আমার বাংলা, যখন যেখানে, ডাকবাংলার ডায়েরি, ক্ষমা নেই (বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে), এখন এখানে প্রভৃতি। ভ্রমণকাহিনির মধ্যে রয়েছে যেতে যেতে দেখা, অগ্নিকোণ থেকে ফিরে, ভিয়েতনামে কিছু দিন ইত্যাদি। ছোটদের জন্য লিখেছেন কথার কথা, অক্ষরে অক্ষরে, এলাম আমি কোথা থেকে; ছড়ার বই মিউয়ের জন্য ছড়ানো ছিটানো ইত্যাদি। তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা আমাদের সবার আপন: ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন। আরও দুটি অনবদ্য বই হলো কবিতাবিষয়ক লেখালেখি নিয়ে কবিতার বোঝাপড়া আর পুরোনো স্মৃতির এক দুর্লভ অ্যালবাম টানাপোড়েনের মাঝখানে। কতগুলো সাড়াজাগানো গ্রন্থ তাঁর অনুবাদে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে: ডায়েরি অব অ্যানি ফ্রাংক, রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ, চে গুয়েভারার ডায়েরি এবং মওলানা আবুল কালাম আজাদের ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম। প্রাঞ্জল ভাষায় সংক্ষিপ্তসার করেছেন নীহাররঞ্জন রায়ের বহুনন্দিত বড় গ্রন্থ ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’-এর। জীবনে পুরস্কার পেয়েছেন অনেক। ১৯৯২ সালে পেয়েছেন সাহিত্যের জন্য ভারত সরকারের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার।
১৯৬২ সালের ১২ ডিসেম্বরে কেনা কলকাতার নিউএজ প্রকাশনা সংস্থার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নামের কাব্যসমগ্রটি আজও আছে সংগ্রহে। আর ১৯৬৪ সালে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই যত দূরেই যাই তো আমাদের তরুণ জীবনের মনন-ভাবনাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলাম না বইটি, সুভাষদা নিজেই যাকে বলেছেন ‘কবিজীবনের মোড় ঘোরানো বই’।
তারপর শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটে যাই, যদি হারানো সেই ভালোবাসার যত দূরেই যাই পেয়ে বইটি যাই, এই আশায়। সেটি আর না পেলেও হঠাৎ পেয়ে যাই তাঁর গদ্যের নতুন বই ফকিরের আলখাল্লা—দারুণ সব লেখা। তা ছাড়া জানতামই না যে ১৯৪৪ সালে হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে মিলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কেন লিখি নামে একটা বই সম্পাদনা করেছিলেন। ২০০০ সালে বইটি আবার প্রকাশিত হয়েছে বর্ধিত আকারে, তাঁরই সম্পাদনায়। সেটাও সংগ্রহ করলাম।
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কত কথা মনে পড়ে, তা জমে জমে পাহাড় হয়ে যায়। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সেই দিনটির কথা। ১৯৮৬ সাল। বেলা তখন দুপুর ছুঁই ছুঁই করছে। ডা. শরৎ ব্যানার্জি রোড থেকে ছোট্ট একটি গলির মুখে পৌঁছেই তাঁকে দেখতে পেলাম। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পা তুলে বসে লিখছেন। গলির রাস্তাটুকু নিঃশব্দে অতিক্রম করে ভেজানো দরজা খুলে সরাসরি তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে ‘কেমন আছেন’ জিজ্ঞেস করতে এক-দুই মুহূর্ত ইতস্তত করেই হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন তিনি। বললেন, ‘এই মতি যে!’ এক দশকেরও বেশি সময় পর তাঁর সঙ্গে সেবার দেখা। এরপর যতবার দেখা হয়েছে, সেই একইভাবে সহাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন তিনি।
এরপর একান্তই চিকিত্সার জন্য পর পর বেশ কয়েক বছর কলকাতায় গিয়েছি। এর পরও মাঝেমধ্যে সুভাষদার সঙ্গে দেখা করতে, গল্প করতে গিয়েছি। প্রতিবারই অনেকটা সময় কাটিয়েছি তাঁর সঙ্গে। উপহার নিয়ে গিয়েছি কখনো বই, কখনো বলপেন, কখনো বা বিড়ি। প্রতিবার গিয়ে দেখেছি, তিনি কিছু না-কিছু করছেন—পড়ছেন, নয় তো লিখছেন।
এখনো বড় বেশি মনে পড়ে, প্রতিবারই দেখা হলে সেই সরল হাসি, ‘এই যে মতি’ বলে ওঠা সুভাষদাকে। মনে পড়ে, বেশ কয়েক বছর পর, ১৯৯৮ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায় দেখা করতে গেলে আমাকে চিনতে দেরি হলে সুভাষদার স্ত্রী গীতাদি (গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বলেন, ‘ঢাকার মতি এসেছে।’ তারপর সেই হাসি, সেই সস্নেহ দৃষ্টি। সেবার তাঁকে দেখে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। হাঁটতে প্রায় পারেন না, কোমর ভাঙা, কানে শোনেন না একদম। এর মধ্যেই পুরোনো ইংরেজি টাইপ রাইটারে একটা লেখা তৈরি করছিলেন। বলেছিলেন, ‘কী করব বলো, এখনো তো লিখেই খেতে হয়।’ সেই সন্ধ্যায় তিনি ঠিক আগের মতোই নানা রঙের পেনসিল দিয়ে লিখে তাঁর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সদ্যপ্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ সুভাষ মুখোপাধ্যায়: কথা ও কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। এ রকম রঙের পেনসিলে তাঁর লেখা আর ছবি আঁকাসহ আরও কয়েকটি বই উপহার পেয়েছি। ২০০০ সালের অক্টোবরে যখন শেষবার দেখা করতে যাই, তখন সুভাষদা বলেছিলেন, ‘আবার এলে রংপুরের বিড়ি নিয়ে এসো।’ কিন্তু আমার আর যাওয়া হয়নি। তাঁকে রংপুরের তামাকের বিড়িও দেওয়া হয়নি! সেই দুঃখ এখনো আমার মনে বড় বেশি করে বাজে।
কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর। ১৯৭২ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের জাতীয় সম্মেলনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে ঢাকায় আসেন, তখনই তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা হয়। তাঁকে কাছ থেকে দেখে, ঘনিষ্ঠভাবে জেনে ও বুঝে কবিতাকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছিল কবির প্রতি সৃষ্টি হওয়া গভীর ভালোবাসাও। তবে তাঁকে ও তাঁর লেখাকে আমরা জেনেছিলাম ষাটের দশকের শুরুতেই। সে সময়ে সামরিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীর, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের প্রবল আন্দোলনের পোস্টার, ব্যানার, গান আর আবৃত্তিতে সুকান্ত-সুভাষের কবিতার উজ্জ্বল পঙ্ক্তিগুলো স্থান পেয়েছিল। আজও মনে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘ঘোষণা’ কবিতা থেকে নেওয়া সেসব পোস্টারের একটা স্লোগান ‘এ দেশ আমার গর্ব/ এ মাটি আমার চোখে সোনা’। তাঁর আরও কত কবিতা আবৃত্তি হতো, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারা-বর্ণনায় ব্যবহার করা হতো! আমাদের প্রধান গণসংগীতশিল্পী শেখ লুত্ফর রহমান সুভাষদার ‘প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য’ (মে দিনের কবিতা) কবিতায় সুর দিয়ে একটা জনপ্রিয় গান তৈরি করেছিলেন।
তখন আমরা কলেজের ছাত্র, উত্সাহী রাজনৈতিক কর্মী, কমবেশি কবিতাচর্চায় নিমগ্ন। বলা যায়, সুকান্ত-সুভাষের কবিতাতেই আমরা সেসব তেজস্বী দিনের লড়াই আর ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষাগুলোর প্রতিচ্ছায়া দেখতাম। একান্ত ভাবনাগুলো থেকে শুরু করে ভবিষ্যতের স্বপ্ন পর্যন্ত সবকিছু যেন পেয়ে যেতাম তাঁদের কবিতার ছত্রে ছত্রে। সেই আবেগ, সেই হৃত্স্পন্দন আজও বড় বেশি পিছু টানে! এভাবেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমাদের মনন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতাকে প্রভাবিত করে চলছিলেন গভীরভাবে, দশকের পর দশক ধরে।
১৯৭৪ সালে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত হয়ে সুভাষদা ঢাকায় এলে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ে। তাঁর কাছ থেকে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির বহু বিচিত্র বিষয় জানা-বোঝার সুযোগ পাই। মনে পড়ে, সেবার পুরানা পল্টনের সাপ্তাহিক ‘একতা’ অফিসে বসে ছোট একটা লেখা লিখে দিয়েছিলেন। আর সে রাতের কথা তো কোনো দিনই ভুলব না। কারণ, রাত প্রায় ভোর হয়ে গিয়েছিল সাহিত্য নিয়ে আলোচনা, সমাজের প্রতি লেখকের দায়িত্ব নিয়ে বিতর্ক আর তত্কালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাহিত্য-সংস্কৃতির নানামুখী গতিপ্রকৃতি মূল্যায়নের করতে গিয়ে।
২০ ফেব্রুয়ারিতে হোটেল পূর্বাণীর সে রাতের গভীর আলোচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা কাজাখ লেখক আনোয়ার আলিজানভ ও লেখক ইউনিয়নের নেত্রী মরিয়ম সালগানিকের সান্নিধ্যও পেয়েছিলাম আমরা। রাত শেষ হয়ে যখন ফুটে উঠছে ভোরের প্রথম আলো, তখন রাস্তায় বেরিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে হেঁটে ছোট ছোট মিছিলের সঙ্গে পা মিলিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম বাংলা একাডেমির বটতলায়। দিনটি ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি। এখনো ভেবে আন্দোলিত হই, একই সঙ্গে মন বিষাদে ভরে যায়, সেই কবে একুশের ভোরে মিছিলে হেঁটেছিলাম সুভাষদার সঙ্গে! এই একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে সুভাষদা কবিতা আর গদ্য দুই-ই লিখেছেন।
সেই বছরের ডিসেম্বরে, প্রচণ্ড শীতের সময় মস্কোতে সুভাষদার সঙ্গে আবার দেখা। রুশ লেখক ইউনিয়নের অফিসে সেই মরিয়ম সালগানিকের সঙ্গে আমাদের অনেক গল্প আর আড্ডার কথা মনে পড়ে। তখন সুভাষদা আফ্রো-এশীয় লেখক সমিতির একজন নেতা।
মনে পড়ে, একবার সাহিত্য, রাজনীতি, তাঁকে ঘিরে তপ্ত হয়ে ওঠা রাজনৈতিক বিতর্ক এবং সুভাষদার ভালো লাগা না-লাগা সম্পর্কে নানা বিষয়ে সরাসরি বিস্তারিত জানার আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি সাগ্রহে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ১৯৮৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরের পুরো সকাল-দুপুর নির্দিষ্ট হয়েছিল সে জন্য। আমার আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পেরে তিনি নিজে থেকেই বললেন, ‘আমাদের কথোপকথন থেকে যে লেখা তৈরি হবে, তাকে আমরা “আত্মজিজ্ঞাসা” হিসেবেই বিবেচনা করতে পারব।’ তখন আমরা ঢাকার বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। সে কারণে তখনকার রাজনীতি ও রাজনীতির ভবিষ্যৎ আমাদের আলোচনায় এসেছিল বারবার। বিশেষ করে, সুভাষদাকে নিয়েও তখন অনেক কথা। ঢাকায় বসেও সেসব শুনে আমাদের মনে জেগে উঠত নানা প্রশ্ন।
প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য থেকে পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কারণ সম্পর্কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় খোলাখুলি কথা বলেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন, ‘১৯৭৮ সাল থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও কংগ্রেস দল সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) নীতি মেনে নিতে পারিনি। তবে এর আগেও কোনো কোনো সময়ে পার্টির নীতি বা আমার লেখা নিয়ে কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তবে আমি বরাবরই পার্টির নীতি মেনে চলেছি। ষাটের দশকের মধ্যভাগে পার্টির ভাঙনে অশেষ কষ্ট পেয়েছি, দুঃখে অনেক রাত আমি ঘুমোতে পারিনি।’
সিপিআইয়ের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের পর তিনি কোন মতবাদে বিশ্বাস করেন, এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, ‘আমি নিজেকে কমিউনিস্ট বলে মনে করি। তবে আমি মনে করি না কমিউনিস্ট বলে আমার কোনো ভুল নেই, আমার চিন্তাধারা অভ্রান্ত। আগে যেসব কথা ভেতরে বলতাম, সেগুলো এখন বাইরে বলি।’
সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করেন না তিনি পার্টি বা সাম্যবাদী আদর্শের কোনো ক্ষতি করছেন। সত্যিই কি তা-ই? শুধু বামপন্থী নয়, বাংলাদেশেও সাধারণভাবে অনেকেরই এ প্রশ্ন ছিল। কারণ, তাঁদের সবার কাছেই প্রগতির উজ্জ্বল এক প্রতীক তিনি। ‘কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?’—প্রথম জীবনের সেই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা তাঁর হাতে হাত রেখেছিলেন পরম বিশ্বাসে, তাঁদের তিনি কী বলে বোঝাবেন, প্রশ্ন করতেই সুভাষদা স্মিত হেসেছিলেন।
কিন্তু তিনি তাঁর জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির বিরাট অবদানের কথা স্বীকার করেছেন সব সময়। তাঁর কথায়, ‘আমার জীবন, আমার সাহিত্যে এটা সত্য। বহু সময়ে বহুজনকে হতাশ হতে দেখেছি। কিন্তু আমি হতাশ হইনি। পার্টিতে না এলে আমি কোনো দিন এভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে পারতাম না। জীবনকে এমন স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পেতাম না। পার্টিতে না এলে আমি কী হতাম? হয়তো অধ্যাপক বা বড় চাকুরে। এমন লোককে আমি ঈর্ষা করি না। বরং ওঁরা আমাকে ঈর্ষা করে। আমি শহরের মানুষ। একজন মধ্যবিত্ত। কিন্তু আমি সারা বাংলাতেই যেতে পারি। সর্বত্র আমি বন্ধু-আত্মীয় পেয়েছি; পরে সারা ভারতেও। এমনটা হতো না, যদি আমি একটা আদর্শবাদী পার্টিতে না থাকতাম। তাই আমি দুঃখ করি না। বরং আমি কৃতজ্ঞ কমিউনিস্ট পার্টির কাছে।’
শুধু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নন, এ কৃতজ্ঞতাবোধ রয়েছে আমাদের মধ্যেও। কিন্তু এ-ও আরেক সত্য যে অনেক সাফল্য সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি এবং এককেন্দ্রিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই ওই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মস্ত বড় কারণ।
তাঁর প্রিয় লেখকদের সম্পর্কে জানতে চেয়ে তাঁকে বেশ বিপদে ফেলেছিলাম। কারণ, এ রকম প্রশ্ন সব সময়ই বেশ বিব্রতকর, বিশেষ করে লেখকদের জন্য। একটু চিন্তা করে তিনি বললেন, ‘বলা খুব মুশকিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাদ দাও। তিনি তো আছেনই। কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সমর সেন আর অরুণ মিত্র। যাঁরা আমাদের অগ্রজ, সবার লেখাই আমার ভালো লাগে।’
বুদ্ধদেব বসু?
‘বুদ্ধদেব বাবুকে মানুষ হিসেবে, সম্পাদক হিসেবে খুব শ্রদ্ধা করি।’
লেখক হিসেবে?
‘খুব একটা টিকবেন, স্থায়ী হবেন, তা মনে হয় না। প্রথম দিকের লেখাগুলো ছাড়া, যেমন: বন্দীর বন্দনা।’
আপনার সমবয়সী লেখকদের মধ্যে কার লেখা ভালো লাগে?
‘এটা বলা মুশকিল। তবে অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষের লেখা পছন্দ করি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প খুব ভালো লাগে।
‘ঢাকার কবিদের মধ্যে শামসুর রাহমান আর আল মাহমুদের প্রায় সব কবিতাই ভালো লাগে। নির্মলেন্দু গুণেরও কিছু কিছু কবিতা ভালো লাগে। তবে অনেক সময় বড় বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে যায়।’
সাহিত্যের বাইরে কোন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ রয়েছে, তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘সাহিত্য আমার খুব বেশি পড়া নেই। আমার ঝোঁকটা সেদিকে নয়। বরং সাহিত্যের বাইরের বিষয় নিয়ে পড়তেই আমি বেশি পছন্দ করি। দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব আর পপুলার সায়েন্স। এসব বিষয়ে বই পড়তে আমার বেশি ভালো লাগে। কারণ, তা থেকে আমি জানতে পারি অনেক বেশি।
‘বিদেশি অন্য ভাষার লেখক-কবিদের মধ্যে আমি ওয়াল্ট হুইটম্যানের ভক্ত ছিলাম। আমার নিজের লেখায় তুরস্কের নাজিম হিকমতের খুব প্রভাব আছে। কৈশোরে রুশ কবি মায়াকোভস্কিকে খুব ভালো লাগত। যে লেখক আমাকে প্রভাবিত করেননি, অথচ ভালো লেগেছে, তিনি হলেন চিলির পাবলো নেরুদা।’
শেষবার যখন দেখা হলো তখনো সুভাষদা বলেছিলেন, ‘সম্ভব হলে উর্দু-বাংলা অভিধান আর ধাঁধার বই পেলে পাঠাবে।’
কবিতা, লেখালেখি এবং নিজের প্রিয় লেখকদের নিয়ে কথা বলার সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে তিনি বেশ কিছু মন্তব্য করলেন। উল্লেখ করেন দুটি ঘটনারও। আর তা থেকে উঠে এল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর চিন্তাভাবনার পরিচয়। তাঁর কথায়, ‘ছেলেবেলায়, কৈশোরে আমি রবীন্দ্রবিরোধী ছিলাম। এর বোধহয় প্রয়োজন ছিল। তাঁর কাছ থেকে সরে আসার দরকার ছিল। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিতায় একটা চিঠি লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম ‘রবিবাবুকে’। কবিতাটি ছিল দীর্ঘ। কবিতাটি পরে আর খুঁজে পাইনি। সেটির মূল কথাগুলো ছিল এ রকম, “তোমার কবিতা আমাকে মুগ্ধ করে। আমি তখন অন্য রাজ্যে চলে যাই। কিন্তু আমি যখন বাস্তবে ফিরে আসি, তখন আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়...। তোমার কবিতা আর আমার বাস্তবতায় কোনো মিল খুঁজে পাই না। তাই, হয় তোমার কবিতা ফিরিয়ে নাও, নয় এই জগত্টাকে বদলে দাও।”
‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ডাকে কবিতাটি পাঠিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় ছিলাম। যদিও সেটা একরকম ঔদ্ধত্য ছিল। পরে একদিন উত্তর পেলাম। তবে সেটা রবীন্দ্রনাথ লেখেননি। লিখেছিলেন তাঁর সে সময়ের সহকারী সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। তিনি লিখেছিলেন, “গুরুদেব আপনার কবিতা পড়ে খুশি হয়েছেন, আশীর্বাদ করেছেন।” মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ নিজে লেখেননি বলে সেদিন বেশ চটেছিলাম।’
সুভাষদা একটু সময় নিয়ে ভেবে বললেন, ‘পরে ১৯৫৩ সালে শান্তিনিকেতনের এক সাহিত্যসভায় যোগ দিয়েছিলাম। সেখানে সুধাকান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে আমি রবিবাবুর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়েছিলাম। সুধাকান্ত বাবু বলেন, “আমি কবিতাটি পড়তে শুরু করলে গোড়ার দিকে তাঁর মধ্যে খুশি খুশি ভাব দেখা দেয়। কিন্তু কবিতাটি শেষ হলে গুরুদেব গম্ভীর হয়ে যান।” বহুদিন পরে হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া জেনে আমি খুশি হয়েছিলাম।
‘আরেকটি ঘটনার কথা বলি। ১৯৪৯ সালে, আমি তখন কলকাতা জেলে আটক। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে পার্টিতে তুমুল বিতর্ক বেধেছিল। মূল বিষয় ছিল: রবীন্দ্রনাথ-হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ-না। জেলের ভেতরে যাঁরা ছিলেন, পার্টি থেকে তাঁদেরও মত চেয়ে পাঠানো হয়। সে সময়ে পার্টির সামগ্রিক উগ্র রাজনীতির প্রভাবে আমিও রবীন্দ্রবর্জনের পক্ষে মত দিয়েছিলাম।
‘জেলের ভেতরে তখন এক মজার ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে একবার পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হলো। আমিও বক্তা ছিলাম। বলার আগে ঠিক করে নিয়েছিলাম, বলব রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি ইত্যাদি। কিন্তু বলতে বলতে যখন শেষ করলাম, দেখা গেল আমি পুরোপুরি আমার চিন্তার বিরুদ্ধে বলেছি। রবীন্দ্রনাথ-হ্যাঁ-এর পক্ষে বলেছি। এ নিয়ে কারাবন্দী বন্ধুদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।’
নিজের পেশা ও শখ নিয়ে সুভাষদা বলেন, ‘আমার কোনো স্থায়ী পেশা বা জীবিকা নির্বাহের জন্য তেমন কিছু ছিল না। শুরুতে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে শিশুপত্রিকা সন্দেশ সম্পাদনার কাজে যোগ দিয়েছিলাম। রুচিশীল প্রকাশনী সংস্থা সিগনেটের সঙ্গেও কিছুদিন কাজ করেছি। তবে সে-ও অল্প দিনের ব্যাপার। আমার স্থায়ী পেশা সব সময়ের জন্যই সাহিত্য আর রাজনীতি।
‘প্রথম জীবনে ফুটবল খেলার পাগল ছিলাম। রাজনীতিতে আসার পর খেলা বিদায় নিয়েছে। এখন মাছ ধরতে ভালোবাসি। আর ভালো লাগে ছোটদের সঙ্গে মিশতে, গল্প করতে।’
কী করে, কী করে স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থে তিনি বলেছেনও, ‘ছেলেবেলায় স্বপ্ন ছিল লড়াইয়ের ময়দানে পল্টন হওয়ার। তারপর সন্ন্যাসী ও জেলখাটা স্বদেশি হওয়ার। বয়ঃসন্ধিতে পেয়ে বসেছিল খেলোয়াড় হওয়ার বাসনা। শেষ পর্যন্ত কোনোটাই টেকেনি।’
জিজ্ঞেস করি, আপনার বন্ধুদের মধ্যে আগে কাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন?
সুভাষদা বলেন, ‘পুরোনো বন্ধু-সুহৃদদের কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বান্নে ভাই, সাজ্জাদ জহীরের কথা। এই উর্দু সাহিত্যিকের আকস্মিক মৃত্যু আমাকে তীব্র কষ্ট দিয়েছে। হিন্দি চলচ্চিত্রজগতের বড় মাপের শিল্পী বলরাজ সাহনীর সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগেও বোম্বাই শহরে দেখা হয়েছিল। এক সেমিনারে তিনি ছিলেন সভাপতি আর আমি বক্তা। বলরাজ সাহনী আমার বাংলা বক্তৃতার হিন্দি তরজমা করে দিয়েছিলেন। তাঁর মতো শিল্পিত মন আর হয় না। উর্দু সাহিত্যিক কৃষান চন্দর আর চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের কথাও সব সময় মনে পড়ে।’
আমাদের কথোপকথনের একপর্যায়ে তিনি বলেন, বছর দুই-তিন আগে দার্জিলিংয়ে এক অনুষ্ঠানে রবিশঙ্করের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। তাঁরা পুরোনো দিনগুলোর কথা, সেই চল্লিশের দশকের সময়ের কথা বলেছিলেন। রবিশঙ্কর জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবার তেমন কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায় না?
সুভাষদা সেদিন বলছিলেন, ‘সুচিত্রা মিত্র আর জর্জ বিশ্বাসের মতো শিল্পী হয় না।’ তাঁর আবাল্য বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আসেন মাঝেমধ্যে। শিল্পী নীরদ মজুমদার, পরিতোষ সেন ও অপেক্ষাকৃত সমবয়সীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। সে সময় সবার সঙ্গেই ছিল মেলামেশা। পরিচিত মহল, বন্ধুমহল ছিল বেশ বড়। সে হৃদ্যতা, সে আন্তরিকতা এখন আর দেখা যায় না।
কলকাতায় অবস্থানকালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বারবার দেখা করা, অনেক সময় ধরে কথা বলা আর তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের নানা দিক খুঁটিয়ে দেখা কোনো পরিকল্পিত ব্যাপার ছিল না। তবে তাঁকে নিয়ে বহু জিজ্ঞাসা ও বহু প্রশ্ন ছিল। বন্ধুর পথে সুভাষদার অবিরাম পথচলা, পদ্য-গদ্য-উপন্যাস আর অনুবাদে তাঁর অব্যাহত শিল্পচর্চা, প্রতিবাদের কাঁটার আঘাত আর কদাচিৎ ফুলের স্পর্শ পাওয়া, সবশেষে তাঁর বিতর্কিত রাজনীতির নানামুখী জটিলতা নিয়ে কথা বলে এবং নিবিড় বিশ্লেষণ করে আমার নিজের বহু জিজ্ঞাসারও অনেক উত্তর পেয়েছি। সন্ধান পেয়েছি রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি আর জীবনের অন্তর্ভেদী আলোর।
সুভাষদার সঙ্গে নানা সময়ে এতভাবে মিশেছি কিন্তু কখনোই তাঁর শৈশব, পরিবার বা দেশের বাড়ি নিয়ে কোনো কথা হয়নি। কেন হয়নি, তা ভেবে এখন অবাক লাগে। সুভাষদার লেখায় ও কাজে সব সময়ই আমরা বাংলাদেশের একটা বিশেষ স্থান দেখেছি। আমরা জানি, চল্লিশের দশকের মন্বন্তরের সময়ে পূর্ববাংলায় তিনি অতীশ দীপঙ্করের মুন্সিগঞ্জের গ্রামে গ্রামে হেঁটেছেন। কবিয়াল রমেশ শীলকে খুঁজতে খুঁজতে চলে গেছেন চট্টগ্রামে। গারো পাহাড়ের পাদদেশে সুসুং দুর্গাপুরে মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন হাজং নেতা ললিত সরকারের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর ঢাকায় এসেছেন পূর্ববাংলা সাহিত্য সম্মেলনে। ঢাকা শহরে ঘুরেছেন, খুঁজে পেয়েছেন পুরোনো বন্ধু ফররুখ আহমদকে, কিংবদন্তি ইলা মিত্রকে হাসপাতালে দেখতে গেছেন, মধুর ক্যানটিনে চা খেতে খেতে আড্ডা দিয়েছেন। ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে লিখেছিলেন দুটি অনবদ্য রিপোর্টাজ ‘একুশের সুরে বাঁধা’ আর ‘লিখতে বারণ’।
একাত্তরের মার্চে যখন স্বাধীনতাসংগ্রাম শুরু হয়, সুভাষদা তখন উত্তর ভিয়েতনামের এক গ্রামে। সঙ্গে ছিলেন লেখক সাজ্জাদ জহীর। গ্রাম থেকে হ্যানয় শহরে ফিরে বাংলাদেশের লড়াইয়ের খবর পেয়েই সুভাষদা লিখেছেন, ‘আমি লাফিয়ে উঠলাম।’ বাংলাদেশ স্বাধীন হবে, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। কলকাতায় ফিরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামের সমর্থনে লেখক-শিল্পীদের সংগঠিত করার কাজে নেমে পড়েছিলেন। রাতদিন ছোটাছুটি করেছেন। নানাভাবে সাহায্য করেছেন বাংলাদেশের লেখক-শিল্পীদের। বিজয়ের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি, তার আগেই ৩ ডিসেম্বরের পর সুভাষদা ঢুকে পড়েছিলেন বাংলাদেশের ভেতরে যশোরে। মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে রাত কাটিয়েছেন। ১১ থেকে ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুরো সময় যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরার বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে ঘুরেছেন মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে, মিশেছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। দেখেছেন, মানুষ দলে দলে প্রিয় স্বদেশভূমিতে ফিরছে। প্রত্যক্ষ করেছেন পাকিস্তানি সেনাদের নৃশংসতা। সাতক্ষীরায় মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে বসে মোমের আলোয় পড়েছেন জীবনানন্দ দাশের রূপসী বাংলা। ভেবেছিলেন জীবনানন্দ দাশের বাংলাদেশ নিয়ে একটা তথ্যচিত্র করবেন।
একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম নিয়ে কবিতা লিখেছেন, রিপোর্টাজ লিখেছেন। কলকাতায় দেখা জহির রায়হানের ছোট দুই ছেলে অপু-তপুকে উদ্দেশ করে চিঠির আকারে লিখেছিলেন এক দারুণ গদ্য। যিনি পড়বেন, তাঁকে যুগপৎ বিষণ্ন আর উদ্দীপিত করবে। তিনি লিখেছিলেন, ‘জহিরের মতো বড় মনের মানুষ আমি জীবনে বেশি একটা দেখিনি।’
বাংলাদেশকে নিয়ে সুভাষদা যা লিখেছেন, তাঁর একটা সংকলন গ্রন্থ ঢাকার সাহিত্য প্রকাশ থেকে প্রকাশ করেন বন্ধু মফিদুল হক। সুভাষদার দেওয়া নামে বাংলা আমার, বাংলাদেশ প্রথম বের হয় ১৯৮৮ সালে, দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ১৯৯৮ সালে। এটি পরিকল্পনার জন্য মফিদুল হককে কৃতজ্ঞতা জানানোর পাশাপাশি বইটি বের করতে আমার উত্সাহের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন সস্নেহে। এত দিন পর সুভাষদার ওই লাইন কটি আবার পড়ে চোখে পানি চলে আসে, চোখ ভিজে যায়। আমি বারবার মনে মনে বলতে থাকি, সুভাষদা, আপনাকে কোনো দিন ভুলব না।
বাংলাদেশের প্রতি সুভাষদার কেন এত টান, সেটা এবার নতুন করে জেনে আনন্দে বিস্মিত হলাম। কারণ, বাংলাদেশের প্রতি সুভাষদার নাড়ির টান রয়েছে। তাঁর দেশের বাড়ি ছিল চুয়াডাঙ্গার দর্শনার লোকনাথপুর গ্রামে। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ ফকিরের আলখাল্লায় প্রকাশিত রিপোর্টাজ ‘পুনর্দর্শনায়’ লিখেছেন, ‘আমাদের গ্রাম হলো লোকনাথপুরে। ছেলেবেলায় দর্শনায় নেমে আমরা গরুর গাড়িতে মেঠো রাস্তার ধুলোকাদা ভেঙে ঢিকোতে ঢিকোতে গ্রামে গিয়ে পৌঁছতাম।’ অর্ধশতাব্দী পর সুভাষদা সীমান্ত পার হয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন দর্শনা পুনর্দর্শনায়। সেই কবে ঠাকুরদার সঙ্গে শেষবারের মতো লোকনাথপুরে গিয়েছিলেন, তা মনে ছিল না তাঁর। তিনি শুনেছেন, তাঁদের আদি বাড়ি ছিল যশোরে সুমুদ্দি গ্রামে। কোনো দিন যাননি সেখানে। শেষমেশ দর্শনায় গিয়ে ওই গ্রামেরও কোনো খোঁজ পাননি।
আসলে সুভাষদার শৈশবের স্মৃতিকথা আমাদের সবার আপন: ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন পড়ে এবারই প্রথম জানলাম তাঁর গ্রাম, শৈশব, মা-বাবা, পরিবারের অনেক কথা। ঠাকুরদা সুভাষদার নাম রেখেছিলেন ‘গোবিন্দ’। বাবা ডাকতেন ‘কালো’ বলে। ছিলেন তিনি ‘মা-সোহাগী’। জন্মেছিলেন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে মামাবাড়িতে। তাঁর শৈশবের তিন-চার বছর কেটেছিল কলকাতায়। কলকাতার পর শৈশবের বড় অংশই কেটেছে রাজশাহীর নওগাঁয়। তিনি লিখেছেন, ‘মানুষের যেখানে জ্ঞান হয়, সে জায়গাই মনের মধ্যে আজীবন থেকে যায়। সেই থেকে উত্তর বাংলার ওপর আমার টান।’ নওগাঁ থেকে ঠাকুরদার সঙ্গে পুজোর ছুটিতে যেতেন লোকনাথপুরে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, ‘নাটোরে এলে কাঁচাগোল্লা, ঈশ্বরদীতে চা, তারপর পদ্মা পেরিয়ে পোড়াদহতে আরেক দফা মুখ বদলানো। এই করে ট্রেন এসে দাঁড়াত দর্শনাতে।’ তারপর বাকি পথ যেতেন গরুর গাড়িতে বা দাদার সঙ্গে দৌড়ে। এই নওগাঁতেই সুভাষদাকে আট বছর বয়সে, তাঁর ভাষায়, ‘ধরে-বেঁধে মাইনর স্কুলের খোঁয়াড়ে’ ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। এই নওগাঁতেই তিনি প্রথম কবিতা লিখেছিলেন। তখন তাঁর বয়স আট-নয় বছর হবে। আসলে নওগাঁর জীবনপ্রবাহ সারা জীবন সুভাষদাকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর নানা লেখায় বারবার এসেছে নওগাঁ আর নওগাঁর মানুষের কথা।
নওগাঁ থেকে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতায়। অষ্টম শ্রেণীতে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়েছিল স্কুল ম্যাগাজিন মৈত্রীতে।
সুভাষদার সঙ্গে বাংলাদেশের নাড়ির টানের খবর পেয়ে বুঝতে পারি তিনি সত্যিই ছিলেন আমাদের, বাংলাদেশের একজন। তাই বলতে কোনো দ্বিধা হয় না, যত দূরেই যান, তিনি তো আমাদেরই লোক।
আমাদের এই সুভাষদার সঙ্গে শেষ দেখা হয় ২০০০ সালের ৬ অক্টোবর সকালে। আবারও সেই বিলম্বে চিনতে পারা, সেই হাসিখুশি সুভাষদা। মনে পড়ে, সব কথাই বলছিলাম কাগজে লিখে লিখে। তিনি কিন্তু কথা বলেছেন পরিষ্কার, ধীরে ধীরে—যেমনটা বলেন সব সময়। তাঁকে বলি, সুভাষদা, কয়েকটি প্রশ্ন করি?
তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, প্রশ্ন লিখে দাও।’
আমার প্রশ্ন, কেমন আছেন, সুভাষদা?
‘এককথায় ভালো আছি। তবে হাঁটতে পারি না। কোমর ভাঙা। কানে শুনতে পাই না। কথা বলতে পারলেও হাবা হয়ে গিয়েছি। কারণ, কারও সাথে তো কথা বলতে পারি না। লিখে লিখে তো আলাপ হয় না। ফলে যা ছিলাম না কখনো, ভয়ানক একা হয়ে গিয়েছি। বাড়ির মধ্যে একা। কারও সঙ্গে কথা বলতে পারি না। কী ঘটছে জানতে পারি না। যখন কাগজ পড়ি মন খারাপ হয়। যাঁরা রাজনীতিতে বড় বড় প্রতিষ্ঠিত নেতা, তাঁদের কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই। দ্বিতীয়ত, এই খুনোখুনি আর সহ্য হয় না। মতি, বড় কষ্ট পাই। কোথাও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না।’
আর, লেখালেখি?
‘লিখেছি তো অনেক, কিন্তু এখন আর শরীরে ঠিক কুলোচ্ছে না। মেজাজও সে রকম থাকছে না। এখন লেখার চেয়ে পড়ার দিকে বেশি ঝোঁক। আমি তো লাইব্রেরিতে যেতে পারি না। কাজেই কেউ যখন বই দেয়, সেগুলো পড়তে পারি। লেখা বন্ধ নয়। আমার এখন প্রায় একাশি বছর বয়স। এখনো সংসার চালাতে হয়। তাই এখনো লিখে খেতে হয়, ফরমায়েশ খাটতে হয়। জীবনে চাকরি করিনি। পেনশন নেই। দিন আনি দিন খাই। এই চলে যাচ্ছে।’
১৯৫১ সালে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর নতুন জীবন শুরু, একসঙ্গে চলার পথ ফুরোল মাত্র সেদিন। দীর্ঘ নিঃসন্তান দাম্পত্যজীবন। কিন্তু সন্তানের অভাব তাঁদের হয়নি। প্রথম সন্তান পুপেকে আনেন বজবজে পার্টির সংগঠন তৈরির সময়। একে একে তিনটি মেয়ের আশ্রয়স্থল হয় তাঁর অনটনের বাড়িতে। পরে আরও দুটি। নিয়মিত রোজগারহীন এক স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ এই কলকাতা শহরে মোট পাঁচটি সন্তান স্বেচ্ছায় আর সানন্দে প্রতিপালন করেছেন। লক্ষ করার বিষয়, তাঁদের পাঁচজনই মেয়ে।
আবার লিখে প্রশ্ন করি, সুভাষদা, অতীতের কথা মনে হলে কষ্ট হয় না?
‘অতীত নিয়ে খুব একটা ভাবি না। তার কারণ, আমার জীবনে সত্যি বলতে কি আফসোস করার কিছু নেই। একটাই শুধু আফসোস, বহু কিছু পড়া হয়নি, জানা হয়নি। জানি না, আমার অন্য রকম জীবন হলে সেটা হতো কি না। যদি অধ্যাপক বা সাংবাদিক হতাম, তাহলে হয়তো আরও বেশি পড়াশোনা করতে পারতাম। তার বদলে মানুষ দেখেছি, বহু ভালো মানুষ দেখেছি। ধরো, আমরা জীবনে বহু কিছু ভুল ভেবেছি, ভুল কাজ করেছি। কিন্তু তার কোনোটাই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। সে জন্য আমার কোনো অনুতাপ নেই। বরং যেভাবে জীবন কাটিয়েছি তাতে বলতে পারি, হয়তো বৈষয়িক খুব কিছু না পারলেও মনের সুখে কাটিয়েছি। জীবনটা তো খুব ভালোভাবে কেটেছে। ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষকে তো ভালোবাসতে শিখেছি। ভালোবাসা পেয়েছি। তার চেয়ে বড় জিনিস তো হয় না। তারপর যেটা হয়নি সেটা তো তুচ্ছ।’
সুভাষদা, ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবেন?
‘ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুব আশাবাদী। আমাদের দেশ এত বদলে যাচ্ছে। আমি তো এখন গ্রামে বা কোথাও যেতে পারি না। যারা ঘুরে আসে, সেখানে তো দেখি যারা নিচে পড়ে ছিল, তারা অসম্ভব বদলে যাচ্ছে। এই ধরো, বাংলাদেশ সম্পর্কে যা পড়ি, ইউনূস যেভাবে গ্রামকে বদলে দিচ্ছে, গ্রামের জীবন, আমাদের এখানে সে রকম না থাকলেও, ধরো, এখানকার কৃষকের ছেলেরা যেভাবে লেখাপড়া করছে, ওরা অনেক ভালো ফল দেখাচ্ছে। ওদের মধ্যে অনেক বেশি ওপরে ওঠার জিদ রয়েছে। শহরে বসে ওপর তলার মানুষদের দেখি। উচ্চ বর্ণের উচ্চ আয়ের বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে খুব হতাশ হয়ে যাই। মনে হয়, এটা আজকের সমাজচিত্র নয়। আজকের চিত্র হলো, যারা নিচে পড়ে ছিল, ওরা সামনে উঠে আসছে। চাকরির চেয়ে লোকের নিজে কিছু করার, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে যাওয়ার ঝোঁকটা বেড়েছে। রাস্তাঘাটে বেরোলে যে ভিড় আমরা দেখি, সেটা শুধু লোকসংখ্যা বেড়েছে বলে নয়, আসলে এত দিন যারা ঘরে বন্দী ছিল, তারা এখন বাইরে বেরিয়ে আসছে। আমার কাছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়।’
সুভাষদা বলেন, ‘বাংলাদেশে যেতে, ইউনূসের গ্রাম দেখতে খুব ইচ্ছে করে। আমি ওর খুব ভক্ত।’
যখন ফিরে আসব, সুভাষদা স্বভাবজাতভাবে আস্তে আস্তে বললেন, ‘আবার এসো মতি। আর কি দেখা হবে, বয়স তো হলো!’
সত্যি, আর তো দেখা হলো না।
সারা জীবন সুভাষদা লড়েছেন জীবনের লড়াই। তিনি বলেছিলেন, ‘কবিতা মূল্যবান, কিন্তু জীবনকে আরও মূল্যবান মনে করি।’ সুভাষদা আসলে ভালোবেসেছিলেন এই জীবনটাকেই—স্বপ্ন, আদর্শ, কবিতা, রাজনীতি, বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি যার এক-একটা অংশ মাত্র। স্মৃতিকথামূলক গদ্য কী করে কী করে বইয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘কবি হবে ছেলেমানুষ। তার মন হবে সাদা, সরল, নিষ্পাপ, সবকিছুতেই থাকবে তার বিস্ময়।’ তিনিই ছিলেন সত্যি সত্যি সেই কবি।
মনে পড়ছে তাঁর সেই কবিতা ‘আজ আছি কাল নেই’-এর কথা। কবিতাটির অংশবিশেষ:
আজ আমি ঠিক আমারই মতন
একজনকে খুঁজছি
যার মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে পারি—
ভাই, একটু ধরো তো
আমি আসছি।
বাংলা ভাষার এই এক মাধুর্য—
আসছি বলে
স্বচ্ছন্দে চলে যাওয়া যায়।
নাকি আমরা আদতে যাই না
আসি।
সুভাষ মুখোপাধ্যায় যাননি, আছেন। এখন থেকে আরও বেশি করে আছেন।